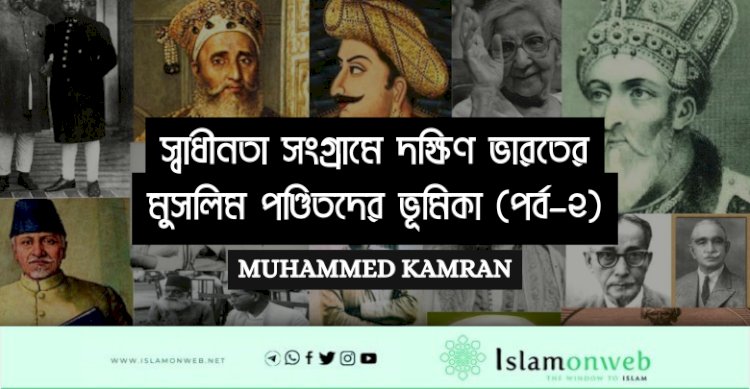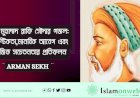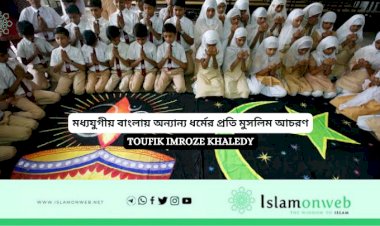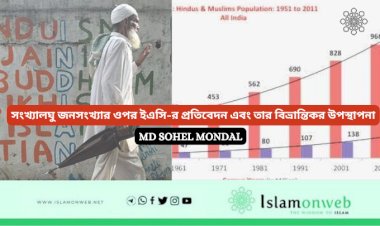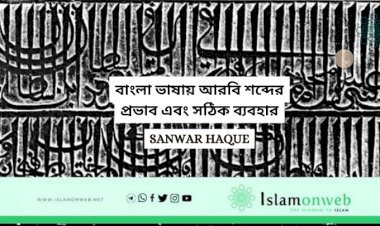স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম পণ্ডিতদের ভূমিকা (পর্ব–২)
সূচনা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম আলেম ও মুক্তিকামীদের ভূমিকা উত্তর ভারতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। মালাবার থেকে হায়দরাবাদ, মাইসোর থেকে তামিলনাড়ু—এই অঞ্চলের আলেমরা শুধু স্থানীয় পর্যায়েই নয়, বরং সর্বভারতীয় সংগ্রামে এক বিশেষ ছাপ রেখে গেছেন। তাঁদের কেউ ছিলেন পরাক্রমশালী শাসক, কেউ ছিলেন আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক, আবার কেউ ছিলেন বিপ্লবী চিন্তাবিদ ও সংগঠক।
প্রথম পর্বে আমরা উত্তর ভারতের অগ্রণী আলেমদের আলোচনা করেছি। এবার দ্বিতীয় পর্বে দক্ষিণ ভারতের আটজন বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হলো।
দক্ষিণ ভারতের কিছু পণ্ডিত এবং তাঁদের ভূমিকা
১. শায়খ জাইনুদ্দীন মাখদুম (১৫৩১–১৫৮৩, মালাবার, কেরালা)
দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে শায়খ জাইনুদ্দীন মাখদুম সাগরী এক অবিস্মরণীয় নাম। ১৫৩১ সালে কেরালার পন্নানি অঞ্চলে জন্ম নেওয়া এই আলেম ছিলেন মাখদুম পরিবারভুক্ত—যে পরিবার ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও সমাজ সংস্কারে অসামান্য অবদান রেখেছিল। তিনি কেবল একজন ধর্মীয় আলেমই নন, বরং ছিলেন এক দূরদর্শী নেতা, যিনি উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনের বৌদ্ধিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।
ষোড়শ শতকে মালাবার উপকূলে পর্তুগিজরা বাণিজ্যের অজুহাতে প্রবেশ করে দ্রুত স্থানীয় রাজনীতি ও সমাজে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। তারা মসজিদ ধ্বংস করে, স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্যাতন করে এবং আরব সাগরের বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই সময়েই মাখদুম সাগরী তাঁর সর্বাধিক খ্যাত গ্রন্থ তুহফাতুল মুজাহিদিন (১৫৮৩) রচনা করেন। এই গ্রন্থ শুধু একটি ঐতিহাসিক দলিল নয়; এটি ছিল মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করার আহ্বান এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের ঘোষণা। তিনি এখানে জিহাদের ধর্মীয় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে পর্তুগিজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নৈতিক ও রাজনৈতিক বৈধতা তুলে ধরেন।
মাখদুম সাগরীর প্রভাব শুধু মালাবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর গ্রন্থ আরব বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে, ফলে আরব বণিক ও অটোমান সাম্রাজ্যের সমর্থন লাভে সহায়তা করে। তাঁর চিন্তা দক্ষিণ ভারতের প্রতিরোধ আন্দোলনকে একটি বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বসংলগ্নতা প্রদান করে। তাই তাঁকে শুধু একজন আলেম নয়, বরং একজন মুক্তিকামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক হিসেবে গণ্য করা হয়, যিনি স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন বহু শতক আগেই।
২. টিপু সুলতান (১৭৫০–১৭৯৯, মাইসোর)
“মাইসোরের বাঘ” (Tiger of Mysore) নামে পরিচিত টিপু সুলতান ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভিক ও সর্বাধিক প্রতীকী যোদ্ধাদের একজন। ১৭৫০ সালে কর্ণাটকের দেবনহল্লিতে জন্ম নেওয়া টিপু ছিলেন মাইসোরের শাসক হায়দার আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশব থেকেই তিনি সামরিক প্রশিক্ষণে পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং আধুনিক অস্ত্র ও কৌশলের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরুদ্ধে এক দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।
টিপু সুলতান বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে প্রতিহত করতে হলে আন্তর্জাতিক মিত্রতা অপরিহার্য। তাই তিনি ফরাসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ইউরোপীয় সামরিক প্রযুক্তি ও সংগঠন মাইসোর সেনাবাহিনীতে প্রয়োগ করেন। তাঁর শাসনামলে মাইসোর রাজ্য আধুনিক কামান, রকেট নিক্ষেপণ প্রযুক্তি এবং উন্নত সামরিক কৌশলের জন্য খ্যাতি অর্জন করে।
চারটি আঙ্গলো–মাইসোর যুদ্ধের(১৭৬৭–১৭৯৯) মধ্যে টিপু বিশেষভাবে স্মরণীয় চতুর্থ যুদ্ধের জন্য, যেখানে তিনি ১৭৯৯ সালে শ্রীরঙ্গপট্টনম দুর্গে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া তাঁকে ভারতের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি বীরের আসনে বসিয়েছে।
টিপু সুলতানের অবদান কেবল সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ভূমি সংস্কার, বাণিজ্য উন্নয়ন, ও কৃষি উৎপাদনে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ধর্মীয় সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মন্দির ও মসজিদ উভয়ের উন্নয়নে অনুদান দিয়েছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও আত্মত্যাগ আজও স্বাধীনতার প্রারম্ভিক সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।
৩. সাইয়্যিদ আলাভি তাঙ্গাল (১৭৫২–১৮৪৫, মালাবার)
কেরালার মুসলিম সমাজে সাইয়্যিদ আলাভি তাঙ্গাল ছিলেন শুধু আধ্যাত্মিক নেতা নন, বরং রাজনৈতিক প্রতিরোধেরও এক শক্তিশালী প্রেরণাদাতা। ১৭৪৩ সালে ইয়েমেনে জন্মগ্রহণ করে তিনি মালাবারে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ী হন। উচ্চমানের আরবি শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে তিনি ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন এবং মালাবারের মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য দৃঢ় করেন।
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি যখন দক্ষিণ ভারতে তাদের প্রভাব বিস্তার শুরু করে, তখন স্থানীয় মুসলমানরা নানা নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হন। এ সময় সাইয়্যিদ আলাভি তাঙ্গাল তাঁদেরকে শুধু ধর্মীয় আচার–আচরণে দৃঢ় থাকতে বলেননি, বরং স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব মালাবারের মুসলমানদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে।
বিশেষত, ১৮শ ও ১৯শ শতকের মালাবার বিদ্রোহগুলোর পেছনে তাঁর দিকনির্দেশনা ও প্রেরণা সুস্পষ্টভাবে কাজ করে। স্থানীয় মুসলমানরা তাঁকে তাঁদের আধ্যাত্মিক আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আর তিনি তাঁদেরকে শিক্ষা দেন যে ঔপনিবেশিক শাসন শুধু রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতারও শত্রু।
তাঁর দীর্ঘ আয়ু ও প্রভাবশালী নেতৃত্ব প্রমাণ করে যে তিনি শুধু একজন সাধকই ছিলেন না; বরং উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের এক নীরব স্থপতি, যিনি মুসলিম সমাজকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন।
৪. উমর কুনহিপ্পু হাজী (১৮৩৭–১৮৯১, মালাবার বিদ্রোহ, কেরালা)
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অভিঘাত কেবল উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর প্রভাব ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে। কেরালার মালাবার অঞ্চলে এরই ধারাবাহিকতায় এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কুনহিপ্পু হাজী। তিনি ছিলেন মালাবার বিদ্রোহ (১৮৮৫–১৮৯১)–এর অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁর সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী—একদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, অন্যদিকে জমিদারি প্রথার শোষণ থেকে কৃষকদের মুক্তি।
কুনহিপ্পু হাজী দরিদ্র কৃষক, মজুর ও সাধারণ মুসলমানদের সংগঠিত করেন এবং তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা শুধু সশস্ত্র প্রতিরোধই গড়ে তোলেননি, বরং বিকল্প ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। এ আন্দোলন স্থানীয় মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু কৃষকদেরও একত্রিত করে, যা মালাবারের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের প্রতিফলন।
যদিও ব্রিটিশরা অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে এবং কুনহিপ্পু হাজী শেষ পর্যন্ত শহীদ হন, তাঁর সংগ্রাম দক্ষিণ ভারতের জনগণের মনে এক অদম্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলন প্রমাণ করে যে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের ছিল না; বরং এটি ছিল সমগ্র জাতির সম্মিলিত সংগ্রাম।
৫. মোহাম্মদ আবদুর রহমান (১৮৯৮–১৯৪৫, কেরালা)
কেরালার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মোহাম্মদ আবদুর রহিমান একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি শুধু একজন সাংবাদিকই নন, বরং ছিলেন এক নিবেদিতপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মী ও জননেতা। ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণকারী রহিমান অল্প বয়সেই স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হন এবং কলমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ও সম্পাদনা করতেন ‘আল–আমিন’ নামক পত্রিকা, যা দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক জাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০–১৯২২) ও খিলাফত আন্দোলনের (১৯১৯–১৯২৪) পক্ষে নিরলসভাবে প্রচার চালান।
তাঁর লেখনী ছিল স্পষ্টবাদী ও আপসহীন। এর ফলেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার করে এবং কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু কারাবাসেও তিনি তাঁর চিন্তা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। বরং তাঁর সংগ্রামী চেতনা কেরালার তরুণ সমাজকে স্বাধীনতার লড়াইয়ে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।
রহিমান শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তিনি কেরালার মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক সংস্কারের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি মানসিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটানো। ১৯৪৫ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলেও, তাঁর অবদান দক্ষিণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অমোচনীয় অধ্যায় হয়ে আছে।
৬. ভি. এম. ওবায়দুল্লাহ (১৮৯৮–১৯৭১, তামিলনাড়ু)
তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বে ভি. এম. ওবায়দুল্লাহ ছিলেন এক বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী কণ্ঠ। ১৮৯৮ সালে জন্ম নেওয়া এই প্রাজ্ঞ নেতা অল্প বয়স থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস–এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে মুসলিম সমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য কাজ করেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের পক্ষে নিরলস প্রচেষ্টা, যা দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেয়।
ওবায়দুল্লাহ ছিলেন কেবল রাজনীতিবিদই নন, বরং এক শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারকও। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের প্রকৃত অগ্রগতি কেবলমাত্র আধুনিক শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই তিনি তামিল মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং তরুণদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।
তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলো মুসলিম যুবসমাজকে স্বাধীনতার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে অনুপ্রাণিত করত। তিনি যুক্তি দিতেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি মুসলিম সমাজকে আধুনিক চিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং জাতীয় সংহতির পথে অগ্রসর হতে হবে।
১৯৭১ সালে তাঁর মৃত্যু হলেও, ভি. এম. ওবায়দুল্লাহ আজও স্মরণীয় একজন নেতা—যিনি দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর জীবন প্রমাণ করে যে শিক্ষা, ঐক্য ও রাজনৈতিক সচেতনতার সমন্বয়ই একটি জাতিকে প্রকৃত মুক্তির পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম।
৭. সাইয়্যিদ আহমদুল্লাহ কাদেরী (১৯০৯–১৯৮৫, হায়দরাবাদ)
হায়দরাবাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সাইয়্যিদ আহমদুল্লাহ কাদেরী ছিলেন মুসলিম সমাজে আধুনিকতার অগ্রদূত। ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণকারী কাদেরী অল্প বয়স থেকেই উর্দু সাহিত্য, ইতিহাস ও সাংবাদিকতার প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শে প্রভাবিত হন।
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কাদেরীর প্রধান হাতিয়ার ছিল তাঁর কলম। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লিখে মুসলমানদের স্বাধীনতার পক্ষে সংগঠিত হতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর লেখনীতে যেমন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের স্পষ্ট আহ্বান শোনা যেত, তেমনি শিক্ষার গুরুত্ব ও সামাজিক সংস্কারের কথাও বারবার প্রতিফলিত হতো। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন—রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, যদি সমাজ জ্ঞান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় মুক্ত না হয়।
স্বাধীনতার পর কাদেরী হায়দরাবাদে শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাহিত্য সংগঠন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয় থেকে মুসলিম সমাজে আধুনিকতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের মুসলিম যুবকদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর লেখনী ও বক্তৃতা বিশেষ ভূমিকা রাখে।
১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু হলেও, সাহিত্য, শিক্ষা ও মুক্তচিন্তার অঙ্গনে তাঁর উত্তরাধিকার আজও দক্ষিণ ভারতীয় সমাজকে অনুপ্রেরণা জোগায়।
৮. মাকদুম আলী মহিউদ্দীন (১৯০৮–১৯৬৯, হায়দরাবাদ)
হায়দরাবাদের প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মাকদুম আলী মহিউদ্দীন ছিলেন ভারতীয় সাহিত্য ও রাজনীতির এক অনন্য চরিত্র। ১৯০৮ সালে হায়দরাবাদের আজমপুরায় জন্ম নেওয়া মাকদুম শৈশব থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে কবিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। তাঁর কবিতায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবি প্রবলভাবে প্রতিফলিত হয়।
মাকদুম হায়দরাবাদী মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক জাগরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি “আন্দোলন–এ–হায়দরাবাদ”–এর সঙ্গে যুক্ত থেকে নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম চালান। তাঁর সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্ম মুসলিম সমাজকে উপনিবেশবিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে শ্রমজীবী, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও বক্তৃতা উপহার দেন।
স্বাধীনতার পরে মাকদুম প্রগতিশীল লেখক সংঘের (Progressive Writers’ Association) অন্যতম নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সাহিত্য শুধু রাজনৈতিক বার্তা বহন করেনি, বরং মানবমুক্তি, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নও তুলে ধরেছিল। তিনি দক্ষিণ ভারতের মুসলিম যুবকদের জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।
১৯৬৯ সালে তাঁর মৃত্যু হলেও, কবিতা ও সাংবাদিকতায় তাঁর বিপ্লবী উত্তরাধিকার আজও দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়ের চেতনাকে জাগিয়ে রাখে।
উপসংহার
দক্ষিণ ভারতের আলেম ও নেতাদের অবদান প্রমাণ করে যে ভারতের স্বাধীনতার লড়াই কেবল উত্তর ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা দেখি, উত্তর ও দক্ষিণ মিলেই গড়ে উঠেছিল একটি সর্বভারতীয় সংগ্রাম। মালাবারের শায়খ জাইনুদ্দীন মাখদুম তাঁর তুহফাতুল মুজাহিদিন–এ পর্তুগিজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে জিহাদের আহ্বান জানান, সেটি যেমন মুসলিম প্রতিরোধের বৌদ্ধিক ভিত্তি তৈরি করেছিল, তেমনি মাইসোরের “বাঘ” টিপু সুলতান তাঁর বীরত্বগাথা দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের এক কিংবদন্তি অধ্যায় রচনা করেছিলেন। কেরালার আবদুর রহিমানের কলমে ও আন্দোলনে আমরা খুঁজে পাই মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক জাগরণ এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ। অন্যদিকে তামিলনাড়ুর ওবায়দুল্লাহ মুসলিম যুবকদের আধুনিক শিক্ষা ও জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। হায়দরাবাদের সাইয়্যিদ আহমদুল্লাহ কাদেরী ও মাকদুম আলী মহিউদ্দীন সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও বিপ্লবী লেখনীর মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপ্নকে গণমানুষের চেতনায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।
এই আলেম ও নেতাদের সংগ্রাম প্রমাণ করে যে স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল এক বহুমাত্রিক ধারা—যেখানে ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলভেদে ভিন্নতা থাকলেও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। তাঁদের ত্যাগ, সাহস ও আত্মনিবেদন আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল সর্বভারতীয়, সর্বজনীন ও বহুধর্মীয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দক্ষিণ অধ্যায় তাই কেবল অতীতের অংশ নয়, বরং আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের এক অমূল্য সম্পদ। এ ঐতিহ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক মুক্তির নাম নয়, এটি ন্যায়, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক অনন্ত সংগ্রাম।