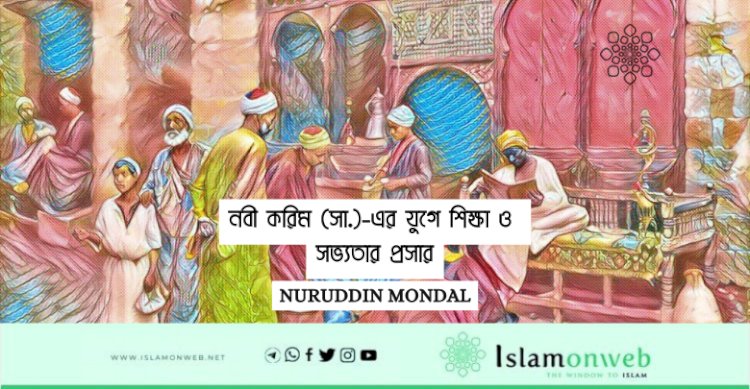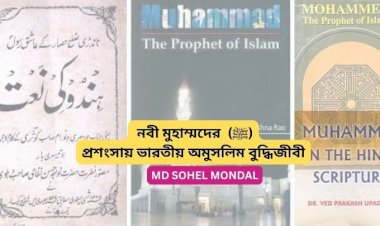নবী করিম (সা.)-এর যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি কেবলমাত্র ইবাদতের উপর নয় বরং জ্ঞান, সভ্যতা, ন্যায়বিচার ও মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার উপরও নির্ভরশীল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেরিতকাল এমন এক সময়ে ঘটেছিল যখন আরব উপদ্বীপে জ্ঞানের আলো প্রায় ছিল না বললেই চলে। সেই প্রেক্ষাপটে জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর আহ্বান এবং অন্যান্য জাতির সঙ্গে জ্ঞানের বিনিময় তাঁর নবুয়তের তাৎপর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। তাঁর বিখ্যাত হাদীস: "اطلبوا العلم ولو بالصين"
(জ্ঞান অর্জন করো, যদিও তোমাকে চীন পর্যন্ত যেতে হয়)—এই বাণী একটি গভীর প্রশ্ন তুলে ধরে: হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি চীনের মতো দূরবর্তী দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন? আর যদি থাকেন, তবে কিভাবে? এই প্রবন্ধে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি, প্রাক-ইসলামি যুগে আরব-চীন বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, নবী করিম (সা.)-এর যোগাযোগজ্ঞান, এবং তাঁর সময়ে আরবের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনা করব। সেই সঙ্গে তুলে ধরা হবে ঐতিহাসিক সূত্র ও প্রাচীন ইসলামী পাণ্ডুলিপির আলোকে নবুয়তের যুগে জ্ঞানের আদান-প্রদানের ভূচিত্র।
প্রাক-ইসলামি যুগে আরব-চীন সংযোগ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
প্রথমেই একটি প্রশ্ন সামনে আসে: নবী করিম (সা.) এমন একটি দেশের কথা কীভাবে জানলেন, যা তাঁর জন্মস্থান মক্কার একেবারে বিপরীত দিকে অবস্থিত? চীন এবং আরবের মধ্যকার বিশাল ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সরাসরি যোগাযোগের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু যদি আমরা প্রাক-ইসলামি আরব অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাই যে আরবরা চীনের সঙ্গে সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিল। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবু হাসান আল-মাসউদী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মুরুজুয্-যাহাব"–এ উল্লেখ করেন যে, ইসলামপূর্ব যুগেই চীনা বণিকরা সমুদ্রপথে আরব উপদ্বীপে আসতেন, বিশেষ করে ওমান এবং বসরা অঞ্চলে। এই তথ্য নিশ্চিত করে যে, আরবরা চীন সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক লেনদেনও চলত।
আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় "আল-মুহাব্বার" নামে মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-বাগদাদীর লেখা একটি কিতাবে। সেখানে বলা হয়েছে, আরব অঞ্চলের “দিব্বা ” নামক স্থানে প্রতি বছর একটি আন্তর্জাতিক মেলা বসত, যেখানে চীন, ভারত, সিন্ধু, ইরানসহ দূর-দূরান্তের মানুষ সমুদ্রপথে এসে অংশগ্রহণ করত। এই দিকটি বোঝায় যে আরব উপদ্বীপ ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জ্ঞান, পণ্য ও সংস্কৃতির বিনিময় ঘটত।
দিব্বা (دبا): নবুয়তের যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র
আরব অঞ্চলের “দিব্বা” নামক বন্দর ছিল তৎকালীন জাহেলি যুগ এবং নবুয়তের যুগে এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মিলনস্থল। দিব্বা’র গুরুত্ব এমন ছিল যে, ইসলাম গ্রহণের পর নবী করিম (সা.) এই অঞ্চলের জন্য আলাদাভাবে একজন গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। সাধারণভাবে কোনো শহরের জন্য কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোর বাইরে একজন পৃথক প্রশাসক নিয়োগ করা হয় তখনই, যখন সেই অঞ্চলের কূটনৈতিক ও আর্থিক গুরুত্ব বিশেষ হয়। দিব্বা’তে প্রতিবছর মেলায় বিদেশি ব্যবসায়ীদের সমাগমের কারণে এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা জরুরি হয়ে উঠেছিল। এই বন্দর নগরীতে চীন, ভারত, সিন্ধু এবং পারস্য থেকে আগত বণিকরা শুধু ব্যবসার জন্য নয়, বরং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এর ফলে নবী করিম (সা.)-এর সময় চীনের অস্তিত্ব এবং তাদের শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের কথা তাঁর জানা ছিল—এটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ধারণা।
যদিও চীনা বণিকদের আরব উপদ্বীপে আগমনের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান, তবু বহু মুসলিম ঐতিহাসিক ও হাদীস বিশারদগণ প্রশ্ন তুলেছেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে কি কখনো চীনা বণিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন? অথবা সরাসরি কোনো চীনা ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতা করেছেন? এই প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ হাদীস আমাদের সামনে আসে:
"اطلبوا العلم ولو بالصين"
“জ্ঞান অর্জন করো, যদিও তোমাকে চীন পর্যন্ত যেতে হয়” (সূত্র: ইমাম বাইহাকী, শু ‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ১৭৬৩৮; দুর্বল সূত্রসহ বর্ণিত)
এই হাদীসটি যদিও সহীহ নয়, তথাপি এর বিষয়বস্তু ইসলামের শিক্ষাগত দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বহু হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, নবী করিম (সা.) “চীন”-এর মতো দূরবর্তী ও বিশেষভাবে জ্ঞানসমৃদ্ধ অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে তিনি চীনের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।
এছাড়াও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবুয়তের যুগে ইয়েমেন ও ওমানের বন্দরসমূহে চীনা কাপড়, কাঁচ, কাগজ, মসলা ইত্যাদি আমদানি হতো, যা মক্কার অভিজাত বণিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। নবী করিম (সা.)-এর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-এর বাণিজ্য কাফেলাও সিরিয়া ও ইয়েমেন হয়ে বিভিন্ন বিদেশি পণ্যের আদান-প্রদান করত। এই প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে যে, নবী করিম (সা.) সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে চীনা সভ্যতা ও তাদের জ্ঞানচর্চার বিষয়ে অবগত ছিলেন।
বাণিজ্য ও জ্ঞানচর্চার পারস্পরিক প্রভাব
আরবরা চিরকালই বিশ্ববাণিজ্যের এক অন্যতম জাতি ছিল। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়া অনুযায়ী মক্কা ছিল একটি নিরাপদ শহর যেখানে চারপাশ থেকে রিজিকের ব্যবস্থা হতো:
” رَبَّنَاۤ اِنِّیۡۤ اَسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُـقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ وَارۡ زُقۡهُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمۡ یَشۡكُرُوۡنَ “
“হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিয্ক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে” । -(সূরা ইবরাহীম: ১৪/৩৭) ।
এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, মক্কা ও মদিনা নগরী বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নবী করিম (সা.)-এর যুগে শিক্ষা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল। তিনি যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে দশজন করে মুসলমানকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন (দ্রষ্টব্য: বদরের যুদ্ধের বন্দিরা)। এই ঘটনা ইসলামি শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। শুধু নিজ জাতির মধ্যেই নয়, বরং বিভিন্ন জাতির বিদ্বান, বণিক ও দূতদের সঙ্গে জ্ঞানবিনিময়ের মাধ্যমে নবী করিম (সা.) আরব সমাজকে এক আন্তর্জাতিক জ্ঞানের কেন্দ্রে রূপান্তর করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে চীনা পণ্ডিত চেন চাও তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, “হিজরি প্রথম শতকেই চীনা নাবিক ও ব্যবসায়ীরা ইসলামী তীরভূমিতে মুসলমানদের সঙ্গে জ্ঞানের আদান-প্রদান শুরু করেছিল।” (Chen Zhao, Muslim-Chinese Encounters in the Early Caliphate, 2003)
এটি প্রমাণ করে যে নবুয়তের যুগে জ্ঞান চর্চার পরিবেশ কেবল আরব সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিল।
চীনের প্রসঙ্গে নবী করিম (সা.)-এর বক্তব্যের তাৎপর্য
“اطلبوا العلم ولو بالصين”—এই কথাটি কোনো কল্পনাবিলাস নয় বরং একটি আদর্শিক নির্দেশনা, যা নবী করিম (সা.) তাঁর উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। তিনি চেয়েছেন তাঁর উম্মত যেন সীমাবদ্ধ মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। চীনের উল্লেখ কেবল ভৌগোলিক বিশালতার প্রতীক নয়, বরং এটি এমন একটি দেশকে বোঝায় যাকে তৎকালীন বিশ্ব জ্ঞান, কারুশিল্প ও শিল্পকলার কেন্দ্র হিসেবে চিনত। নবী করিম (সা.) সেই দেশটির কথা বলে মূলত মুসলমানদের জ্ঞানের উৎস সন্ধানের এক বিশ্বজনীন নির্দেশনা দিয়েছেন। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা শিক্ষাকে কেবল সাংস্কৃতিক বা সামাজিক চাহিদা হিসেবে নয়, বরং এক ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরে। কুরআনের প্রথম ওহিই নাজিল হয় শিক্ষা বিষয়ক:
"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"
“পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন” । — [সূরা আল-আলাক: ৯৬:১]
এই আয়াত দ্বারা ইসলামে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। নবী করিম (সা.)-এর বহু হাদীসেও দেখা যায়, তিনি শিক্ষাকে ঈমানের অংশ, ইবাদতের মাধ্যম এবং জিহাদের রূপ হিসেবে বিবেচনা করতেন। নবী করিম (সা.)-এর শিক্ষাগত নীতিমালার একটি বিশেষ দিক ছিল—ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন। তিনি শুধুমাত্র কুরআন ও শরীয়ত জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেননি, বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা, কৃষি, গণনা, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। চীনের প্রসঙ্গেও তিনি যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—সেটি ছিল এক পার্থিব কিন্তু উচ্চস্তরের জ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যম। এটি এক ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানচর্চার আহ্বান যা ধর্মীয় ভাবধারার পরিপন্থী নয়, বরং সহায়ক।
বর্তমান বৈশ্বিক শিক্ষাব্যবস্থায় একাধিক সংকট বিদ্যমান—মূল্যবোধের অবক্ষয়, একমাত্রিক জ্ঞানার্জন, আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার অভাব ইত্যাদি। এই পটভূমিতে নবুয়তি যুগের শিক্ষার আদর্শ আমাদের সামনে একটি প্রগতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে: নবী করিম (সা.)-এর যুগে জ্ঞানচর্চা আরবের সীমার বাইরে চীন, রোম ও পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি আজকের “গ্লোবাল লার্নিং” ধারণার পূর্বসূরি। কেবল তথ্যভিত্তিক নয়, বরং মূল্যভিত্তিক শিক্ষাই ছিল ইসলামের মূল ভিত্তি। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রের চরিত্র গঠন, নৈতিকতা উন্নয়ন এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখত। নবী করিম (সা.) অনেক সাহাবীকে কৃষি, হস্তশিল্প, ও চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। এই শিক্ষা জীবিকানির্ভর এবং আত্মনির্ভরশীলতা গঠনে সহায়ক ছিল। কেবল মুখস্থ নয়, বরং চিন্তা, গবেষণা এবং আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ ছিল মূল উদ্দেশ্য।
এই গবেষণার আলোকে বলা যায় যে, ইসলামে শিক্ষার ইতিহাস কেবল ধর্মীয় অনুশীলনের এক অনুষঙ্গ নয়, বরং একটি বৈশ্বিক আন্দোলনের সূচনা। নবী করিম (সা.)-এর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সেই যুগে এক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার সূচনাপর্ব ছিল। বর্তমানে, যখন শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকতার ভেতর বন্দি হয়ে গেছে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় স্পষ্ট, তখন ইসলামের এই জ্ঞানভিত্তিক বৈশ্বিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে পর্যালোচনার দাবি রাখে। ইসলামি শিক্ষার মূল চেতনা—জ্ঞান, নীতি ও মানবতা—আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে, যদি তা সঠিকভাবে অনুসৃত হয়।
উপসংহার
নবী করিম (সা.)-এর যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার কেবল একটি ধর্মীয় নবযুগের সূচনা নয়, বরং একটি বৈশ্বিক ও নৈতিক বিপ্লবেরও প্রতিচ্ছবি। প্রাক-ইসলামি আরবের জাহেলি অন্ধকারে তিনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, জ্ঞানার্জন একটি ঐশী নির্দেশ—যা জাতি, ভাষা বা ভূগোলের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। "জ্ঞান অর্জন করো, যদিও তোমাকে চীন পর্যন্ত যেতে হয়"—এই উক্তির মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, তেমনি শিক্ষার সর্বজনীনতা ও প্রাসঙ্গিকতার কথা স্পষ্ট করেছেন। চীনসহ বহির্বিশ্বের সঙ্গে আরবের ঐতিহাসিক সংযোগ, বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে, নবুয়তি যুগের শিক্ষা-দর্শন ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক, ব্যবহারিক ও বহুমাত্রিক। আর এ কারণেই তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা ও সভ্যতা আজও সময়োপযোগী, এমনকি আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার জন্যও এক আদর্শ। বর্তমান বিশ্বের মূল্যবোধ-সংকট ও একমাত্রিক শিক্ষানীতির প্রেক্ষাপটে নবী করিম (সা.)-এর শিক্ষা-দর্শন নতুন দিশা দেখাতে পারে। তাঁর আদর্শ আমাদের শিখিয়েছে—শিক্ষা শুধু দুনিয়ার সাফল্যের সোপান নয়, বরং আত্মিক উৎকর্ষ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিকতার ভিত্তিপ্রস্তর। সুতরাং, আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতায়ও, নবুয়তি যুগের শিক্ষাব্যবস্থা একটি সময়োপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, যা আমাদের শুধু ইতিহাস নয়, ভবিষ্যত গড়ার পথও দেখায়।
References:
- কুরআন মাজীদ, সূরা আল-আলাক, আয়াত ১
- হাদীস: শু‘আবুল ঈমান – ইমাম বাইহাকী
- ابن هشام، سيرة النبوية
- চেন চাও, Muslim-Chinese Encounters in the Early Caliphate, 2003
- মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, Rasulullah in Trade and Diplomacy, 1970
- البخاري، كتاب العلم
- ফাতহুল বারী – ইবনে হাজার আসকালানী
নুরুদ্দিন মন্ডল দারুল হুদা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের একজন গবেষণা পণ্ডিত। তার বিস্তৃত এবং অনুসন্ধিৎসু চিন্তাভাবনার জন্য পরিচিত, নুরুদ্দিন ধর্ম, সমাজ এবং বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের সংযোগস্থলে প্রশ্নগুলির সাথে গভীরভাবে জড়িত।