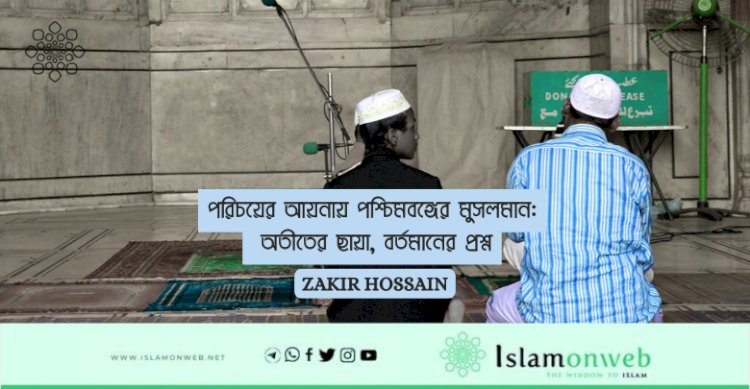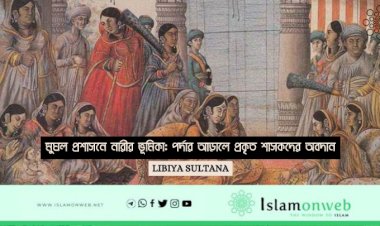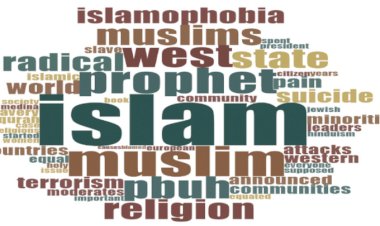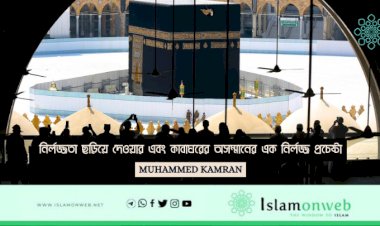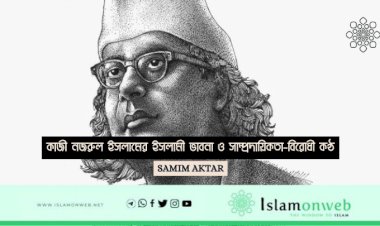পরিচয়ের আয়নায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান: অতীতের ছায়া, বর্তমানের প্রশ্ন
ভূমিকা
একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি — বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস কি কেবল মসজিদ, মাদ্রাসা আর পাঞ্জাবির গল্প? নাকি তার চেয়ে অনেক গভীর, অনেক বিস্তৃত?
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কথা বললেই, একটা দ্বিধান্বিত চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় — এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু জানি কি, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ-ই মুসলমান? সহজ ভাষায়, প্রতি ৪ জনের ১ জন। এটা কেবল সংখ্যা নয়, বরং এক বিশাল সংস্কৃতি, ইতিহাস আর সংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় একটি জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও এদের পরিচয় যেন কোথাও ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে নাম থাকে মুঘল সম্রাটদের, কিন্তু বাংলার কৃষক মুসলমান বা ফরাক্কার ধারে বাস করা সেই ছোট্ট ছেলেটার গল্প আমাদের জানা থাকে না। রাজনীতি যাদের নিয়ে তুমুল বিতর্ক করে, তাদের চিনে না নাগরিক সমাজ। মিডিয়ায় তাদের উপস্থিতি প্রায় শূন্য, আর সরকারি পরিসংখ্যানে তারা কেবল পরিসংখ্যান।
তবে এই সংখ্যাটি শুধু ভোট ব্যাঙ্কের হিসাব নয়, এটা ইতিহাসের চাপা পড়া ধুলোর নিচে লুকিয়ে থাকা গল্প, সংস্কৃতি আর এক প্রজন্মের আকুতি — “আমরা আছি, ছিলাম, থাকবো; কিন্তু আমাদের চিনতে শেখো”।
এই প্রবন্ধে আমরা সেই ২৭ শতাংশ মানুষকে নতুন চোখে দেখার চেষ্টা করব — ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে — যেন বোঝা যায়, এদের পরিচয় সংকট কেবল আত্মপরিচয়ের নয়, বরং রাষ্ট্র, সমাজ এবং আমাদের সকলের এক গভীর অসচেতনতার প্রতিফলন।
দীর্ঘ ইতিহাস, তবুও পরিচয়ের সংকট
পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের ইতিহাস অনেক পুরনো। বহু বছর ধরে এই অঞ্চলে মুসলমানরা শুধু বসবাসই করেননি, বরং বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক, গান, কবিতা—সব কিছুর মধ্যেই তাদের অবদান আছে। মুর্শিদাবাদ একসময় বাংলার রাজধানী ছিল মুসলিম শাসকদের সময়ে। বাংলার কৃষিকাজ, কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য—সবখানেই মুসলমানদের বড় ভূমিকা ছিল।
তবুও আজ অনেকেই এসব কথা জানে না, কারণ স্কুলের বই বা টেলিভিশনে এসব নিয়ে খুব কমই বলা হয়। অনেক সময় মুসলমান মানেই শুধু "ধর্ম" বা "অন্যরকম" পরিচয় মনে করা হয়, যেন তারা ইতিহাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এই কারণেই অনেক মুসলমান এখন নিজের ইতিহাস বা পরিচয় নিয়ে দ্বিধায় ভোগেন। তাঁরা জানেন না—তাদের পূর্বপুরুষরা এই মাটির জন্য কী করেছে, কীভাবে জীবন কাটিয়েছে, কীভাবে দেশ গড়েছে।
আর এই ভুলে যাওয়া ইতিহাসই আজ অনেক মুসলমানকে পরিচয় সংকটে ফেলেছে—নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন তোলে, "আমি এই বাংলার কতটা অংশ?"
যে মাটি যুগের পর যুগ ধরে মুসলমানদের ঘাম আর পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে, সেখানে আজ তাদের পরিচয় নিয়েই কেন এত প্রশ্ন? এতদিনের অবদান সত্ত্বেও কেন তারা বারবার প্রমাণ করতে বাধ্য হন যে, তারা এই দেশেরই অংশ? এই সংকট হঠাৎ করে আসেনি, এর শিকড় অনেক গভীরে। দেশভাগের পর অনেক মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেও, যারা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন—তাদের চোখে পড়ে এক অদৃশ্য দেয়াল। এদেশের নাগরিক হয়েও, তাদের দিকে তাকানো হয় সন্দেহের চোখে। ধীরে ধীরে, একধরনের ভয়, সংকোচ আর একাকীত্ব তৈরি হতে থাকে—যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে চলেছে।
রাজনীতি এই সংকটকে কখনও কমায়নি, বরং অনেক সময় বাড়িয়েই দিয়েছে। একদিকে ভোটের সময় মুসলমানদের ‘ভোটব্যাংক’ বলা হয়, অন্যদিকে বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের দেশপ্রেম, ভাষা, এমনকি খাদ্যাভ্যাস নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। আর সামাজিকভাবে—তাদের আলাদা করে দেখা, কখনও চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়া, কখনও ‘অন্যরকম’ হিসেবে বেঁচে থাকা—এই অভিজ্ঞতা অনেক মুসলমানের পরিচয়ে একটা অস্পষ্টতা তৈরি করেছে।
মুঘল ও নবাব আমলে মুসলমানদের শাসন ও সমাজে অবস্থান
পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের ইতিহাস শুরু হয় কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং সামাজিক, প্রশাসনিক এবং সাংস্কৃতিক অবদান নিয়েও। মুঘল আমল, বিশেষ করে ১৬শ ও ১৭শ শতকে, মুসলমানরা শুধু শাসক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, তাঁরা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, এবং নগর সংস্কৃতির ভিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।
মুঘলদের অধীনস্থ বাংলা একসময় ‘সুবাহ বাংলা’ নামে পরিচিত ছিল, যার রাজধানী ছিল ধাক্কা (বর্তমানে ঢাকা)। পরবর্তীতে যখন মুর্শিদ কুলি খাঁ নবাব নিযুক্ত হন, তখন তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেন মুর্শিদাবাদে — যা পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম প্রশাসনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই মুর্শিদাবাদ শহর শুধু রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল না, এটি ব্যবসা, সংস্কৃতি ও ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও বিকশিত হয়।
নবাবদের শাসনে জমি ব্যবস্থাপনায় মুসলমান জমিদাররা যেমন ভূমিকা রাখতেন, তেমনি হিন্দু জমিদারদের সঙ্গেও ছিল সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। বাংলার ঐতিহাসিক revenue farming system বা ijaradari system-এ মুসলিম ও হিন্দু, উভয় সম্প্রদায়ই অংশগ্রহণ করেছিল — যা প্রমাণ করে যে তখনকার সমাজ কাঠামো ছিল বহুত্ববাদী ও সহযোগিতামূলক।
এছাড়া, সড়ক, মসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা নির্মাণের মধ্য দিয়ে মুসলমান শাসকরা শুধুমাত্র ধর্ম নয়, সামাজিক পরিকাঠামো গঠনের কাজেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদে এখনও যেসব স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়—হাজারদুয়ারি, কাটরা মসজিদ, নিসারপুর বাগান—তা সেই ইতিহাসেরই নীরব সাক্ষী।
তবে এটা ভুললে চলবে না যে, এই শাসন আমল কেবল মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য ছিল না। বরং প্রশাসনিক দক্ষতা, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে সমগ্র বঙ্গ অঞ্চলের উন্নতি হয়েছিল। মুঘল ও নবাবদের আমলে যে সমন্বিত সমাজ তৈরি হয়েছিল, তা-ই পরে বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ কাঠামোর ভিত হিসেবে কাজ করে।
ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া ও বিভাজনের রাজনীতি
মুঘল শাসনের পরে যখন ব্রিটিশরা বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণ করে (১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর), তখন বাংলার মুসলমানদের জীবনে এক বড় পরিবর্তন শুরু হয়। যারা একসময় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা হেরে যেতে থাকেন নতুন শাসকের কাছে। কারণ ব্রিটিশরা ক্ষমতায় এসেই মুসলমানদের দেখেছিল সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে—যারা সামরিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে সংঘবদ্ধ হবার সক্ষমতা রাখে।
এরপর থেকে ব্রিটিশরা মুসলমানদের প্রশাসন, শিক্ষা, এমনকি ব্যবসার জগৎ থেকেও একরকম বাদ দিয়ে দেয়। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম, কারণ তারা ধর্মীয় কারণে ইংরেজি পড়ায় আগ্রহী ছিলেন না, আবার ব্রিটিশরাও তাঁদের প্রতি বিমুখ ছিল। এই সুযোগে হিন্দু সমাজ অনেক আগে থেকেই আধুনিক শিক্ষায় যুক্ত হয়ে যায়, বিশেষ করে কলকাতাকেন্দ্রিক নতুন সমাজ গঠনে। আর মুসলমানদের এক বড় অংশ তখনও গ্রামাঞ্চলে—ধর্মীয় শিক্ষা, কৃষিকাজ আর ছোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে একরকম সামাজিক ও শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা গড়ে ওঠে।
এর মধ্যে ব্রিটিশরা তাদের ‘divide and rule’ বা "বিভক্ত করে শাসন করো" নীতি চালু করে। তারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে তুলতে শুরু করে—কারও পক্ষে যায়, তো কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা ভয় সৃষ্টি করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ তার বড় উদাহরণ, যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা আলাদা করা হয়, পরে আবার তীব্র প্রতিবাদে তা বাতিলও হয়। এসব ঘটনা মুসলমানদের রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে তোলে—তারা বুঝতে থাকে, এই দেশে তাদের অস্তিত্ব অনেকটা কাঁচের মত—ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা সর্বদা থাকে। এই পশ্চাৎপদতা শুধু আর্থিক বা শিক্ষাগত ছিল না, ছিল আত্মবিশ্বাসের দিক থেকেও। মুসলমানরা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে “বিচ্ছিন্ন” ভাবতে শুরু করে—এই বাংলায় থেকেও যেন তারা ‘পুরোপুরি’ আপন নয়।
বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫): বিভক্তির রাজনীতি না কি মুসলিম জাগরণের সূচনা?
১৯০৫ সাল। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল, বাংলা প্রদেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে—পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা। পূর্ব বাংলা হবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা থাকবে সংখ্যায় বেশি। এটাকেই আমরা চিনি "বঙ্গভঙ্গ" নামে।
এই ঘোষণায় হিন্দু সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দুরা একে "বাংলা জাতির টুকরো করে দেওয়া" হিসেবে দেখলেন, এবং শুরু হল তীব্র আন্দোলন—স্বদেশি আন্দোলন। কিন্তু এর উল্টোপিঠে মুসলমান সমাজের বড় একটি অংশ এই বিভাজনকে আশার আলো হিসেবে দেখেছিল।
কারণ, পূর্ব বাংলা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল—না ছিল প্রশাসনিক গুরুত্ব, না উন্নয়ন। ঢাকায় যখন নতুন করে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে, তখন সেখানকার মুসলমানরা মনে করলেন, "অবশেষে আমাদের কথা শোনা হচ্ছে"। মাদ্রাসা, কলেজ, হাসপাতাল—সবকিছু ঢাকায় গড়ে উঠতে লাগল, আর মুসলমানরা একধরনের স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে শুরু করলেন।
তবে এই আশাবাদী মনোভাব বেশি দিন টিকল না। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে দেয় ব্রিটিশ সরকার—হিন্দুদের চাপে পড়ে। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নেয় এক গভীর অসন্তোষ ও হতাশা।
তাদের মনে প্রশ্ন জাগে—"আমাদের চাওয়া কি কেউ শুনবে না? আমরা কি শুধুই সংখ্যা?"
এই ঘটনার মধ্য দিয়েই মুসলমান সমাজে আলাদা রাজনৈতিক চেতনা তৈরি হয়। অনেক ইতিহাসবিদ বলেন, বঙ্গভঙ্গই ছিল ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ গঠনের পেছনের অন্যতম চালিকা শক্তি। মুসলমানরা বুঝে যান, তাঁদের অধিকার কেবল ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিকভাবেও সংগঠিত হওয়া দরকার।
বঙ্গভঙ্গ তাই কেবল একটা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল না—এটি ছিল মুসলিম জনগণের আশা, সম্ভাবনা এবং পরে আবারও সেই আশা ভেঙে যাওয়ার কাহিনি।
দেশভাগ (১৯৪৭): বিভাজনের দাগ আর মুসলমানদের নতুন সংকট
১৯৪৭ সাল—ভারত স্বাধীন হলো, কিন্তু সেই স্বাধীনতা এল একটা বড় রকমের ব্যথা নিয়ে। ভারত আর পাকিস্তান—দুটি আলাদা রাষ্ট্র তৈরি হলো ধর্মের ভিত্তিতে। এ ছিল ইতিহাসের অন্যতম বড় মানবিক বিপর্যয়, যেখানে কোটি কোটি মানুষ বাধ্য হয় নিজের জন্মভিটে ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে।
বাংলার ক্ষেত্রেও ঘটল একই ঘটনা—পূর্ব বাংলা গেল পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ), আর পশ্চিম বাংলা রয়ে গেল ভারতের অংশ হিসেবে। কিন্তু সমস্যা হল, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলেও সব মুসলমান তো পাকিস্তানে যাননি। অনেকেই থেকে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে—কারণ এটাই ছিল তাদের জন্মভূমি, পূর্বপুরুষদের কবর এখানে, জমি-জিরেত, ভাষা, সংস্কৃতি সবই এই বাংলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু যারা থেকে গেলেন, তাদের জন্য শুরু হল এক নতুন যুদ্ধ—নিজের পরিচয় টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ।
অনেকেই তখন সন্দেহের চোখে দেখত পশ্চিমবঙ্গে থাকা মুসলমানদের—“ওরা থেকে গেল কেন? দেশভাগ তো ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে!” এ রকম প্রশ্ন যেন অদৃশ্য দেয়াল তুলে দিল সমাজে। বহু জায়গায় মুসলমানরা সম্পত্তি হারালেন, ‘এনিমি প্রপার্টি’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল বহু ঘরবাড়ি। অনেকেই উদ্বাস্তু হয়ে পড়লেন নিজ দেশে। তাদের সন্তানদের অনেকেই আজো জানে না—তাদের দাদু-নানারা কেমন আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন। একদিকে পরিচয় টিকিয়ে রাখা, অন্যদিকে টিকে থাকার সংগ্রাম—এই দ্বৈত চাপে পড়ে মুসলিম সমাজের বড় অংশ চুপ হয়ে গেল, নিজেকে গুটিয়ে নিল। এই মানসিক সংকট—“আমি কি এই দেশের সম্পূর্ণ অংশ, না একফালি সন্দেহ?”—এখনো অনেকের মধ্যে বয়ে চলে।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকরিতে পিছিয়ে থাকা: সাচার রিপোর্টের আয়নায় মুসলমানদের বাস্তবতা
দেশভাগের এত বছর পরেও যদি দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে অনেক মুসলমান পরিবার এখনো প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী তৈরি করতে লড়ছে, তাহলে বুঝতে হবে—কোনো একটা জায়গায় বড় ধরনের গলদ থেকেই গেছে। ২০০৬ সালে ভারত সরকার গঠন করে "সাচার কমিটি", যার কাজ ছিল—দেশজুড়ে মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করা। এই কমিটির রিপোর্ট ছিল চোখ খুলে দেওয়ার মতো।
কী বলা হয়েছিল সেখানে?
মুসলমানদের শিক্ষার হার, জাতীয় গড়ের চেয়েও নিচে।
সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ২.৫% থেকে ৪.৯%—যেখানে জনসংখ্যার হার অনেক বেশি।
শহরে বসবাসকারী মুসলমানদের দারিদ্র্য হার ছিল প্রায় ৩৮%।
অনেক মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল বা রাস্তাঘাটের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই।
এমনকি বলা হয়েছিল, মুসলমানদের অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে দলিত সম্প্রদায়ের থেকেও পিছিয়ে।
পশ্চিমবঙ্গেও এই চিত্র খুব একটা আলাদা নয়। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরের মতো মুসলিম-প্রধান জেলাগুলোতে দেখা যায়—স্কুল ড্রপআউট হার বেশি, মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ কম, আর চাকরির সুযোগ নগণ্য। বহু পরিবারের বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার বদলে এখনো ইটভাটায় কাজ করে বা ফুটপাথে দোকান দেয়।
কেন এমনটা হচ্ছে?
এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে—দীর্ঘদিনের অবহেলা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, নীতি প্রণয়নে বাস্তব না বোঝা, আবার সমাজের মধ্যেও একধরনের "আমরা বঞ্চিত" মানসিকতা গেঁথে গেছে, যেটা থেকে বেরিয়ে আসাও কঠিন। তবে এটা পরিষ্কার—এই পশ্চাৎপদতা কেবল আর্থিক না, আত্মবিশ্বাস, সম্মান আর স্বপ্ন দেখার অধিকারেও বড় রকমের ক্ষয় তৈরি করেছে।
রাজনীতি আর ভোট: মুসলমান মানেই ভোটব্যাংক?
পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলো বহু বছর ধরে মুসলমানদের দেখেছে একটা ভোটব্যাংক হিসেবে—মানে, এমন একটা বড় ভোটার গোষ্ঠী, যাদের ভোট একদল একসাথে পায়, কিছু প্রতিশ্রুতি আর আবেগের কথা বলে।
নির্বাচনের সময় অনেক নেতা মুসলমানদের নিয়ে কথা বলেন—কখনও বলেন “আপনারা আমাদের ভাই”, কখনও বলেন “আপনাদের নিরাপত্তা রক্ষা করব”, আবার কখনও বলেন “আপনাদের জন্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন হবে”। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই সব কথা কতটা বাস্তব হয়ে ওঠে?
বাস্তবতা কী বলছে?
পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২৭%। এত বড় ভোটার গোষ্ঠী হওয়ার পরও তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা খুবই কম।
অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এখনো ভাল স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল বা রাস্তা নেই।
সাচার কমিটির রিপোর্ট (২০০৬) বলেছে—ভারতে মুসলমানদের অবস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দলিতদের থেকেও।
ভোট পাওয়া গেলেও উন্নয়ন কেন নেই?
কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো মুসলমানদের শুধু ভোটের সময় মনে রাখে। উন্নয়নের নামে যা কিছু হয়, তা অনেক সময় প্রতীকী—কিছু মাদ্রাসা, কিছু অনুদান, বা কোনও নেতার ছবি সহ কিছু প্রকল্প।
কিন্তু আসল সমস্যাগুলো—চাকরি, আধুনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সুযোগ, আইনি নিরাপত্তা—সেগুলো নিয়ে কাজ হয় না।
এর ফলে মুসলমানদের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক ধরনের হতাশা। অনেকেই মনে করেন—“আমরা শুধু ভোট দেওয়ার জন্যই জরুরি, সম্মানের জন্য না।”
এইভাবে কি সংকট আরও গভীর যাচ্ছে । মুসলমানরা যখন নিজেদের “ভোটের মানুষ” ভাবতে বাধ্য হন, তখন নাগরিক হিসেবে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তখন ধর্মীয় পরিচয়টাই বড় হয়ে দাঁড়ায়—জাতীয় পরিচয় নয়। আর এখান থেকেই জন্ম নেয় আত্মপরিচয়ের সংকট।
সমাধান
পরিচয়ের সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মুসলমানদের নিজেকে আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে। আর এই কাজের মূল চাবিকাঠি হলো ইসলামী শিক্ষা—যেটা কেবল ধর্মীয় আচার না, বরং নৈতিকতা, জ্ঞান, দায়িত্ববোধ আর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা শেখায়।
ইসলামে বলা হয়েছে—
“আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, যারা জ্ঞান অর্জন করে।” (সূরা মুজাদালা: ১১)
এই জ্ঞানের মধ্যে শুধু কোরআন-হাদিস নয়, আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজচিন্তা, ইতিহাস—সবই পড়তে হবে। কারণ জ্ঞানই হলো সেই অস্ত্র, যা একজন মুসলমানকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, আর আত্মবিশ্বাস থেকেই জন্ম হয় পরিচয়।
আজকের দিনে মুসলিম সমাজের দরকার এমন সব স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার, যেখানে শুধু সিলেবাস শেখানো হবে না—নিজের বিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, আর মানবিক মূল্যবোধ শেখানো হবে। সাথে দরকার শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন—যেগুলো সত্যিকারের নেতৃত্ব গড়ে তুলবে, দান-সাহায্য না করে সক্ষমতা তৈরির কাজ করবে। স্থানীয় পর্যায়ে মুসলিম পাড়া-মহল্লায় ছোট পাঠাগার, যুক্তিবাদী আলোচনা মঞ্চ, স্কলারশিপ ফান্ড—এসবই হতে পারে একেকটা আলো জ্বালানোর জায়গা।
আজকের বিশ্বে একজন মুসলমানকে হতে হবে একই সাথে ভালো নাগরিক আর ভালো মুসলমান।
কোরআনে বারবার বলা হয়েছে ন্যায়বিচার, সততা, প্রতিবেশীর হক আদায় করার কথা—এসবই একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের গুণ। তাই ইসলামী পরিচয় আর নাগরিক পরিচয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং একে অপরকে সমৃদ্ধ করে। যখন একজন মুসলমান ছাত্র জানবে—সে শুধু মুসলিম নয়, সে একজন সচেতন বাঙালি, একজন ভারতীয় নাগরিক—তখনই সে নিজেকে ছোট মনে করবে না। বরং গর্ব নিয়ে বলবে:
“আমি মুসলমান, আমি শিক্ষিত, আমি এই দেশের গর্ব।”
উপসংহার: ইতিহাস থেকে শিক্ষা, পরিচয়ে দৃঢ়তা
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের পরিচয় সংকট কেবল একটি মানসিক অবস্থান নয়—এর শিকড় ছড়িয়ে আছে ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজের গভীরে। দেশভাগ, রাজনৈতিক ব্যবহার, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা—এই সমস্ত কারণ একসঙ্গে মিলেই তৈরি করেছে এই জটিল বাস্তবতা। কিন্তু এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। তার প্রথম শর্ত হলো—নিজেদের ভুল-ত্রুটি বুঝে আত্মসমালোচনা করা, অতীতকে দোষ না দিয়ে বর্তমানকে বদলাতে উদ্যোগ নেওয়া। পরিবর্তন বাইরের কেউ এনে দেবে না—এটা গড়তে হবে ভেতর থেকে, নিজের চেষ্টায়।
এই আত্মগঠনের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে ইসলামী শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ। ইসলাম শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি এক জীবন্ত জীবনবিধান—যা মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল, শিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ ও সহনশীল নাগরিক হতে শেখায়। একজন মুসলমান তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি সমাজ ও দেশের দায়িত্বও পালন করে। আজ দরকার এমন একটি মুসলিম সমাজ—যারা কেবল 'ভোটব্যাংক' নয়, বরং দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে যুক্ত এক সক্রিয় শক্তি। একজন মুসলমান ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, উদ্যোক্তা বা লেখক—যখন গর্ব করে বলতে পারে,
"আমি একজন মুসলমান, আমি একজন নাগরিক, আমি একজন মানুষ" তখনই সত্যিকার অর্থে পরিচয় সংকটের জবাব তৈরি হবে।