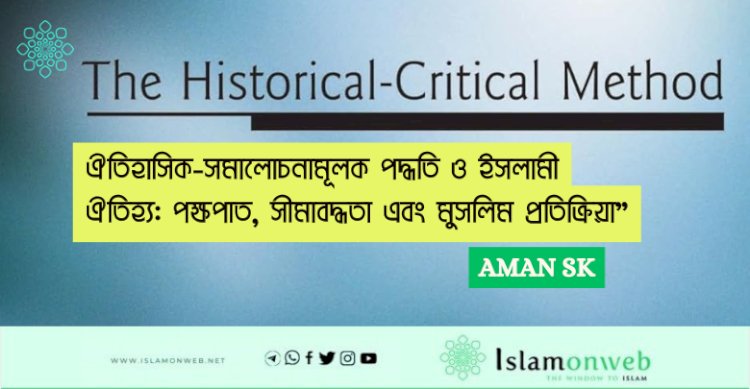ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক পদ্ধতি ও ইসলামী ঐতিহ্য: পক্ষপাত, সীমাবদ্ধতা এবং মুসলিম প্রতিক্রিয়া”
ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক পদ্ধতি (HCM) কী?
ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক পদ্ধতি (HCM) হলো একটি আধুনিক একাডেমিক পদ্ধতি, যা ধর্মীয় ও সাহিত্যিক পাঠ বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পাশ্চাত্য বাইবেল গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং এখন ক্রমশ কুরআন ও ইসলামি ঐতিহ্যের অধ্যয়নেও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতির প্রভাব ধর্মতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে গভীরভাবে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে তিনটি মূল বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে ।
এই পদ্ধতিরটি একটি সাহিত্যিক নথি বা ধর্মগ্রন্থকে ‘ঐতিহাসিকভাবে’ এবং ‘সমালোচনামূলকভাবে’ অধ্যয়ন করে। তাই এর প্রকৃত অর্থ বোঝার জন্য আমাদের দেখা দরকার — এটি কিভাবে ‘সমালোচনামূলকভাবে’ কোনো লেখা বিশ্লেষণ করে এবং কিভাবে ‘ঐতিহাসিকভাবে’ করে।
HCM একটি ‘সমালোচনামূলক’ পদ্ধতি হিসেবে
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ব্যাখ্যা করেছেন — কোনো সাহিত্যিক লেখাকে সমালোচনামূলকভাবে বোঝার মানে হলো, তার উৎস, প্রচার, ও অর্থ নিয়ে প্রচলিত ধারণাগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে, সেই লেখাটির নিজস্ব পাঠ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উৎসের আলোকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাইবেলের মতো ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে প্রাক-আধুনিক দার্শনিক বারুখ স্পিনোজা বলেছিলেন — আমাদের ধারণা করা উচিত নয় যে ধর্মগ্রন্থটি সত্য বা ঐশ্বরিক। বরং এটিকে সাধারণ মানুষের লেখা বই হিসেবে দেখা উচিত, যেখানে কোনো অলৌকিক উপাদান নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে বিশ্লেষণ ও সন্দেহভিত্তিক অধ্যয়ন পদ্ধতির সূচনা হয়।
ডাচ চিন্তাবিদ জ্যাকব পেরিজোনিয়াস (মৃত্যু ১৭১৫) “অসাদৃশ্য নীতি” প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, যদি কোনো ধর্মীয় প্রতিবেদন প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, তবে সেটিই হয়তো বেশি সত্য, কারণ প্রচলিত বিশ্বাস তৈরির জন্য কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিরোধী কিছু লিখবে না।
HCM একটি ‘ঐতিহাসিক’ পদ্ধতি হিসেবে
সিনাই ব্যাখ্যা করেছেন — কোনো পাঠকে ঐতিহাসিকভাবে পড়ার মানে হলো, তার অর্থগুলো এমন হতে হবে যা সেই সময়ের মানুষদের পক্ষে ‘ভাবা’ বা ‘বলা’ সম্ভব ছিল, এবং তা সেই সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বোঝা যাবে, যতটা আমরা আজ পুনর্গঠন করতে পারি।
ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক গবেষণায় ‘ভাবনাযোগ্য’ ও ‘বলনযোগ্য’ শব্দ দুটি বোঝায় — অতীতের ঘটনাগুলো বর্তমানের মতোই প্রাকৃতিক নিয়মে সীমাবদ্ধ ছিল। অতীতের মানুষের মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতাও আজকের মতোই ছিল। তাদের কাজকর্মও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ব্যাখ্যা করা যায়। আরেকটি ধারণা হলো ‘অসামঞ্জস্য বা অপ্রাসঙ্গিকতা’ খোঁজা। অর্থাৎ, যদি কোনো লেখায় এমন কিছু থাকে যা লেখার সম্ভাব্য সময়ের সাথে মেলে না, তবে বোঝা যায় যে লেখাটি আসলে পরবর্তীকালের।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে — যদি HCM অনুযায়ী কোনো পাঠের অর্থ সেই সময়ের মানুষের চিন্তায় ও কথায় সীমাবদ্ধ হতে হয়, তবে আমরা যে ঐতিহাসিক পরিবেশ পুনর্গঠন করি, তা কি আমাদের নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী নয়? যদি এই ধারণাগুলো প্রাকৃতিক বা নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে হয়, তবে সেই পুনর্গঠিত ইতিহাসে আল্লাহর নবী, অলৌকিক ঘটনা, বা ঐশ্বরিক ওহি সত্য হিসেবে স্থান পাবে না। সহজভাবে বলতে গেলে, অতীতকে বোঝার যে মানদণ্ড HCM ব্যবহার করে, সেটিই আগে থেকে ধর্মীয় সত্যের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে দেয়। সিনাই নিজেও পরে এই সমস্যাটি উপলব্ধি করেন।
ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক পদ্ধতি (HCM) কি সত্যিই নিরপেক্ষ?
আমরা ইতিমধ্যে সংক্ষেপে দেখেছি HCM কীভাবে কাজ করে। এখন দেখা যাক এটি সত্যিই নিরপেক্ষ কি না। এই পদ্ধতি তিনটি মূল ধারণার ওপর নির্ভর করে, যেগুলোকে এটি মূল নীতি হিসেবে ধরে নেয় —
১) ঐতিহাসিক উপমার নীতি (Principle of Historical Analogy - PHA),
২) কালভ্রষ্টতা শনাক্তকরণ (Detection of Anachronism - DOA), এবং
৩) অসাদৃশ্যতার নীতি (Principle of Dissimilarity - POD)।
ঐতিহাসিক উপমা ও কালভ্রষ্টতা শনাক্তকরণের নীতিগুলো — যেমন সিনাই নিজেও স্বীকার করেছেন — ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন:
“ঐতিহাসিক উপমার নীতি গ্রহণ করলে বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, তখন ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত ভবিষ্যদ্বাণী বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার পূর্বাভাসের কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। অলৌকিক ঘটনা বা ঈশ্বরীয় হস্তক্ষেপের ধারণাও এভাবে বাদ পড়ে যাবে। অবশ্য এসব ধারণা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু এগুলো আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার মূল ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে।”
অর্থাৎ, ফরাসি দার্শনিক রেনে গ্যুনোঁ (মৃত্যু ১৯৫১) যেভাবে বলেছেন, “এই পুরো পদ্ধতিটি কয়েকটি ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলো আসলে কেবলই পূর্বধারণা ছাড়া কিছু নয়।” এই পদ্ধতির ব্যবহারকারীরা (তা তারা স্বীকার করুন বা না করুন) ধরে নেন যে প্রত্যেক ধর্মীয় মতবাদ প্রকৃতিতে বা বস্তুবাদে ভিত্তি করে শুরু হয়েছে, কারণ তারা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী চিন্তার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেন। ফলে তারা লেখাগুলোকে বারবার এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন, যাতে তা বস্তুবাদী মানসিকতার সঙ্গে মিলে যায়, এবং প্রকৃত অর্থ হারিয়ে যায়।
এইভাবে তারা দুটি বড় ভুল করেন। প্রথম ভুল হলো — উচ্চতর দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা বুঝতে পারেন না যে HCM-এর ভিত্তি যে প্রাকৃতিকতাবাদী চিন্তা, তা বাস্তবতার ভুল ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এই অজ্ঞানতা থেকে তারা এ-ও বোঝেন না যে মানুষের বাস্তবতা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা — অর্থাৎ মেটাফিজিক্যাল বিশ্বাস —ই ইতিহাস ও অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে দেয়। দ্বিতীয় ভুল হলো — এই পদ্ধতির সীমা ভুলভাবে বোঝা। তারা এটিকে সার্বজনীন মনে করে, যেন এটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই ভ্রান্ত ধারণায় তারা বিশ্বাস করেন যে শুধু ভাষাগত দক্ষতার জোরেই তারা যে কোনো বিষয়ের ওপর মত দিতে পারেন, যা আসলে একটি ভুল ধারণা।
আধুনিক পাশ্চাত্যের ইতিহাস-দৃষ্টি, যা ‘উদ্ভববাদী’ প্রাকৃতিকতাবাদে (evolutionistic naturalism) ভিত্তি করে গঠিত, তা আসলে পশ্চিমের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল এবং মোটেও সার্বজনীন নয়। তাই এর যে ধারণাগুলোর ওপর এটি নির্ভর করে এবং যেগুলো ‘প্রাচ্য’ বা ওরিয়েন্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, সেগুলো ভুল বা বিকৃত ফলাফল দেয়। কেউ যদি বলে এটি সার্বজনীন, তাহলে তাকে তার যুক্তি দিতে হবে। কিন্তু এমন কোনো যুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অপরিহার্যতা (necessity), যা কোনো গবেষণায় শতভাগ মতৈক্য দেখালেও প্রমাণিত হয় না। আর যদি বলা হয় যে কেউ বলেনি এটি সার্বজনীন, তাহলে আমাদের বক্তব্যই ঠিক — এবং তখন এটিকে সার্বজনীন হিসেবে ব্যবহারও করা উচিত নয়।
ওরিয়েন্টালিস্টদের ব্যবহৃত DOA (Detection of Anachronism) সব ধরনের সত্যিকারের ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ঘটনাকে আগেই অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। তাদের মতে, এসব ঘটনা পরবর্তীকালের কল্পনা মাত্র, বাস্তবে সেগুলো ঘটতে পারে না। এই ধারণা এক প্রকার নীতি হয়ে দাঁড়ায়, যেমন আমেরিকান দার্শনিক অ্যালভিন প্লান্টিঙ্গা বলেছেন — “কোনো লেখার অর্থ হবে লেখকের মানবিক অভিপ্রায় অনুযায়ী যা তিনি বলতে চেয়েছেন; ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য বা শিক্ষা এখানে বিবেচ্য নয়।”
অসাদৃশ্যতার নীতি (Principle of Dissimilarity) যে ধর্মেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তা সেই ধর্মের প্রচলিত বা প্রথাগত বিশ্বাসের (orthodoxy) মিথ্যাকে ধরে নিয়ে চলে। কারণ এই নীতি বলে, যা কিছু প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে, সেটিই সম্ভবত সত্য — যেহেতু কেউ প্রচলিত বিশ্বাস তৈরি করতে গিয়ে নিজের বিপরীতে কিছু বানাবে না। কিন্তু এই ধারণার প্রমাণ কী, যে একে এমন এক অখণ্ড ও অপ্রতিরোধযোগ্য নীতি হিসেবে ধরা হবে? এটি স্পষ্টভাবেই প্রথাগত বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাত দেখায়, যেখানে তার সত্যতা বা অসত্যতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করার পরিবর্তে আগেই মিথ্যা ধরে নেওয়া হয়েছে।
এখন অমরা একটি ছোট উদাহরণ দেখব, যা অসাদৃশ্যতার নীতির এই ‘অ-নিরপেক্ষতা’কে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। (এই উদাহরণটি শুধু পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য দেওয়া হচ্ছে; এটি মূল যুক্তির ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না।)
কুরআনের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন
সমালোচনামূলক ইতিহাসবিদরা’ ইসলামিক ঐতিহাসিক বিবরণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে কুরআন আসলে অনেক পরে, অর্থাৎ অষ্টম বা নবম শতকে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই ধারণা ভেঙে যায় যখন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হিজাজি লিপিতে লেখা একটি কুরআনের পাণ্ডুলিপির কার্বন-ডেটিং করা হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলাফল দেখায়, এই পাণ্ডুলিপিটি খ্রিস্টাব্দ ৫৬৮ থেকে ৬৪৫ সালের মধ্যে লেখা হয়েছে। ইসলামিক প্রচলিত বর্ণনা অনুযায়ী, কুরআন নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতি জীবনে (৬১০–৬৩২ খ্রিস্টাব্দে) অবতীর্ণ হয়েছিল এবং প্রায় ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা উসমান (রাঃ) কুরআনের লিখিত সংকলন প্রচার করেন। অর্থাৎ ৬১০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি কুরআন অবতরণ ও সংকলনের মূল সময়কাল।
কিন্তু অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল সাঈদ রেনল্ডস বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপির তারিখ নির্ধারণের পর লেখেন — “এই প্রাচীন তারিখগুলো দেখে মনে হচ্ছে কুরআন উসমানের আগেই, এমনকি তারও অনেক আগে লিখিত হতে পারে। তাই কুরআনের উৎস নিয়ে প্রচলিত গল্প নতুন করে ভাবার সময় এসেছে, এমনকি মুহাম্মদের জীবনের প্রচলিত তারিখগুলোও।” এখানে দেখা যায় যে এই সব ‘ওরিয়েন্টালিস্টদের’ চিন্তার পেছনে কাজ করছে “অসাদৃশ্যতার নীতি”। প্রথমে তারা প্রচলিত ইসলামিক ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল কুরআন অনেক পরে তৈরি হয়েছে। পরে যখন বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করল যে কুরআন আসলে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর যুগের কাছাকাছি সময়েই ছিল, তখন তারা আবার বলল— না, তাহলে হয়তো কুরআন তারও আগে লেখা!
রেনল্ডস আরও বলেন — “যা অনেকেই ইসলামিক ইতিহাসের প্রমাণ হিসেবে দেখছেন (যেমন নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেছিল যে এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য ঐক্য ও উপলব্ধির মুহূর্ত তৈরি করেছে), সেটি আসলে ভালোভাবে দেখলে প্রমাণ করে যে ইসলামিক ইতিহাস আমাদের ধারণার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন।” এই মন্তব্য শুনতে নিরপেক্ষ মনে হলেও (বিদ্রূপার্থে বলা হচ্ছে), বাস্তবে এটি একেবারে প্রাকৃতিকতাবাদী চিন্তা চাপিয়ে দেয়, যেখানে সব ধর্মীয় দাবি আগেই মিথ্যা ধরা হয়। আসলে কেউ চাইলেই প্রচলিত ইসলামিক ইতিহাসে বিশ্বাস রাখতে পারেন, অথচ নাস্তিক, খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী হয়েও থাকতে পারেন, কারণ এখানে কুরআনের প্রচলিত সময়কাল স্বীকার করা মানে ধর্মীয় মতবাদ মানা নয়। কিন্তু না — তারা তা মেনে নিতে পারে না; তাই বলে বসে, কুরআন হয় অনেক পরে নয়তো নবীর জীবনের আগেই লেখা।
একজন জনপ্রিয় ইতিহাসবিদ, টম হল্যান্ড, আরও একধাপ এগিয়ে দাবি করেন যে বার্মিংহাম পাণ্ডুলিপির তারিখ প্রমাণ করে কুরআন নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্মের আগেই লেখা হয়েছিল! এসব অদ্ভুত দাবি তৈরির পেছনেও কাজ করছে সেই একই অসাদৃশ্যতার নীতি — অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস সবসময়ই ভুল, আর আসল ইতিহাস পরে তৈরি।
জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (মৃত্যু ১৯২০) বলেন, ধর্মপ্রবর্তকরা নিজেরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষা তৈরি করেননি; বরং পরবর্তী প্রজন্ম তাদের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে এসব গড়ে তুলেছে। এর বিপরীতে ইসলামিক প্রচলিত ধারণা বলে, পরবর্তী প্রজন্ম শুধু নবীর ﷺ আসল শিক্ষাকে সংরক্ষণ করেছে এবং তাঁর নামে মিথ্যা কথা ছড়ানো থেকে বিরত রেখেছে। তাহলে প্রশ্ন আসে — জ্ঞানের কোন ভিত্তিতে ম্যাক্স ওয়েবারের ধারণাকে ইসলামিক প্রচলিত বর্ণনার চেয়ে বেশি সত্য ধরা হবে? এর ভিত্তি কী? পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী ও ইউরোকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি? এমন ভিত্তিকে সার্বজনীন হিসেবে মানতে হলে সেটির যৌক্তিক প্রমাণ দিতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বাইরের জগতে, নইলে এটি কেবল এক বৃত্তাকার যুক্তি।
দার্শনিক ডব্লিউ. টি. স্টেইস যেমন সুন্দরভাবে বলেছেন, “আমরা চাই বা না চাই, দর্শন থেকে পালাতে পারি না, কারণ জ্ঞানের যে পথেই যাই না কেন, দর্শন আমাদের সামনে তার প্রশ্ন নিয়ে অপেক্ষা করে।”
মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে
উপরের আলোচনাগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পশ্চিমাদের মধ্যে সত্যিকারের ‘প্রাচ্য’ বা ওরিয়েন্টকে বোঝার ক্ষমতা খুবই সীমিত। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, আলোকায়ন যুগের উত্তরাধিকারী হিসেবে, ধর্ম অধ্যয়নের এই তথাকথিত পণ্ডিতরা — যেমন গ্যুনোঁ বলেছেন — “তাদের নিজের চিন্তা ও সংস্কৃতির ধারণাগুলোই তারা অন্য ধর্মের বিশ্লেষণে নিয়ে আসে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সব তত্ত্বকে ইউরোপীয় চিন্তার কাঠামোর মধ্যে জোর করে ফেলতে চায়। মূলত, পদ্ধতিগত প্রশ্ন ছেড়ে দিলে, ওরিয়েন্টালিস্টদের সবচেয়ে বড় ভুল হলো সবকিছু নিজেদের পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। অথচ কোনো মতবাদ সঠিকভাবে বোঝার প্রথম শর্ত হলো — যাঁরা সেই মতবাদ গড়েছেন, তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিকে বোঝার চেষ্টা করা।”
এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ও ইউরোকেন্দ্রিক মানসিকতা, যেটি তারা স্বীকার করুক বা না করুক, যেমন অধ্যাপক জোসেফ লম্বার্ড বলেছেন — “যখন একজন গবেষক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়েন, তখন তিনিও কিছু পূর্বধারণা নিয়ে আসেন, যেমন একজন ধর্মতাত্ত্বিক করেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ধর্মনিরপেক্ষ গবেষক তাঁর বিশ্বাস নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেন না, যদিও তিনিও সেগুলোর দ্বারা সীমাবদ্ধ।” এই মনোভাব তাদের এমন ভ্রান্ত ধারণায় ফেলেছে যে তারা মনে করে, মুসলমানদের তুলনায় তারাই ইসলামিক ঐতিহ্যকে ভালো বোঝে। মুইর, স্প্রেঙ্গার, গিবন, গোল্ডজিহার, শাখট প্রমুখ ওরিয়েন্টালিস্টরা এমন মনোভাবেই কাজ করেছেন যেন বলছেন — “মুসলমানরা নিজের ধর্ম বা নবীকে ঠিকমতো বুঝতে পারেনি, যতক্ষণ না আমরা এসে ব্যাখ্যা করলাম।”
এই অ-নিরপেক্ষ পদ্ধতির আরেকটি বড় অপব্যবহার হলো ইসলামিক ঐতিহ্যকে এমনভাবে দেখা যেন এটি বহু আগে বিলুপ্ত কোনো সভ্যতা। অতীতের কোনো বিলুপ্ত সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় যেভাবে অনুমান নির্ভর পুনর্গঠন করতে হয়, ইসলামিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তারা তেমনি আচরণ করে। কিন্তু ভুলে যায়, ইসলামিক ঐতিহ্য আজও টিকে আছে, জীবন্ত ও সক্রিয়, এবং এর এখনো স্বীকৃত প্রতিনিধি আছেন। তাঁদের পরামর্শ ও ব্যাখ্যা যে কোনো একাডেমিক জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।
তবে যদি কেউ মনে করে যে এই প্রতিনিধিরা নিজের বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থই বোঝেন না, তাহলে তাদের কথা কোনো গুরুত্বই পায় না। গ্যুনোঁ একে বলেছেন ‘বৌদ্ধিক ক্ষীণদৃষ্টি’ (intellectual myopia) — যা শারীরিক দূরদৃষ্টিহীনতার চেয়েও মারাত্মক। তাঁর ভাষায় —
“যেমন শারীরিক ক্ষীণদৃষ্টি ধীরে ধীরে তৈরি হয়, তেমনি মানসিক ক্ষীণদৃষ্টিও এক ধরনের অভ্যাসের ফল। এই কারণেই অধিকাংশ ওরিয়েন্টালিস্টরা যারা তাদের পদ্ধতি মেনে নিতে চায় না বা তাদের সিদ্ধান্ত মানে না, তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখায়। এটি আসলে অতিরিক্ত বিশেষায়নের অপব্যবহারের ফল, এবং তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্কতার একটি ভ্রান্ত প্রকাশ, যা সহজেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়।” সার্বিকভাবে বলতে গেলে, ওরিয়েন্টালিস্টরা যতটা ইতিবাচক গবেষণার ফল দিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করেছেন প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার। তারা নিজেদের অযৌক্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে অন্য সব চিন্তার পথকে ‘অবৈজ্ঞানিক’ বলে বন্ধ করে দিয়েছেন।
উপসংহার
ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক পদ্ধতি (HCM) ধর্মীয় ও সাহিত্যিক পাঠ বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর ভিত্তি প্রায়ই পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা ইসলামী ঐতিহ্যের মূল আত্মাকে অবহেলা করে। প্রাচ্যবিদদের এই একপেশে মানসিকতা ইসলামী জ্ঞানের প্রকৃত গভীরতাকে বিকৃত করেছে। গ্যুনোঁ, আভিসেনা ও আধুনিক চিন্তাবিদরা দেখিয়েছেন যে সত্য বোঝার জন্য প্রয়োজন উচ্চতর দর্শনভিত্তিক পদ্ধতি—যেখানে প্রতিটি বিজ্ঞান সত্যের অধীন। মুসলমানদের উচিত জ্ঞানচর্চায় এই মৌলিক নীতিগুলিতে ফিরে আসা, যাতে ঐতিহ্য, যুক্তি ও আত্মিক জ্ঞান সমন্বিত হয়। ইতিহাস বিশ্লেষণের লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু তথ্য নয়, সত্যের সন্ধান। তাই প্রয়োজন একটি এমন পদ্ধতির, যা বস্তুবাদী সীমা অতিক্রম করে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকে একত্র করে। সত্য ও জ্ঞানের এই সংলগ্ন দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামী ঐতিহ্যের প্রকৃত শক্তি এবং ভবিষ্যতের সঠিক জ্ঞানচর্চার দিকনির্দেশ।