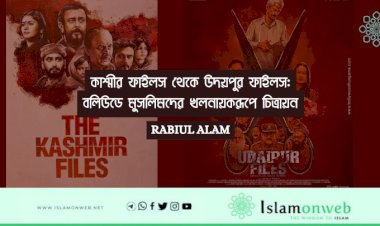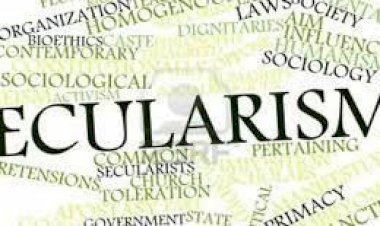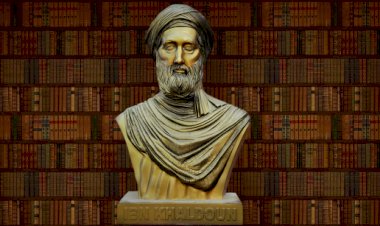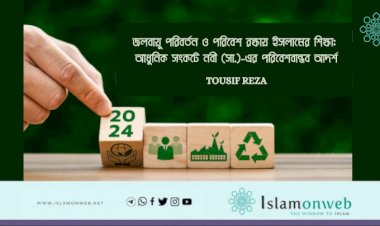পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা ও তাদের শিক্ষাব্যবস্থা: বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের একটি পর্যালোচনা
ভূমিকা
পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার একটি সমৃদ্ধ ইসলামী ইতিহাস রয়েছে। একসময় সুফি, সুলতান এবং নবাবদের হাত ধরে এখানে সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল । কিন্তু এই ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে এই জেলাগুলির মুসলিম জনসংখ্যা (মুর্শিদাবাদে ৬৬.২৭% এবং বীরভূমে ৩৭.০৬%) আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ।
ইংরেজ শাসনের সময় (ঔপনিবেশিক আমলে), বিশেষ করে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর এবং মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হলে, মুসলিমদের পতন শুরু হয় ।
এই পরিস্থিতিতে, অনেক দরিদ্র মুসলিম পরিবারের জন্য শিক্ষার একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে সম্প্রদায়-চালিত "খারিজি" বা "কওমি" মাদ্রাসাগুলি । এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি সাহায্য বা পাঠ্যক্রম ছাড়াই, সাধারণ মানুষের অনুদানে চলে । কিন্তু প্রায়শই এই মাদ্রাসাগুলি অর্থের অভাব, যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং পুরানো শিক্ষণ পদ্ধতির মতো সমস্যার সাথে লড়াই করে, যা শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিতে বাধা দেয় ।
বেশিরভাগ গবেষণাই সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলির উপর হয়েছে, কিন্তু এই গ্রামীণ, সম্প্রদায়-ভিত্তিক খারিজি প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি । এই গবেষণার লক্ষ্য সেই শূন্যস্থান পূরণ করা। এখানে এই মাদ্রাসাগুলির পাঠ্যক্রম, তাদের চ্যালেঞ্জ এবং সমাজে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কিছু সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, কেস স্টাডি: প্রশ্নাবলী ও সাক্ষাৎকার, এবং অন্যান্য উৎস.
খারিজি মাদ্রাসা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান অবস্থা
বাংলায় মুসলিমদের আগমন ঘটেছিল মূলত সুফি এবং আরব বণিকদের মাধ্যমে । খলজি, ইলিয়াস শাহী, হুসেন শাহী এবং পরবর্তীকালে নবাবরা মুর্শিদাবাদের কাত্রা মসজিদ ও মতিঝিল মাদ্রাসার মতো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে, বিশেষ করে যখন মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় প্রশাসনিক কেন্দ্র সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন মুসলিমদের শিক্ষা ও অর্থনীতিতে ধস নামে ।
আজও এই জেলাগুলি অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে, এবং বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। মুসলিমদের সাক্ষরতার হার (মুর্শিদাবাদে ৬৩.২২%) হিন্দুদের (একই জেলায় ৭২.৯৭%) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম । এই ব্যাপক দারিদ্র্য এবং শিক্ষাগত অনগ্রসরতার কারণেই দরিদ্র পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও খাবারের জন্য খারিজি মাদ্রাসাগুলিতে পাঠায়।
"খারিজি" মাদ্রাসা মানে হলো এগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণের "বাইরে" (খারিজি) এবং "কওমি" অর্থাৎ "সম্প্রদায়ের" দ্বারা পরিচালিত । এগুলি সম্পূর্ণভাবে মানুষের অনুদান, যাকাত এবং ওয়াকফের উপর নির্ভর করে চলে । ঐতিহাসিকভাবে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিরুদ্ধে ইসলামী ঐতিহ্য ও শিক্ষাকে রক্ষা করার জন্যই দেওবন্দ আন্দোলনের (১৮৬৬) সূচনা হয়েছিল, এবং সেই অনুপ্রেরণাতেই বাংলা জুড়ে এই খারিজি মাদ্রাসাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় ।
অভিভাবকরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে নয়, বরং বেশ কিছু আদর্শিক ও ব্যবহারিক কারণেও খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে বেছে নেন। প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে; অভিভাবকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এখানে শিক্ষার্থীরা কঠোর শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং একজন "ভালো মুসলিম" হিসেবে গড়ে ওঠার শিক্ষা পায়। দ্বিতীয়ত, মাদ্রাসাগুলি সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, যা সেক্যুলারাইজেশনের মুখে ইসলামী সংস্কৃতি, পরিচয় এবং ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাকে সুরক্ষিত রাখে। তৃতীয়ত, এই মাদ্রাসাগুলির প্রধান সুবিধা হলো এর সহজলভ্যতা: এটি দরিদ্রতম পরিবারগুলির জন্যও বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুযোগ সহ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব করে তোলে, যা পারিবারিক ব্যয়ভার লাঘব করে। এই মাদ্রাসাগুলি মূলত "দরস-ই-নিজামী" নামক একটি ঐতিহ্যবাহী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, যেখানে প্রাথমিক স্তর (ইবতিদাইয়্যাহ) থেকে শুরু করে ফিকহ (ইসলামী আইন) বা হাদিসের মতো বিষয়ে উন্নত বিশেষীকরণের (তাখাসসুস) ব্যবস্থা রয়েছে।
সমস্যা এবং সমাধান
খারিজি মাদ্রাসাগুলি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি বেশ কিছু গুরুতর কাঠামোগত দুর্বলতায় জর্জরিত। প্রথমত, এই মাদ্রাসাগুলির শংসাপত্রগুলি সরকারি স্বীকৃতিবিহীন হওয়ায়, শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা বা মূলধারার কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না, ফলে তাদের ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র ইমামতি বা মাদ্রাসার শিক্ষকতার মধ্যে শিক্ষাগত অচলাবস্থা-য় আবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত, তাদের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রধানত মুখস্থ-নির্ভর এবং সেকেলে, যেখানে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বা আধুনিক শিক্ষণ কৌশলের অভাব রয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশে বাধা দেয় এবং তাদের বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অপ্রস্তুত রাখে। তৃতীয়ত, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুতে পাঠদান করা হয়, যা শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সংস্কৃতি ও পশ্চিমবঙ্গের চাকরির বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন করে। পরিশেষে, ক্রমাগত আর্থ-সামাজিক প্রান্তিকীকরণের শিকার এই মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের 'ভুক্তভোগী' মনে করে, যা তাদের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বা 'একঘরে' হওয়ার সংস্কৃতি তৈরি করেছে এবং মেয়েদের মধ্যে উচ্চহারে স্কুল ছাড়ার প্রবণতা বাড়িয়েছে। এই সমস্ত সমস্যাগুলি সম্মিলিতভাবে মাদ্রাসা ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে দুর্বল করে দিয়েছে।
মাদ্রাসার বর্তমান গভীর সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একটি ব্যাপক সংস্কার কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য। এই কৌশলটি চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: প্রথমত, মাদ্রাসাকে শুধুমাত্র ব্যর্থ ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল হিসেবে না দেখে, বরং এটিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুনভাবে দেখা প্রয়োজন যা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে এক অনন্য "সাংস্কৃতিক পুঁজি" প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, পুরানো "ব্যাংকিং মডেল"-এর পরিবর্তে একটি ছাত্র-কেন্দ্রিক, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করা আবশ্যক, যা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করবে। এর জন্য ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশ এবং জটিল ধারণা বোঝানোর জন্য ফাইনম্যান কৌশল ও LSRW (শোনা, বলা, পড়া, লেখা) পদ্ধতির মতো ব্যবহারিক কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। তৃতীয়ত, শিক্ষার মূল স্রোত থেকে শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্নতা দূর করতে পাঠ্যক্রমের একীকরণ প্রয়োজন। এখানে আধুনিক বিষয়গুলির (ইংরেজি, গণিত) কার্যকর শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাঠ পরিকল্পনা গোছানোর জন্য ADDIE মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। চতুর্থত, মাদ্রাসাগুলিকে কঠোর "ঐতিহ্যবাদ" এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ ত্যাগ করে "জ্ঞানতাত্ত্বিক বহুত্ব" (একাধিক চিন্তাধারা গ্রহণ) ফিরিয়ে আনতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এই সমন্বিত সংস্কারগুলি মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে সময়ের উপযোগী করে তুলতে পারে।
উপসংহার
বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের খারিজি মাদ্রাসাগুলি সেকেলে বা অচল নয়, বরং এগুলি হাজার হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশুর জন্য শিক্ষা, নৈতিক নির্দেশনা এবং সামাজিক সুরক্ষার অপরিহার্য কেন্দ্র । তবে, এই গবেষণা দেখায় যে অর্থের অভাব, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং পুরানো শিক্ষণ পদ্ধতির মতো গুরুতর সমস্যাগুলি তাদের অবদানকে খর্ব করছে । এই সমস্যাগুলি স্নাতকদের ভবিষ্যতকে সীমিত করে দিচ্ছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যত নির্ভর করছে সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপর। যদি তারা আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিকে ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের সাথে একীভূত করতে পারে, মাতৃভাষার (বাংলা) ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার করতে পারে, তবেই তারা বর্তমান বাধাগুলি অতিক্রম করতে পারবে । এর মাধ্যমে তারা একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সফল হতে সাহায্য করতে পারবে ।
তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি
Begum, Shabnam. Bengal’s Contribution to Islamic Studies during the 18th Century. Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, 1994.
Eaton, Richard M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. University of California Press, 1993.
Hasan, Md. Kamrul, and Dr. Md. Shamim Firdous. “Socio-Economic Condition of the People of Birbhum District during Colonial Bengal.” Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects, March 2019.
Hoque, Md. Zaharul. “Muslim Education in Murshidabad District of West Bengal: Problems and Solutions.” International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS), May 2016.