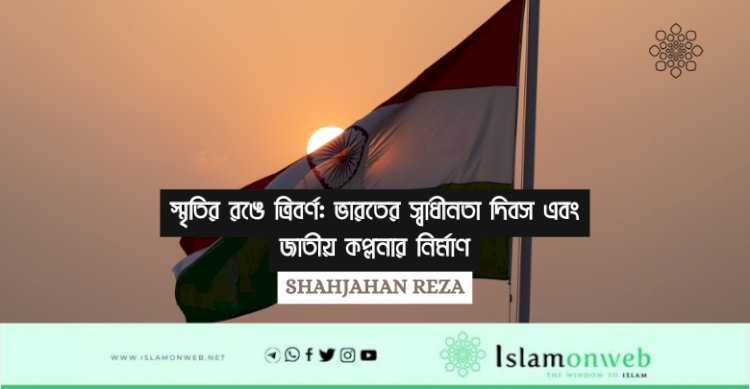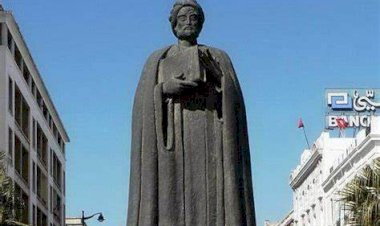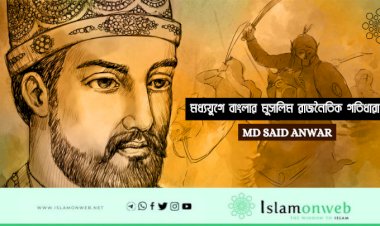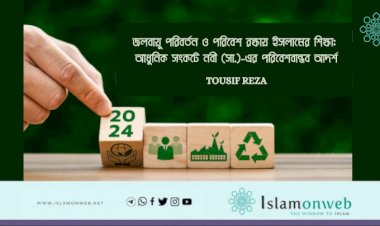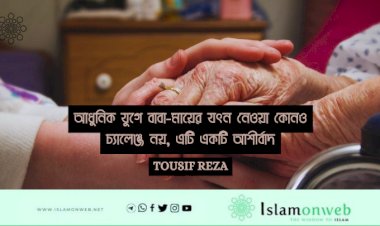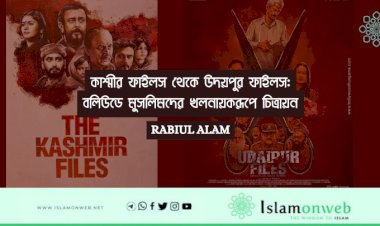স্মৃতির রঙে ত্রিবর্ণ: ভারতের স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় কল্পনার নির্মাণ
ভূমিকা
প্রতি বছর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের আকাশজুড়ে যখন ত্রিবর্ণ পতাকা দোলায়িত হয়, সঙ্গে যুক্ত হয় ভাষণ, কুচকাওয়াজ ও দেশাত্মবোধক আনুষ্ঠানিকতার সুপরিকল্পিত মঞ্চায়ন, তখন স্বাধীনতা দিবস যেন কেবল রাষ্ট্রীয় উদযাপনের আড়ম্বর নয়, বরং জাতির সমষ্টিগত স্মৃতিচর্চার এক অনন্য পরিসর রচনা করে। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ইতিহাস কেবল স্থির নথিপত্রে সংরক্ষিত নয়; বরং তা ক্রমাগত পুনর্গঠন, পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে জাতিগত পরিচয় ও আত্মচেতনার অন্তর্গত রাজনীতিকে উন্মোচিত করে। মোরিস হালবওয়াখ্, পিয়ের নোরা এবং বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের আলোচনায় যে "স্মৃতিরাজনীতি" (Politics of Memory) ধারণাটি উদ্ভাসিত হয়, তা আমাদের সতর্ক করে যে জাতীয় অতীতের প্রতিটি আখ্যান আসলে নির্বাচিত স্মরণ ও কৌশলগত বিস্মরণের দ্বন্দ্বে গঠিত, যা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত শক্তির দ্বারা নির্ধারিত।
ভারতের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা দিবসের আখ্যান গঠিত হয়েছে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক উপকরণ ও প্রতীকের মাধ্যমে, তবে এর মধ্যে তিনটি মাধ্যম বিশেষভাবে কার্যকর, পাঠ্যপুস্তক, চলচ্চিত্র এবং রাজনৈতিক ভাষণ। এই ত্রিমুখী মাধ্যম কেবল জাতীয় স্মৃতির স্থাপত্য নির্মাণ করে না, বরং দেশপ্রেম, ঐক্য ও নাগরিকত্বের আদর্শকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত করার প্রধান যন্ত্রে পরিণত হয়। একই সঙ্গে এগুলো প্রায়ই বিকল্প ইতিহাস ও প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে আড়াল বা অবমূল্যায়ন করে। এই প্রবন্ধে ১৯৪৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত উল্লিখিত তিনটি মাধ্যম কীভাবে স্বাধীনতা দিবসের সমষ্টিগত স্মৃতি নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে, এবং সেই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় জাতির ‘কল্পিত সম্প্রদায়’ (Imagined Community) ধারণাকে কীভাবে পুনরুৎপাদন করেছে, তার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।
পাঠ্যপুস্তক: জাতীয় ইতিহাসের স্থপতি
বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠকক্ষ স্বাধীনতা দিবসের অর্থ ও তাৎপর্যের প্রাথমিক ও স্থায়ী ভিত্তি নির্মাণ করে। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক দশকে এনসিইআরটি (NCERT) এবং রাজ্য শিক্ষাবোর্ডের (State Educational Board) পাঠ্যপুস্তকসমূহ আনুষ্ঠানিক জাতীয় আখ্যানের প্রধান বাহনে পরিণত হয়েছে। এসব পাঠ্যক্রমে ১৫ আগস্টকে উপস্থাপন করা হয় এক মহিমান্বিত ঐতিহাসিক পরিণতি হিসেবে, যেন সমগ্র ভারতবর্ষ অভিন্ন চেতনায় এবং নৈতিকভাবে অব্যর্থ এক স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভারতের মতো একটি দেশে, যার স্বাধীনতার ইতিহাস রক্ত, ত্যাগ, আর অদম্য সংগ্রামের এক মহাকাব্য — আজ সেই ইতিহাসকে বিকৃত করা, মুছে ফেলা হচ্ছে সংগঠিতভাবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত নায়কদের, তাঁদের আদর্শ আর আত্মদানকে পিছনে ঠেলে, সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট কিছু গোষ্ঠী ইতিহাসের পটচিত্রকে বদলে দিচ্ছে। প্রকৃত সত্যকে চাপা দিয়ে, তুচ্ছ ও মনগড়া গল্প, মনস্তুষ্টিকর কিংবদন্তি, আর রাজনৈতিক সুবিধার উপযোগী চরিত্রদের সামনে আনা হচ্ছে। আজাদির লড়াই ছিল একটা সার্বজনীন আন্দোলন — হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, দলিত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের রক্তে রাঙানো পথ। অথচ সেই ইতিহাসের ঐক্যের জায়গায় বসানো হচ্ছে বিভাজন, সেই গৌরবের বদলে শিখানো হচ্ছে গৌণতা। এটা শুধু ইতিহাসের প্রতি অন্যায় নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আত্মপরিচয় ও বিবেকের উপরও এক নিষ্ঠুর আঘাত।এভাবে পাঠ্যপুস্তক কেবল অতীতকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করে না, বরং জাতীয়তাবাদী স্মৃতিচর্চার নির্দিষ্ট এক সংস্করণকেও প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা প্রদান করে।
তবে এই উপস্থাপন কোনোদিনই স্থির বা অপরিবর্তিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, এনসিইআরটির (NCERT) ১৯৭৫ সালের অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত, যেখানে স্বাধীনতার প্রধান স্থপতি হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুকে কেন্দ্রীয় আসনে স্থাপন করা হয়েছে। অপরদিকে, ২০০০ ও ২০১০-এর দশকের সংশোধিত সংস্করণে তুলনামূলকভাবে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক আন্দোলনের ভূমিকা, যদিও তা এখনো একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ। তদুপরি, গিরিজন বিদ্রোহ, কৃষক আন্দোলন এবং নারী বিপ্লবীদের অবদান প্রায়শই পাঠ্যের প্রান্তবর্তী স্থানে কিংবা ফুটনোটসদৃশ ক্ষুদ্র উল্লেখে সীমিত থাকে, যা ইতিহাসচর্চার অভ্যন্তরে বিদ্যমান নির্বাচিত স্মরণ ও কৌশলগত বিস্মরণের প্রবণতাকে সুস্পষ্ট করে তোলে।
এখানে পাঠ্যক্রম-নকশার অন্তর্নিহিত রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে আর কোনটি বাদ পড়বে—তা নিছক শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রশ্ন নয়, বরং একেবারেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Nation and Its Fragments-এ দেখিয়েছেন যে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস প্রায়শই একটি “শিক্ষামূলক” হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়, যার উদ্দেশ্য অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও দ্বন্দ্বকে মসৃণ করে একটি অভিন্ন ও সংহত জাতীয় অতীতের চিত্র নির্মাণ করা। সুতরাং পাঠ্যপুস্তক কেবল তথ্যপ্রদানকারী মাধ্যম নয়; বরং তা জাতীয়তাবাদী স্মৃতিচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং নাগরিকদের মনে একটি নির্দিষ্ট জাতীয় ধারণাকে স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ ও অপরিহার্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে।
পর্দার স্মৃতি: বলিউডের আবেগ
আজকের ভারতে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা যেন দিনকে দিন বিকৃত হয়ে পড়ছে। যেটা একসময় ছিল একত্রে বাঁচার স্বপ্ন, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা, আজ সেটা পরিণত হয়েছে এক বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের হাতিয়ারে। দেশপ্রেমকে এখন এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেন মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা আর বিদ্বেষই তার অপরিহার্য অঙ্গ। এক শ্রেণির প্রচারণা মুসলমানদের আজ "অন্য" করে তুলেছে — যেন তারা এই মাটিরই নয়, যেন তাদের প্রতি সন্দেহ করাই প্রকৃত দেশপ্রেম। অথচ এই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে লক্ষ মুসলমান রক্ত দিয়েছে, কণ্ঠ দিয়েছে ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’-এর স্লোগানে। আজ সেই ইতিহাস ধামাচাপা দিয়ে, জাতীয়তাবাদের নামে একপাক্ষিক, বিদ্বেষমূলক আবেগ জাগানো হচ্ছে, যা আমাদের সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে গলাটিপে হত্যা করছে। এই বিভাজনমূলক দেশপ্রেম দেশকে বড় নয়, বরং ছোট করে। সত্যিকারের দেশপ্রেম কখনোই ঘৃণার উপর দাঁড়ায় না — তা দাঁড়ায় ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ন্যায়ের উপর।
যেখানে পাঠ্যপুস্তক স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি নির্মাণ করে, সেখানে চলচ্চিত্র গড়ে তোলে তার আবেগীয় ও নান্দনিক স্মৃতি। মনোজ কুমারের শহীদ (১৯৬৫)-এর আত্মোৎসর্গমূলক আখ্যান থেকে শুরু করে লগান (২০০১)-এর ঔপনিবেশিক ক্রিকেটকেন্দ্রিক প্রতীকী সংগ্রাম, বলিউড (Bollywood) বারবার এমন বর্ণনা রচনা করেছে, যা দর্শকের মনে সমষ্টিগত গর্ব, ঐক্য ও ত্যাগের আবেগকে সক্রিয় করে তোলে। এই চলচ্চিত্রগুলো পিয়ের নোরা-র পরিভাষায় প্রকৃত lieux de mémoire, যেখানে ইতিহাস ও আবেগ একত্রিত হয়ে জাতীয় পরিচয়ের এক যৌথ অর্থ ও অভিজ্ঞতা নির্মাণ করে।
দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্রের ধারাটি সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬২ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধপরবর্তী সময়ে উপকার এবং বর্ডার-এর মতো সামরিকতাবাদী চলচ্চিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, যেখানে দেশপ্রেম মূলত শারীরিক ত্যাগ ও সীমান্তরক্ষার মাধ্যমে প্রতীকীকৃত। উদারীকরণের যুগে, যেমন চক দে! ইন্ডিয়া (২০০৭)-এ, দেশাত্মবোধ রূপান্তরিত হয়েছে খেলাধুলা, নরম ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের মাধ্যমে। ২০১০-এর দশক থেকে সাম্প্রতিক সময়ে, উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক (২০১৯) এবং RRR (২০২২)-এর মতো চলচ্চিত্রে দেখা যায় অ্যাকশন-নির্ভর ন্যারেটিভের সঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণ, যা সমকালীন রাজনৈতিক বয়ান ও রাষ্ট্রীয় নীতি-প্রয়োগের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এই ধারাবাহিক পরিবর্তন প্রদর্শন করে যে দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্মৃতিচর্চার শক্তিশালী বাহন। ফলে, চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি স্বাধীনতা দিবসের আবেগীয় শব্দভান্ডার গঠন করে এবং জটিল ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সংক্ষেপে বীরত্বপূর্ণ ও প্রতীকী আখ্যান হিসেবে পুনর্লিখন করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়।
শব্দের রাজনীতি: স্বাধীনতার ভাষণ ও কল্পিত সম্প্রদায়
প্রতি বছরের লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবস ভাষণ জাতীয় স্মৃতিনির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৪৭ সালে জওহরলাল নেহেরুর “Tryst with Destiny” ভাষণ একতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতির উন্নয়নের আশাবাদে পরিপূর্ণ ছিল। পরবর্তী দশকগুলোতে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণসমূহ প্রায়শই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করেছে—যেমন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর খাদ্যসঙ্কটকালে “জয় জওয়ান জয় কিসান” আহ্বান, জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ়তার বয়ান, অথবা অটল বিহারী বাজপেয়ীর শান্তি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রতিশ্রুতি। এভাবে ভাষণগুলি কেবল রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উপস্থাপন করে না, বরং নাগরিকদের মধ্যে একটি নির্বাচিত জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে পুনর্নির্মাণের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
সাম্প্রতিক সময়ে নরেন্দ্র মোদীর স্বাধীনতা দিবস ভাষণে নিরাপত্তা, আত্মনির্ভর ভারত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে স্বাধীনতা দিবস কেবল অতীতের স্মৃতিচর্চা নয়; বরং এটি একটি রাজনৈতিক এবং দার্শনিক ক্ষেত্র, যেখানে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব জাতির ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণের মাধ্যমে জনগণের মানসিকতা ও নৈতিক চেতনা রূপায়ণ করে। এ ধরনের ভাষণ শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করে না, বরং একটি কল্পিত জাতীয় সম্প্রদায় (Imagined Community) গঠনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের নীতিগত ও সাংস্কৃতিক দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করে। ফলে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণসমূহ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সমন্বিত সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে, যা নাগরিকদের মধ্যে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ, ঐক্য এবং আত্মপরিচয়ের সংজ্ঞা জাগ্রত করে।
উপসংহার
ভারতে স্বাধীনতা দিবস কেবল একটি উৎসব নয়, বরং একটি জাতীয় স্মৃতির মঞ্চ, যেখানে অতীতকে কেবল স্মরণ করা হয় না, বরং তা সমসাময়িক প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুনভাবে রচিত হয়। পাঠ্যপুস্তক, চলচ্চিত্র এবং রাজনৈতিক ভাষণের সমন্বয়ে ১৫ আগস্টের অর্থ ক্রমাগত পুনর্নির্মাণ করা হয়, যা নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, ঐক্য এবং নৈতিক চেতনার অনুভূতি সঞ্চার করে। এই প্রক্রিয়ায় সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের “কল্পিত সম্প্রদায়” (Imagined Community) তত্ত্বের এই বাস্তবায়নকে আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারি—জাতি তার নিজস্ব গল্প, স্মৃতি এবং চেতনা রচনা করার মাধ্যমে অস্তিত্বকে সংহত ও প্রাসঙ্গিক রাখে। স্বাধীনতা দিবস তাই অতীতের স্মৃতিচর্চা, বর্তমানের রাজনৈতিক চেতনা এবং ভবিষ্যতের জাতীয় দর্শনের এক সমন্বিত উদাহরণ হিসেবে কার্যকর হয়।
তবে, এই কল্পিত জাতীয়তা যদি একতরফা বা নির্বাচনী হয়, তা প্রায়শই বর্জনমূলক দেশপ্রেমের জন্ম দেয়, যা বিশেষ ইতিহাস, সম্প্রদায় বা কণ্ঠকে প্রান্তিক করে রাখে। স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতিচর্চা তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন তা বহুত্ববাদ, জটিলতা এবং সমালোচনামূলক পর্যালোচনাকে স্বাগত জানাবে—যাতে স্বাধীনতার গল্প কেবল অতীতের প্রতীক হিসেবে নয়, বরং বর্তমানের সঙ্গে এক জীবন্ত সংলাপ, বিকল্প আখ্যান ও নাগরিক চেতনার সক্রিয় অংশ হিসেবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ নিশ্চিত করে যে জাতীয় স্মৃতিচর্চা কেবল প্রথাগত ন্যারেটিভের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সংবেদনশীল প্রক্রিয়া, যা নাগরিকদের মধ্যে সমতা, বিচারবুদ্ধি এবং ইতিহাসবোধ জাগ্রত করে।