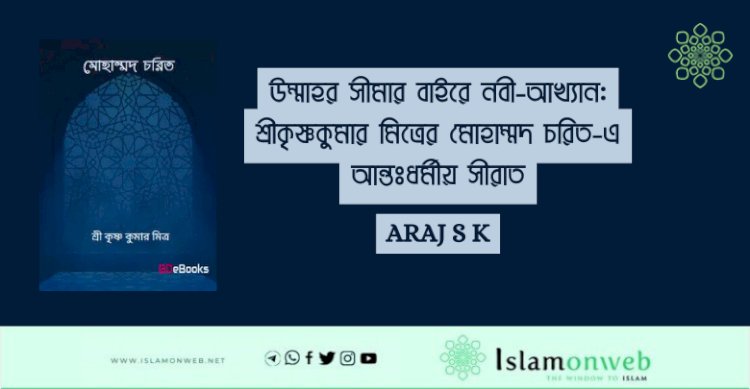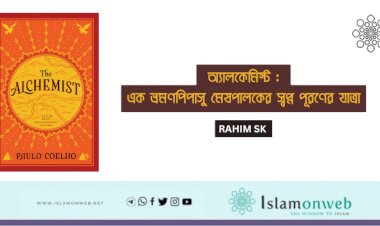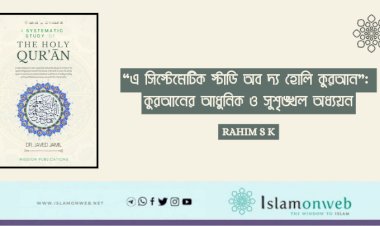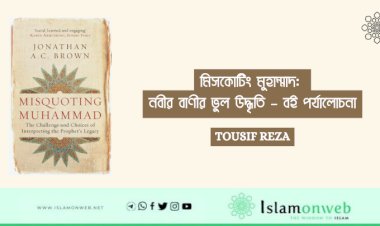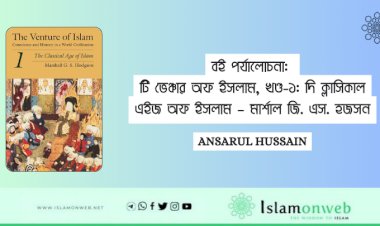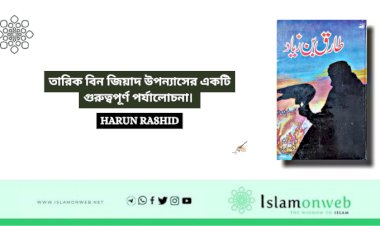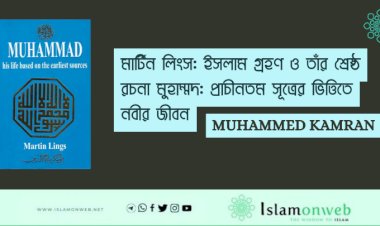উম্মাহর সীমার বাইরে নবী-আখ্যান: শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের মোহাম্মদ চরিত-এ আন্তঃধর্মীয় সীরাত
ভূমিকা
সীরাহ হল নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী। মুসলমানদের জন্য সীরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে তারা নবীর আদর্শ (সুন্নাহ) শেখে, কোরআনের প্রেক্ষাপট বোঝে এবং ইসলামী আইনের উৎস সম্পর্কে ধারণা পায়। প্রথম দিকের সীরাহ গ্রন্থকার ছিলেন ইবনে ইসহাক (মৃ. ৭৬৭) ও ইবনে হিশাম (মৃ. ৮৩৩)। আজও এগুলো গবেষণার মূল উৎস। কিন্তু শুধু মুসলমানরা নয়, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে অনেক অমুসলিম লেখকরাও নবীর জীবনী লিখেছেন। তারা সাধারণত ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এসব লেখায় নবীর চরিত্রের প্রশংসা থাকলেও, ওহি (প্রকাশ), মুজিজা (অলৌকিক ঘটনা) ইত্যাদি বিষয় অনেক সময় অস্বীকার করা হয়েছে বা যুক্তিবাদীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই প্রশ্ন ওঠে—যদি মুসলিম সমাজের বাইরে থেকে কেউ নবীর জীবনী লেখেন, তাহলে সেটি কেমন হয়?
এই প্রবন্ধে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। বিষয় হিসেবে নেওয়া হয়েছে শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাংলা গ্রন্থ “মহম্মদ চরিত”। মিত্র (১৮৫২–১৯৩৬) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ নেতা, সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি সঞ্জীবনী সাপ্তাহিক সম্পাদনা করতেন এবং সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। মহম্মদ চরিত প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে (কিছু সূত্র অনুযায়ী আরও আগে সংস্করণ বের হয়েছিল)।
বইটি দাঁড়িয়ে আছে তিনটি ধারার সংযোগস্থলে:
১) ঊনবিংশ শতকের বাংলার ছাপাখানা ও সংস্কার আন্দোলন,
২) ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী-ঈশ্বরবিশ্বাস,
৩) এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের উপর চলা বিতর্ক।
মূল যুক্তি হলো: মিত্র নবীর জীবনকে একজন নৈতিক সংস্কারকের গল্প হিসেবে দেখিয়েছেন, মুসলমানদের মতো “আল্লাহর প্রেরিত রাসূল”-এর পবিত্র জীবন হিসেবে নয়। তিনি নবীর নৈতিক সাহস, ন্যায়বিচার ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ওহি, মুজিজা ও রাসূলত্বকে ছোট করে দেখিয়েছেন। এতে ব্রাহ্মসমাজের মূল্যবোধ যেমন যুক্তি, একেশ্বরবাদ ও সার্বজনীন নৈতিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। আবার ভিক্টোরীয় যুগের ইসলামের ব্যাখ্যার সঙ্গে এটার মিল পাওয়া যায়।
এই প্রবন্ধের লক্ষ্য তিনটি: বাংলা ভাষায় লেখা একটি বিরল অমুসলিম সীরাহ বিশ্লেষণ, ভিন্ন ধর্মের মানুষের দৃষ্টিতে “পবিত্র জীবনী লেখার” নৈতিকতা বোঝা, এবং ঔপনিবেশিক বাংলায় আন্তঃধর্মীয় আলোচনা বোঝা।
২. পটভূমি: সীরাহ, ব্রাহ্মসমাজ ও ঔপনিবেশিক বাংলা
২.১ সীরাহ
সীরাহ হল নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন কাহিনি। মুসলমানরা তাঁর চরিত্র, তাঁর কাজ (সুন্নাহ) এবং কোরআনের প্রেক্ষাপট জানার জন্য এটি পড়েন। এখানে বোঝানো হয়—কীভাবে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ওহি পেয়েছিলেন, কীভাবে মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর সাহাবীদের প্রতি তাঁর দয়া-মমতা কেমন ছিল। প্রথম দিকের সীরাহ রচয়িতা ছিলেন ইবনে ইসহাক, যার কাজ পরে ইবনে হিশাম সম্পাদনা করেছিলেন। “মাঘাজি” (অভিযান) গ্রন্থগুলিও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পরবর্তীকালে ওয়েস্টার্ন গবেষক উইলিয়াম গিলিয়মের ইংরেজি অনুবাদ বহুল পড়া হয়েছে।
২.২ ব্রাহ্মসমাজ: যুক্তি, সংস্কার ও সর্বজনীন ধর্ম
ব্রাহ্মসমাজের সূচনা করেন রাজা রামমোহন রায় (১৮২৮)। পরে কেশবচন্দ্র সেন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নেতৃত্ব দেয়। এর মূল শিক্ষা ছিল: এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস (একেশ্বরবাদ), নৈতিক জীবন, সমাজ সংস্কার (যেমন সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা দূর করা)। ব্রাহ্মসমাজের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তি, মানব-চেতনা আর নৈতিক আইনকে ধর্মের আসল ভিত্তি ধরা। তারা কুসংস্কার, অলৌকিকতা বা মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করত। তাই তারা অন্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করত—যাতে সমাজের কল্যাণ ও নৈতিক উন্নতি হয়।
এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে মিত্র নবীর জীবনী লিখেছিলেন। তিনি নবীকে একজন মহান সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দেখিয়েছেন, কিন্তু মুসলমানদের মতো তাঁর রাসূলত্বকে গ্রহণ করেননি। তাঁর চোখে নবী মুহাম্মদ ছিলেন একজন সংস্কারক—যিনি জাহেলিয়াতের অমানবিক সমাজ ভেঙে একটি নতুন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। ইতিহাসবিদ ডেভিড কপফ দেখিয়েছেন যে ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আবার ব্রায়ান হ্যাচার প্রমাণ করেছেন, ব্রাহ্মো ও হিন্দু সংস্কারকরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থেকে ধারণা নিয়ে এক নতুন সর্বজনীন নৈতিক ধর্ম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।
২.৩ ঔপনিবেশিক বাংলা ও বাংলার নবজাগরণ
বাংলার নবজাগরণ মানে হলো উনবিংশ শতকে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে এক বড় পরিবর্তন। এ পরিবর্তন আসলো ব্রিটিশ অফিসার, খ্রিস্টান মিশনারি আর শিক্ষিত হিন্দু বিদ্বানদের মিলনের মাধ্যমে। এর মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ১৮৩০ সালের আগে কিছু শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল এশিয়ার প্রথম উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলোর একটি, যেখানে ইউরোপীয় ধাঁচে পড়ানো হতো। ধীরে ধীরে কলকাতা ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে বদলাতে শুরু করে। তখন বই, সংবাদপত্র আর সাময়িকী প্রকাশ হতে থাকে—কখনও ইংরেজিতে, কখনও বাংলায়। এই নবজাগরণে কিছু ইউরোপীয় ওরিয়েন্টালিস্ট পণ্ডিতও যুক্ত ছিলেন—যেমন উইলিয়াম জোন্স, উইলিয়াম কেরি, এইচ.এইচ. উইলসন আর জেমস প্রিন্সেপ। তারা ভারতীয় ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করতেন। ১৮০০ সালে ব্রিটিশরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গড়ে তোলে। এই কলেজ কাজ করত এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে, যেটি আগে উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই সময়ে ১৮০০ সালের জানুয়ারিতে সেরামপুর মিশন শুরু হয়, যেখানে ব্যাপটিস্ট মিশনারি কেরি, মার্শম্যান আর ওয়ার্ড যুক্ত ছিলেন।
এই পরিবেশে বাঙালি চিন্তাবিদরা নিজেদের ভাষায় নতুন লেখা শুরু করেন। ওরিয়েন্টালিস্ট আর মিশনারিদের সহায়তায় বাংলা সাহিত্য আধুনিক রূপ নিতে থাকে। বাংলার নবজাগরণের চারটি প্রধান ফল দেখা যায়—
১. আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গড়ে ওঠে,
২. ভারতের প্রাচীন ও সোনালি অতীত নতুন করে আবিষ্কৃত হয়,
৩. সামাজিক সংস্কারের ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে,
৪. অগ্রগতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয়।
১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলার বিভাগের প্রধান হন। তাকে প্রায়ই ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ বলা হয়। তিনি প্রথম বাংলা ব্যাকরণ বইও লিখেছিলেন। একই সময়ে ব্রাহ্মসমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তারা কুসংস্কার আর ক্ষতিকর প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মেয়েদের শিক্ষা উৎসাহিত করে। বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষাকে সমর্থন করে। ছাপাখানার কারণে তখন বই, পত্রিকা ছড়িয়ে পড়ছিল। সংস্কার নিয়ে নতুন বিতর্ক হচ্ছিল। ধর্ম নিয়ে নতুনভাবে আলোচনা শুরু হয়। এই সময়েই আবির্ভাব হয় শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্রের। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক, ১৮৮৩ সালে শুরু হওয়া সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক। তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারেরও এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বাংলাপিডিয়া তাঁকে একদিকে সংস্কারক, আবার অন্যদিকে ব্রাহ্মনেতা হিসেবে বর্ণনা করেছে—মানে সমাজে তাঁর দ্বৈত ভূমিকা ছিল।
৩. নিবিড় পাঠ: মিত্র কীভাবে নবীর কাহিনি বলেছেন
এই জীবনীটি মিত্র পাঁচটি দিক থেকে সাজিয়েছেন। এগুলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝায় এবং একই সঙ্গে ইসলামী সীরাহর সঙ্গে তুলনা করা যায়।
৩.১ একেশ্বরবাদ ও নৈতিক সংস্কার
শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র নবী মুহাম্মদকে দেখিয়েছেন সত্যিকারের একেশ্বরবাদের প্রচারক হিসেবে। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক—মূর্তিপূজা, সামাজিক অন্যায় আর খারাপ প্রথার বিরুদ্ধে লড়েছেন। এ ছবি ব্রাহ্মসমাজের ভাবনার সঙ্গেই মিলে যায়। ব্রাহ্মরা যেমন এক ঈশ্বরকে মানত, সামাজিক সংস্কার চাইত, আর যুক্তির ওপর ধর্ম গড়তে চাইত, তেমনি মিত্রও নবীর জীবনকে একটি সার্বজনীন নৈতিক শিক্ষা হিসেবে দেখেছেন। মিত্রর মতে, নবীর ডাক শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সত্য ও বিবেক মেনে চলতে চাওয়া সব মানুষের জন্য। তাই হিন্দু বা অন্য যে কেউ তাঁর জীবনকে শ্রদ্ধা করতে পারে। এভাবে মিত্র নবীকে শুধু ইসলামের ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং মানবতার জন্য এক আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তবে ইসলামী সীরাহয় নবীকে এভাবে দেখা হয় যে, তিনি একেশ্বরবাদ ও ন্যায়বিচারের প্রচারক হলেও তাঁর কর্তৃত্ব আসে আল্লাহর কাছ থেকে। কোরআন শুধু নৈতিক শিক্ষা নয়, বরং আল্লাহর সরাসরি বাণী। নবীর মিশন শুধু সংস্কারকের নয়, বরং আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের। তাঁর জীবন, কথা, কাজ সবই আল্লাহর নির্দেশিত। তাই মুসলমানদের কাছে নবীর জীবন হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত আইন ও সমাজ গঠনের ভিত্তি।
৩.২ মুজিজা ও অলৌকিক ঘটনা
মিত্রর মহম্মদ চরিত বইতে অলৌকিক ঘটনার জায়গা খুবই কম। ব্রাহ্মসমাজ যুক্তিবাদী ধর্মে বিশ্বাস করত। তাদের কাছে ধর্ম মানে যুক্তি, নৈতিকতা আর এক ঈশ্বরের উপাসনা। তাই মিত্র অলৌকিক ঘটনার গুরুত্ব দেননি। যদি উল্লেখও করেন, সেটা খুব সংক্ষেপে বা প্রতীকীভাবে। তাঁর আসল জোর ছিল নবীর মানবিক গুণের ওপর—সততা, সাহস, দয়া, সমাজ বদলানোর ক্ষমতা। নবীকে তিনি ইতিহাসের মহান মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে নয়। এভাবে দেখা উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিদের চিন্তার সঙ্গে মিলে যায়। তারা বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাদের কাছে ধর্ম মানে যুক্তির ওপর দাঁড়ানো বিষয়, অলৌকিক ঘটনা নয়। তাই ধর্মীয় নেতার আসল মূল্য হলো তাঁর নৈতিক শিক্ষা আর মানবিক উন্নতির কাজ।
কিন্তু ইসলামে কোরআনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিজা ধরা হয়। কারণ এটি আল্লাহর সরাসরি বাণী। এছাড়াও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, মেরাজের ঘটনা ইত্যাদি নানা মুজিজার কথা সীরাহ ও হাদিসে পাওয়া যায়। এগুলো নবীর বিশেষ মর্যাদা ও আল্লাহর সমর্থনের নিদর্শন। অন্যদিকে মিত্র এসব বাদ দিয়েছেন। তাঁর নবীর জীবনী থেকে অলৌকিক দিক মুছে গেছে। রয়ে গেছে একজন সাহসী সংস্কারক ও দূরদর্শী নেতার কাহিনি। ফলে মুসলমানদের কাছে নবীর পবিত্র মর্যাদা যেখানে ঈশ্বরের সমর্থনের ওপর দাঁড়িয়ে, সেখানে মিত্রর বর্ণনায় তিনি কেবল নৈতিক মহত্ত্বের প্রতীক।
৩.৩ আইন, সমাজ ও নেতৃত্ব
মহম্মদ চরিত গ্রন্থে মিত্র নবীকে মূলত একজন নেতা হিসেবে দেখিয়েছেন, যিনি গোত্রগুলিকে এক করেছেন, ঝগড়া থামিয়েছেন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়েছেন। তিনি নবীর প্রশংসা করেছেন একজন দিকনির্দেশক হিসেবে, যিনি তাঁর জনগণকে নতুন পথ দেখিয়েছেন। এই ছবি ব্রাহ্মসমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে মিলে যায়—নৈতিক সংস্কার, ঐক্য, শৃঙ্খলা। আবার এটা মিত্রর সময়কার জাতীয়তাবাদী ভাবনার সঙ্গেও মানিয়ে যায়। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে নবী কেবল নেতা নন, বরং আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও ইসলামী আইনের প্রণেতা। তাঁর জীবন ও কথা (সুন্নাহ) মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় কর্তৃত্ব বহন করে। সীরাহ শুধু গল্প নয়, বরং কোরআনের আয়াতের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে এবং ইসলামী আইন-প্রথার ভিত্তি গড়ে দেয়। মিত্র নবীর সামাজিক ও নৈতিক মাহাত্ম্য মানলেও, তাঁর ধর্মীয় কর্তৃত্ব মানেননি। তিনি নবীকে সমাজসংস্কারক হিসেবে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু রাসূল ও আইনদাতা হিসেবে দেখাননি।
৩.৪ কোরআন ও ওহি
মহম্মদ চরিত গ্রন্থে কোরআনকে মিত্র মূলত নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া এক মহৎ গ্রন্থ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে কোরআন হলো ন্যায়ের পথ দেখানোর বই। তবে তিনি ওহিকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে আসা বার্তা) যুক্তিবাদীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—যেমন নৈতিক জাগরণ বা বিবেকের কণ্ঠস্বর। কিন্তু ইসলামে কোরআন আল্লাহর সরাসরি বাণী। এটা কেবল নৈতিক শিক্ষা নয়, বরং অবিকৃত ঐশী বাণী। নবীর প্রথম ওহি হিরার গুহায় পাওয়া, মক্কায় দাওয়াত দেওয়া আর মদিনায় সমাজ গড়ার কাহিনি—সবকিছু কোরআনের ঐশী উৎসের ওপর দাঁড়িয়ে। অতএব মিত্র কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও, সেটাকে পুনর্নির্বাচিত করে মানবিক নৈতিক বই বানিয়েছেন। মুসলমানদের কাছে যেখানে কোরআন সর্বোচ্চ ঐশী আইন, সেখানে মিত্র সেটিকে মানবিক নৈতিকতার নির্দেশিকা হিসেবে তুলে ধরেছেন।
৩.৫ নবীর চরিত্র (আখলাক)
নবীর চরিত্র বিষয়ে মিত্রর বর্ণনা ইসলামী সীরাহর সঙ্গে অনেকটাই মেলে। দু’জনেই নবীকে সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, সাহসী, দয়ালু এবং ন্যায়ের প্রতি নিবেদিত হিসেবে দেখিয়েছেন। এগুলো এমন গুণ, যা যে কোনো ধর্মের মানুষ শ্রদ্ধা করতে পারে। তবে পার্থক্য হলো ব্যাখ্যায়। ইসলামে নবীর আখলাক তাঁর রাসূলত্ব ও ওহির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাঁর নৈতিকতা আসে সরাসরি আল্লাহর দিকনির্দেশ থেকে। কিন্তু মিত্র নবীর চরিত্রকে ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করে কেবল নৈতিক আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এর ফলে নবীর জীবন সব ধর্মের মানুষের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে যে পবিত্র ও ঐশী গভীরতা আছে, তা কমে গেছে।
৪. মিত্র কেন এভাবে লিখলেন?
৪.১ ব্রাহ্মসমাজের সার্বজনীনতা
ব্রাহ্মসমাজ মনে করত সব ধর্মের মধ্যে কিছু না কিছু মিল আছে। তাদের লক্ষ্য ছিল সেই মিলগুলো খুঁজে বের করা। তাদের কাছে ধর্মের আসল ভিত্তি হলো— এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, নৈতিক নিয়ম মানা, সত্যবাদিতা, সহানুভূতি, আর সমাজ সংস্কারের ইচ্ছে। তারা মূর্তিপূজার বিরোধিতা করত, জাতিভেদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াত। তারা চাইত ধর্ম যেন কুসংস্কার বা অন্ধ আচার নয়, বরং যুক্তি আর বিবেক দিয়ে চালিত হয়। তাই যখন ব্রাহ্ম চিন্তাবিদরা নবীজির জীবন (সীরাত) দেখতেন, তখন তারা জোর দিতেন সেই দিকগুলোতে যেগুলো তাদের ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়—যেমন: এক ঈশ্বরে ভক্তি, সততা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা। কপ্ফ নামে এক গবেষক বলেছেন, ব্রাহ্মরা প্রায়শই যুক্তি আর মানবতাকে দেবত্বের মতো মানত, এবং ধর্মকে চালিত করত সেগুলোর মাধ্যমে। হ্যাচার আরও বলেন, তারা বিভিন্ন ধর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা সার্বজনীন ধর্ম তৈরি করতে চাইত, যেখানে গুরুত্ব থাকত নীতি, ন্যায়বিচার আর মানবমর্যাদায়।
৪.২ ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা ও ভিক্টোরীয় অভ্যাস
১৯শ শতকে ইংরেজিতে লেখা অনেক বই ইসলাম (এবং অন্যান্য ধর্ম) নিয়ে বলত। সেখানে ধর্মপ্রবর্তকদেরকে অনেক সময় প্রথমে নৈতিক শিক্ষক হিসেবে দেখানো হতো, পরে নবী হিসেবে—বা অনেক সময় একেবারেই নবী হিসেবে নয়। ক্লিন্টন বেনেট-এর গবেষণায় দেখা যায়, ভিক্টোরীয় যুগে ইসলাম নিয়ে কেউ ইতিবাচকভাবে লিখেছেন, আবার কেউ নেতিবাচকভাবে। কিন্তু দুই দিকেই একটা বিষয় সাধারণ ছিল—আধুনিক নৈতিক মানদণ্ড দিয়েই ধর্মকে দেখা। বাঙালি সংস্কারকরা, যারা এইসব লেখা পড়তেন আর অনুবাদ করতেন, তারাও এই অভ্যাস কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন।
৫. আন্তঃধর্মীয় সীরাত: সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা
নবীজির জীবনী নিয়ে আন্তঃধর্মীয় লেখা, যেমন শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র করেছিলেন, একদিকে নতুন দরজা খুলে দেয়, আবার অন্যদিকে কিছু জটিল সমস্যাও তৈরি করে। এতে কিছু বড় লাভ হয়, আবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বাদও পড়ে যায়। দুই দিক একসাথে ভাবলে আমরা বুঝতে পারি, এমন কাজের আসল মূল্য কতটা এবং সীমাবদ্ধতাই বা কোথায়। প্রথম লাভ হলো সহজবোধ্যতা। মিত্রের বইয়ের মাধ্যমে বাংলার অমুসলিমরা নবীজিকে এমনভাবে জানতে পেরেছিল, যেভাবে তারা সহজে বুঝতে পারে। কঠিন ধর্মীয় ধারণার বদলে তিনি নবীজিকে দেখিয়েছিলেন এক সংস্কারক হিসেবে—যিনি কুসংস্কার, মূর্তিপূজা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন। এটা ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারক আর উনিশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের ভাবনার কাছাকাছি ছিল। ফলে হিন্দু পাঠকদের কাছে নবীজি ন্যায়, সততা ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।
দ্বিতীয় লাভ হলো সম্মানজনক ভঙ্গি। মিত্র বিদ্রূপ বা আক্রমণাত্মক ভাষায় লেখেননি—যেটা দুঃখজনকভাবে অনেক ঔপনিবেশিক লেখায় দেখা যেত। বরং তিনি নবীজির সাহস, ধৈর্য ও নৈতিক চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। সেই সময়ে এটি ছিল বিরল, আর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উন্নত করতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তৃতীয় লাভ হলো আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি। নবীজিকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ভাগাভাগি করতে পারে, মিত্র কৌতূহল জাগিয়েছিলেন। তাঁর বই পাঠকদের ইসলাম নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে উৎসাহিত করতে পারত, হয়তো আন্তঃধর্মীয় আলাপচারিতাও এগিয়ে দিত। এতে বোঝা যায় আন্তঃধর্মীয় জীবনী একে অপরের প্রতি সহমর্মিতা গড়তে পারে এবং কুসংস্কার কমাতে পারে।
তবে এর কিছু বড় ক্ষতিও ছিল। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো ওহি ও পবিত্র কর্তৃত্বের বিষয়টি বাদ পড়া। মুসলমানদের কাছে নবীজি কেবল সংস্কারক বা নৈতিক শিক্ষক নন; তিনি আল্লাহর রাসূল, যিনি কুরআন পেয়েছিলেন। সীরাতের আসল মানে এই দিকের ওপর নির্ভর করে। এটাকে বাদ দিলে গল্পের ধরণই বদলে যায়। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো মোজেজা ও অদৃশ্য বিষয় বাদ দেওয়া। ঐতিহ্যগত সীরাতে কুরআনকে এক চিরস্থায়ী মোজেজা ধরা হয়, আর আরও অনেক নিদর্শন আছে যা আল্লাহর সমর্থন প্রমাণ করে। যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যেমন মিত্রের ছিল, সেসব সাধারণত উপেক্ষা করে। এতে মুসলিম দৃষ্টিতে জীবনী অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।
তৃতীয় বিষয় হলো নিয়ম বা আদর্শের প্রশ্ন। ইসলামে নবীজির জীবন শুধু নৈতিক শিক্ষা নয়, বরং ইবাদত, শরিয়ত, দৈনন্দিন জীবন—সবকিছুর জন্য অনুসরণীয়। যদি কেবল নৈতিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে নবীজি হয়ে যান শুধু একজন জ্ঞানী শিক্ষক, মুসলমানদের জন্য পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশক আর থাকেন না। এতে সীরাতের আসল মানে পাল্টে যায়। শেষে নৈতিক ভাবনার জায়গাও আছে। ইতিহাস যে কেউ লিখতে পারে, কিন্তু যখন কোনো পবিত্র ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা হয়, তখন বাড়তি সতর্কতা জরুরি। সঠিক সূত্র ব্যবহার করা উচিত, লেখকের অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত (যেমন মিত্র করেছিলেন ব্রাহ্ম সংস্কারক হিসেবে), আর ভুল ধারণা বা স্টেরিওটাইপ এড়িয়ে চলা উচিত। জীবন্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ করাও সহায়ক হতে পারে। খালিদি আর বেনেটের মতো গবেষকরা বলেছেন, আন্তঃধর্মীয় লেখায় এসব নিয়ম মানা খুবই জরুরি। সব মিলিয়ে, মিত্রের বই দেখায় আন্তঃধর্মীয় সীরাতের একদিকে সম্ভাবনা, অন্যদিকে ঝুঁকি। এতে সম্মান ও আলাপ আসতে পারে, আবার বিশ্বাসীদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র দিকগুলো বাদও পড়ে যেতে পারে।
৬. গ্রহণ ও উত্তরাধিকার
মোহাম্মদ চরিত বইটি কেমনভাবে গৃহীত হয়েছিল সে বিষয়ে সরাসরি তথ্য বেশি নেই। তবে পরিস্থিতি দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। বাঙালি হিন্দু আর ব্রাহ্ম পাঠকেরা বইটিকে সম্ভবত স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ এতে ইসলামকে সম্মানজনকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, আর সেটা সংস্কার আন্দোলনের ভাবনার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। মুসলিম পাঠকদের প্রতিক্রিয়া হয়তো মিশ্র ছিল—কেউ হয়তো নবীজির চরিত্র নিয়ে শ্রদ্ধাশীল ভাষা দেখে খুশি হয়েছিলেন, আবার কেউ হয়তো খেয়াল করেছিলেন যে বইটিতে ইসলামের পূর্ণ ধর্মীয় বার্তা ধরা হয়নি। মিত্র পরে বুদ্ধদেব চরিত আর অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নিয়েও লিখেছিলেন। এতে বোঝা যায় তিনি চেয়েছিলেন বিভিন্ন ধর্মকে আন্তঃধর্মীয় “পরিচিতি” আকারে তুলে ধরতে। এই বই দক্ষিণ এশিয়ার এমন কিছু লেখার অংশ, যেখানে নবীজিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থাপন করা হলেও তাঁর অবস্থানকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
উপসংহার
মোহাম্মদ চরিত হলো নবী মুহাম্মদের জীবনীকে বাংলায় বর্ণনা করার একটি বিরল ও মূল্যবান প্রচেষ্টা, যা বঙ্গীয় নবজাগরণের সময়ে বৃহত্তর পাঠকের জন্য লেখা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র শ্রদ্ধা ও প্রশংসার ভঙ্গিতে লিখেছেন। তিনি নবীকে দেখিয়েছেন এক সাহসী সংস্কারক, মানুষের ঐক্যসাধক এবং নৈতিক আদর্শ হিসেবে। এইভাবে তিনি নবীজিকে ব্রাহ্ম ও সংস্কারক পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে, তাঁর এই চিত্রণে মুসলমানদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো কিছুটা হ্রাস পেয়েছে—যেমন ওহি (প্রকাশিত বাণী), মোজেজা (অলৌকিক ঘটনা), এবং সুন্নাহর (নবীর জীবনাচরণের) কর্তৃত্ব। এই পরিবর্তন ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী ও সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঔপনিবেশিক যুগের প্রবণতাকে প্রকাশ করে, যেখানে ধর্মপ্রবর্তকদের আধুনিক জীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষক হিসেবে দেখা হতো।
ফলাফল দাঁড়িয়েছে এমন এক আন্তঃধর্মীয় সীরাত, যা একদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্মানজনক, কিন্তু অন্যদিকে বাছাই করা ও নতুনভাবে গড়া। এই লেখা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে—কীভাবে নবীজিকে “উম্মাহর সীমার বাইরে” বর্ণনা করার চেষ্টায় সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি সীমাবদ্ধতাও আছে। এটি ভবিষ্যতের আন্তঃধর্মীয় লেখকদের উৎসাহিত করে এমনভাবে লিখতে—যাতে একদিকে লেখা সহজবোধ্য ও ন্যায্য হয়, অন্যদিকে স্পষ্টভাবে বলা হয় কোথায় মুসলিম বিশ্বাস থেকে ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়ে গেছে।