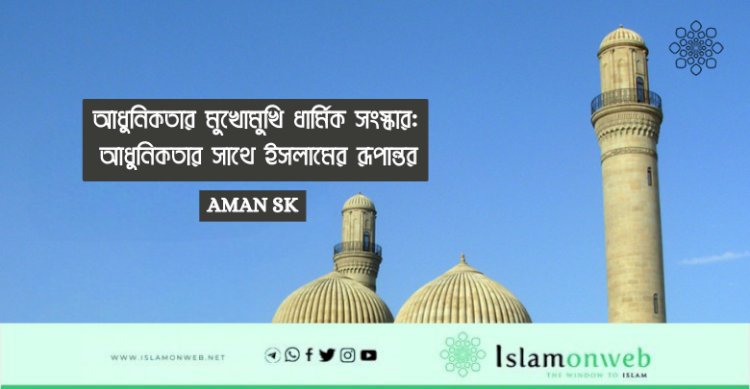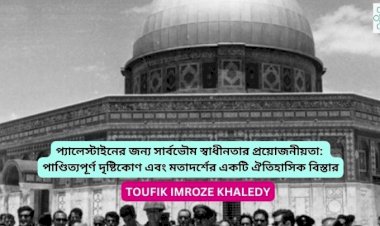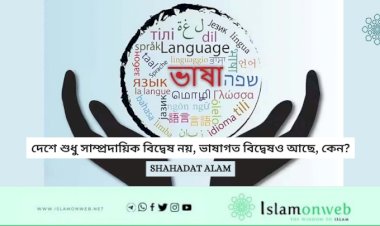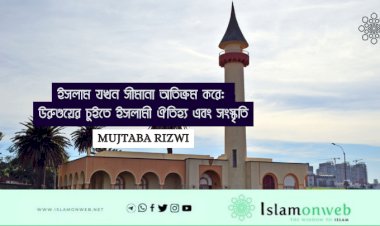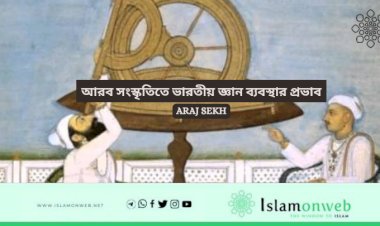আধুনিকতার মুখোমুখি ধার্মিক সংস্কার: আধুনিকতার সাথে ইসলামের রূপান্তর
ভূমিকা :
সালাফি আন্দোলন— নামে পরিচিত এই চিন্তাধারার অনুসারীরা তাদের নামটি নিয়েছেন "সালাফ" শব্দ থেকে, যার অর্থ—ইসলামের প্রথম যুগের ধার্মিক ও বিশুদ্ধপ্রাণ মুসলিম প্রজন্ম। এই সংস্কারকরা বিশ্বাস করতেন, সেই আদর্শ যুগের অনুসরণ করেই ইসলামকে আবার তার মূল ও বিশুদ্ধ রূপে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ১৮ শতকে মুসলিম বিশ্বে যে সব পুনর্জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাদের বেশিরভাগই ছিল শুদ্ধতাবাদী রীতি। তারা মনে করতেন, প্রাথমিক মুসলিম সমাজ ছিল অনেক শক্তিশালী, পরিশ্রমী, এবং সত্যিকার ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী। তাদের মতে, পরবর্তী যুগে ইসলামকে দুর্বল করে তোলে কিছু কুসংস্কার, অন্ধ অনুসরণ এবং বাইরের সংস্কৃতির প্রভাব—যেমন গ্রিক যুক্তিবিদ্যা ও পারস্যের সুফিবাদ।
১৮০০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এই শুদ্ধতাবাদী চিন্তাধারা দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়:
- আধুনিকতাবাদী শুদ্ধতাবাদী
- ঐতিহ্যবাদী শুদ্ধতাবাদী
এই দুই গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল এক—সালাফদের যুগের ইসলামকে ফিরিয়ে আনা। তবে তাদের পথ ছিল ভিন্ন, বিশেষ করে আধুনিকতার প্রতি তাদের মনোভাব ছিল একেবারে বিপরীত।
আধুনিক শুদ্ধতাবাদীবাদের রূপরেখা ও সৈয়দ আহমদ খানের ভূমিকা
আধুনিকতাবাদী শুদ্ধতাবাদী চিন্তা মূলত আধুনিকতা ও পশ্চিমা প্রভাবের মোকাবেলায় গড়ে উঠেছিল। এই ধারার চিন্তাবিদরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগের সরল, যুক্তিসম্মত ইসলামকে আদর্শ হিসেবে ধরেছিলেন এবং সেটিকে নতুন যুগের প্রসঙ্গে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই ধারায় ভারতীয় মুসলিম চিন্তাবিদ সৈয়দ আহমদ খান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হলে আধুনিক চিন্তা ও পশ্চিমা বাস্তবতার সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। এজন্য তিনি যুক্তিবাদ ও আইনের উদার ব্যাখ্যার উপর জোর দেন। ১৮৬৮ সালে তিনি পশ্চিমা জীবনধারা গ্রহণ করেন, এবং ১৮৭৫ সালে ভারতের আলিগড়ে প্রতিষ্ঠা করেন
অ্যাংলো-মুহাম্মদান ওরিয়েন্টাল কলেজ—যা আজকের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। এটি হয়ে ওঠে ইসলামী সংস্কারবাদী শিক্ষার অন্যতম সফল কেন্দ্র।
সৈয়দ আহমদ খান শুধু সংস্কারক নন, বরং তিনি ছিলেন এক সাহসী চিন্তাবিদ যিনি ইসলামী চিন্তার পরিধি প্রসারিত করেছিলেন। তিনি কুরআনের পাশাপাশি বাইবেলেরও ব্যাখ্যা লেখেন এবং "তাহযীব আল-আখলাক" নামে একটি উর্দু সাময়িকী চালু করেন, যা সেই সময়ের অন্যতম চিন্তাশীল ইসলামি মুখপত্রে পরিণত হয়। তার চিন্তাধারায় পাওয়া যায় শাহ ওলিউল্লাহ-প্রভাবিত সংস্কারবাদী মনোভাব, যেখানে অন্ধ অনুসরণ (তাকলিদ) ও নতুন উদ্ভাবিত ধর্মীয় রীতির বিরোধিতা রয়েছে।
তবে এর পাশাপাশি তিনি কিছু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণাও গ্রহণ করেন, যেমন ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এবং এই বিশ্বাস যে কুরআনের কোনো আয়াত প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত হতে পারে না।
তার ভাষায়—
If the word [of the Quran] is not according to the work [the law of nature], then the word cannot be the word of God
“যদি কুরআনের বাণী প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে না মেলে, তবে সেটি আল্লাহর বাণী হতে পারে না।”
তবে তিনি এটাও বলেন, আমরা মানুষ এখনও প্রকৃতির নিয়ম ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারিনি। তিনি ইজমা বা সর্বসম্মত মতকেও চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না, বরং মনে করতেন, যুক্তিবোধ ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি।
হাদীস নিয়ে সৈয়দ আহমদ খানের সংকট ও তার বিশ্লেষণধর্মী অবস্থান
১৮৬০-এর দশকে, সৈয়দ আহমদ খান যখন ব্রিটিশ লেখক উইলিয়াম মুইর-এর হাদীসবিষয়ক সমালোচনার মুখোমুখি হন, তিনি গভীরভাবে বিচলিত হন। তিনি বুঝে ফেলেন, ইসলামকে আক্রমণের একটি নতুন পথ খুলে গেছে—যেটা ছিল বাইরের শত্রুদের বুদ্ধিবৃত্তিক আঘাত। ১৮৭০ সালে তিনি মুইর-এর বইয়ের জবাব লেখা শুরু করেন। যদিও তিনি অনেক পশ্চিমা সমালোচনাকেও আংশিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, প্রাচীন মুসলিম আলেমরা হাদীসের বিষয়বস্তুর যাচাই-বাছাই (content criticism) যথাযথভাবে করেননি। তার মতে, হয়তো তারা এই কাজটা ভবিষ্যতের আলেমদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, হাদীসগুলো লিখিত রূপ নিতে সময় নিয়েছিল, আর সেই একই সময়ে অনেক জাল হাদীস ছড়িয়ে পড়েছিল—যেগুলো মূলত নবীজিকে অতিরিক্ত গৌরবিত বানিয়েছিলেন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি বেছে নিয়েছিলেন —হাদীস বর্ণনায় সারমর্ম বা সাধারণ অর্থে বলার অনুমতি থাকায় অনেক হাদীসের আসল বক্তব্য অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।
এই সমস্যার সমাধানে তিনি নিজের জীবনের বড় একটি সময় ব্যয় করেন। তার অবস্থান ছিল স্পষ্ট:
হাদীসকে আধুনিক যুক্তিবোধ, কুরআনের মূলনীতি ও ঐতিহাসিক সত্য অনুযায়ী নতুনভাবে যাচাই করতে হবে।
এই যাচাইয়ের জন্য তিনি একধরনের সমালোচনামূলক পদ্ধতি প্রস্তাব করেন—যেটি তিনি তৈরি করেন তিনটি জায়গা থেকে:
- হানাফি মাজহাবের নীতিনির্ভর বিচারপদ্ধতি
- মু’তাজিলা দর্শনের যুক্তিনির্ভরতা
- পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
তার মতে, যেসব হাদীস যুক্তির সঙ্গে মানে না, নবীজির মর্যাদাকে খাটো করে, অথবা কুরআন বিপরীত
সেগুলো বাতিল করা উচিত। তিনি আরও বলেন, হাদীসের বর্ণনাকারীরা সবাই যেন যোগ্য আলেম হন, এটা হানাফিদের মতোই অপরিহার্য শর্ত হওয়া দরকার।
তিনি শুধু মুতাওয়াতির হাদীস (অর্থাৎ বহু মানুষের মাধ্যমে টানা বর্ণিত) ছাড়া বাকি সব হাদীসকে পরীক্ষার আওতায় আনার পক্ষে ছিলেন। তার মতে, ইতিহাসভিত্তিকভাবে নির্ভরযোগ্য হাদীস আসলে মাত্র পাঁচটি। তিনি মনে করতেন, অলৌকিক ঘটনা বা বাস্তবে অসম্ভব কোনো কাহিনি বর্ণনাকারী এমন হাদীসগুলোকেও বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ডে পরখ করা উচিত।
সৈয়দ আহমদ খানের হাদীস বিশ্লেষণের পদ্ধতি তাকে অনেকক্ষেত্রেই প্রচলিত ইসলামী ধারা থেকে ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। তিনি মনে করতেন, নবীজির সুন্নাহ শুধু ধর্মীয় বিষয়েই প্রযোজ্য, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক আইনকানুনে নয়। এজন্য তিনি এমন সাহসী মত দেন যে, নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজ ছিল আসলে একটি স্বপ্নের ঘটনা—যেখানে অধিকাংশ সুন্নি ও শিয়া মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, তিনি শারীরিকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, নবীজি অলৌকিক কোন মুজিযা করেননি।
চিরাগ আলীর মতো, তিনি কুরআনে “জিন” শব্দ ব্যবহারের বিষয়েও ব্যতিক্রমী ব্যাখ্যা দেন। তার মতে, জিন বলতে কোনো অদৃশ্য বা অতিপ্রাকৃত প্রাণী নয়—বরং এটি হয়তো আরব অঞ্চলের কোনো সেমিটিক গোত্রকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
যদিও তিনি অনেক ওরিয়েন্টালিস্ট (পশ্চিমা গবেষক)–এর হাদীসবিষয়ক সমালোচনা মেনে নিয়েছিলেন, তবুও তার আসল লক্ষ্য ছিল ইসলামকে পশ্চিমা সংশয়বাদ ও যুক্তিহীন সমালোচনা থেকে রক্ষা করা। যেমন, যখন উইলিয়াম মুইর বলেন, কুরআনের কিছু অংশ হারিয়ে গেছে—তখন সৈয়দ আহমদ খান হাদীসের মাধ্যমেই তার জবাব দেন।
তিনি প্রস্তাব করেন, হাদীস যাচাইয়ের জন্য কুরআনকেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এতে তিনি এমন একটি যৌক্তিক মাপকাঠি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যা মুসলিম ও পশ্চিমা গবেষক—দু’পক্ষই গ্রহণ করতে পারে। কারণ, পশ্চিমারা কুরআনকে তুলনামূলকভাবে ইতিহাসভিত্তিক দলিল হিসেবে গ্রহণ করত।
আধুনিকতার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টায় তিনি এমনকি বাইবেলের পক্ষেও অবস্থান নেন। যখন ইউরোপীয় সমালোচকরা বলেন, হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ের মহাবন্যা সারা পৃথিবীজুড়ে হয়নি বা ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই—তখন খান বলেন, হ্যাঁ, সেই বন্যা হয়েছিল, তবে তা ছিল কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমিত।
মিশরে আধুনিক শুদ্ধতাবাদীবাদের উত্থান ও মুহাম্মদ আবদুহর যুক্তিনির্ভর অবস্থান
যখন ভারত উপমহাদেশে সৈয়দ আহমদ খান ইসলামী চিন্তায় নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছিলেন, তখন মিশরেও আধুনিক শুদ্ধতাবাদীবাদ এক নতুন জাগরণে রূপ নিচ্ছিল। আর এই প্রবাহের নেতৃত্বে ছিলেন মিশরের আলেম মুহাম্মদ আবদুহ (মৃত্যু: ১৯০৫) এবং তার সিরীয় ছাত্র রাশিদ রিদা (মৃত্যু: ১৯৩৫)। আবদুহ কায়রোর বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ১৮৮২ সালে তাকে মিশর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পরে তিনি লেবানন ও ফ্রান্সে ঘুরে মিশরে ফিরে এসে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে প্রধান মুফতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
হাদীস নিয়ে তিনি খুব কাঠামোগত বা বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা না করলেও, সুন্নাহকে ইসলামী আইন ও বিশ্বাসের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন—হাদীস যাচাইয়ের প্রচলিত পদ্ধতি যথেষ্ট নয়, এবং হাদীসের মূল সংগ্রহ (corpus) কে সমালোচনামূলকভাবে পুনর্বিবেচনা করা দরকার। তার মতে, যেসব হাদীস নবীজির নিশ্চিত সুন্নাহ হিসেবে প্রমাণিত, সেগুলো অমান্য করা যাবে না। তবে এর সংখ্যা খুবই সীমিত। আর যেসব হাদীস মুতাওয়াতির নয়, সেগুলোতে কেউ বিশ্বাস করতে চাইলে করতে পারে, কিন্তু কাউকে জোর করে বিশ্বাস করানো যাবে না, কিংবা তা অস্বীকার করায় অবিশ্বাসী বলা যাবে না। তিনি এমন হাদীসও প্রত্যাখ্যান করেন, যা আল্লাহর পূর্ণ মহান সত্তার ধারণাকে ক্ষুন্ন করে। ভবিষ্যদ্বাণী, কিয়ামতের নিদর্শন কিংবা ইসরাইলি উৎস থেকে আসা হাদীস নিয়েও তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন, এবং খুব কম সংখ্যক হাদীসকেই এসব বিষয়ে প্রামাণ্য মনে করতেন।
এই দৃষ্টিভঙ্গি—যে শুধু মুতাওয়াতির হাদীসই বিশ্বাসযোগ্য ও অপরিহার্য—এটি পরবর্তীতে আধুনিকতাবাদ ও আধুনিক শুদ্ধতাবাদীবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে আল-আজহারের ফাতওয়া কমিটি এই চিন্তাকে ধর্মীয় ফতোয়ার রূপ দিয়েছিল।
রাশিদ রিদা ও হাদীস বিশ্লেষণে নতুন চিন্তার ধারা
মুহাম্মদ আবদুহর প্রধান ছাত্র ছিলেন সিরীয় চিন্তাবিদ রাশিদ রিদা, যিনি তার শিক্ষক থেকে আরও বিস্তারিতভাবে হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আল-মানার নামে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, যেটি ইসলামী সংস্কারমূলক লেখার জন্য মুখ্য মঞ্চে পরিণত হয়েছিল।
রিদা যুক্তি দেন যে, ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হল কুরআন, আর শুধুমাত্র মুতাওয়াতির হাদীসই প্রকৃতভাবে নির্ভরযোগ্য। কারণ আহাদ হাদীস সর্বোচ্চ সম্ভাব্য জ্ঞান দিলেও নিশ্চিত জ্ঞান দেয় না। তিনি মুতাওয়াতির হাদীসকে মুসলিম সমাজে চালু ও চর্চিত সুন্নাহর সঙ্গে তুলনা করেন—যেমন নামাজ, হজের নিয়ম বা রাসূলের কিছু প্রসিদ্ধ বাণী। পক্ষান্তরে, হাদীসবইয়ের যে অধ্যায়গুলোতে রাসূলের আচরণ ও কথাবার্তার বিস্তারিত বা অপ্রচলিত বর্ণনা রয়েছে (যেমন—আদব বা শিষ্টাচার বিষয়ক), সেগুলো সাধারণত আহাদ হাদীস ভিত্তিক এবং সবসময় নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। সৈয়দ আহমদ খানের মতোই, রাশিদ রিদা বিশ্বাস করতেন যে ‘সাধারণ অর্থে বর্ণনা করা হাদীসের অনুমোদন’ বহু ভুলকে জন্ম দিয়েছে। কারণ এতে করে বর্ণনাকারীদের নিজস্ব ব্যাখ্যা বা মতামত অনিচ্ছাকৃতভাবে হাদীসে মিশে যেতে পারে।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—ইসরাইলিয়াত গ্রহণ করা এক ধরনের বিভ্রান্তির উৎস। যদিও অনেক প্রামাণ্য হাদীস সংকলনেও এগুলো পাওয়া যায়, রিদা বলেন, প্রাথমিক যুগের বর্ণনাকারী কাব আল-আহবার ও ওয়াহ্ব ইবন মুনাব্বিহ বিশ্বাসযোগ্য নন, কারণ তারা ইসরাইলিয়াত বর্ণনায় খুবই শিথিল ছিলেন।
আধুনিক যুগের গবেষকরা এদের গ্রহণযোগ্যতা বাতিল করতে পারেন—এই যুক্তি দেখিয়ে রিদা বলেন, বর্তমান সময়ে ইহুদি গ্রন্থের সঙ্গে এসব বর্ণনার তুলনা করা সম্ভব, যা আগের যুগের সমালোচকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি বলেন, কাব ও ওয়াহ্ব যেসব তথ্য দিয়েছেন তা তাওরাতের প্রকৃত বর্ণনার সঙ্গে মেলেনি। (বিঃদ্রঃ—নবম শতাব্দীর আলেম আল-জাহিজ মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রাচীন মুসলিমরা যখন ‘তাওরাত’ বলতেন, তারা পুরা হিব্রু ধর্মগ্রন্থকে বোঝাতেন।)
রিদা আরও জোর দেন যে, আহাদ হাদীসগুলোকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে পুনরায় বিশ্লেষণ করতে হবে। যদিও এই ধারা ইসলামী বিচারশাস্ত্রের পুরনো অংশ ছিল, পরে তা অনেকটাই উপেক্ষিত হয়েছে। রিদা একপর্যায়ে বলেন, প্রাচীন মুসলিমদের বিষয়ভিত্তিক হাদীস বিশ্লেষণই আধুনিক ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির অগ্রদূত।
উপসংহার
আধুনিকতাবাদী শুদ্ধতাবাদী চিন্তাধারা মূলত আধুনিকতার চ্যালেঞ্জের জবাবে গড়ে উঠেছিল। তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় অনেক সময় তারা ইসলামী ঐতিহ্য থেকে সাহসীভাবে ভিন্ন পথও অবলম্বন করেছেন। সৈয়দ আহমদ খান, মুহাম্মদ আবদুহ ও রাশিদ রিদার মতো চিন্তাবিদেরা হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আনেন—যা যুক্তিবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা ছিল।
তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে অগ্রসর বিশ্বে টিকিয়ে রাখা, বিকল্প ধর্মীয় চিন্তা গড়ে তোলা এবং পাশ্চাত্য সমালোচনার মুখে ইসলামের ভাবমূর্তি রক্ষা করা। যদিও এই প্রচেষ্টা অনেক বিতর্কের জন্ম দেয়, তবুও এই ধারাটি মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে।
(এই প্রবন্ধে প্রকাশিত সমস্ত মতামত, ধারণা ও বিশ্লেষণ সম্পূর্ণরূপে লেখকের ব্যক্তিগত। এতে লেখকের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে, যা কোনওভাবেই আমাদের প্ল্যাটফর্মের (বা এই প্ল্যাটফর্মের মালিক, সহযোগী বা প্রতিনিধিদের) মতামত, নীতি কিংবা অবস্থানকে প্রতিনিধিত্ব করে না।)
রেফারেন্স :
- Hadith Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World - JONATHAN A. C. BROWN
- Ahmad, Islamic Modernism, p. 53
- Christian W. Troll, Sayyid Ahmad Khan: A Reinterpretation of Muslim Theology