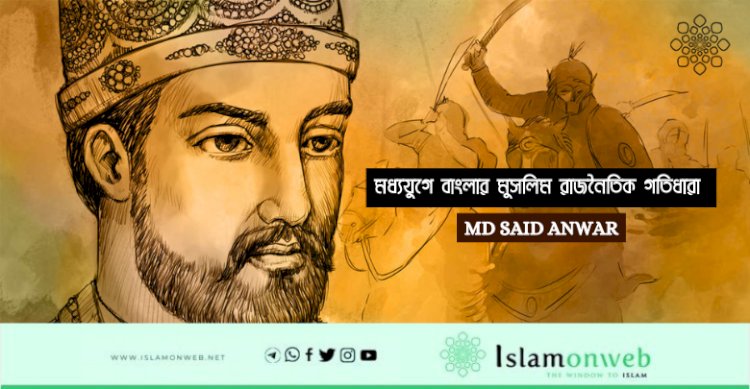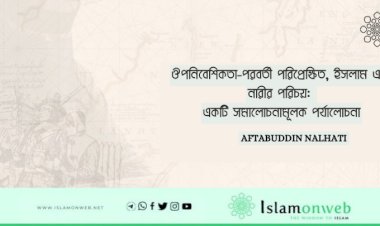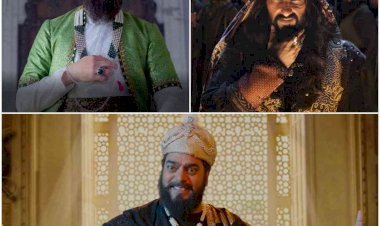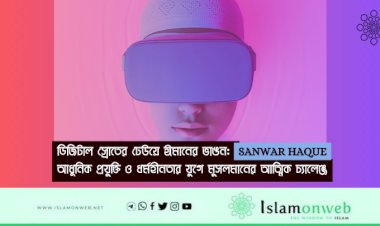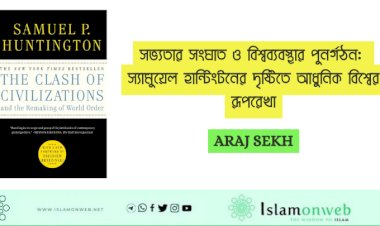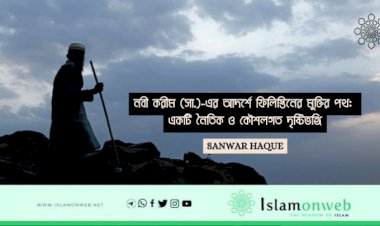মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক গতিধারা
ভূমিকা:
ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় মুসলমানদের বাংলা বিজয় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই অভিযান ছিল খুজ, খলজি, খালাজি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত মুসলিম উপজাতিদের ভারত সীমান্তের দিকে অভিযানের অংশবিশেষ। মোহাম্মদ বখতিয়ারের সেই অভিযানের সহজ সাফল্য সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। এবং এটি ভারতের অভ্যন্তরে তুর্কীদের এই অগ্রগতির প্রথম পর্ব যেটি (১২০২-০৩) নদিয়া অভিযানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। স্বাধীন ভাগ্যোন্বেষী সেনানায়ক বখতিয়ার খলজির নদিয়া অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগের সূচনা হয়।কিন্তু এই অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠন, আর এই লুণ্ঠনের প্রলোভন বখতিয়ার কে বাংলার রাজধানী গৌড়-লক্ষ্ণনাবতীর দিকে ধাবিত করে।গৌড় লক্ষ্ণনাবতীর সহজ বিজয় বখতিয়ারকে রাজ্য স্থাপনে উৎসাহিত করে।
রাজধানীর সহজ স্থাপন অন্যদিকে রাজার পলায়ন সেন-রাষ্ট্রের এমন পরিস্থিতি তাদের শেষ মর্যাদাটুকু বিলীন করে দেয়। সম্পূর্ণ নিজের শক্তি ও দক্ষতার বলেই বখতিয়ার বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলায় স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের যে ঐতিহ্য রেখে যান, তা পরবর্তীকালে বিস্তার লাভ করে গৌরবময় গৌড় সালতানাতে পরিণত হয়। তার শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গোষ্ঠীতন্ত্র ও মালিকানা। যা তার শাসনব্যবস্থাকে আরো দৃঢ় করে তোলে। বখতিয়ার সে যুগের কিছু মুসলিম আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কিছু বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে দ্বিধা করেনি, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম সংস্কৃতির প্রসারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি মাদ্রাসা ও মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন। একজন সৈনিক হয়েও বখতিয়ার উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সদ্য-প্রতিষ্ঠা মুসলিম রাষ্ট্র শুধু সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। এবং তার এই উপলব্ধি প্রমাণ করে যে তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি কতটা স্পষ্ট ছিল।
(১২০৬) খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির মৃত্যুর পর খলজিদের মধ্যে এক তীব্র অন্তবিরোধ বেধে যায়। হত্যাকারী আলি মর্দান খিলজীকে নজরবন্দী করে রাখা হয় এবং বখতিয়ারের অন্যতম সহচর শিরাণ খিলজি কে নেতৃপদে নির্বাচিত করা হয়। সেই সময় যদি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু রাজ্যগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ চালাত, তাহলে বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক গতিধারা হয়তো ভিন্ন রূপ নিত। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেরকম কিছুই ঘটল না। তবে যা ঘটতে চলেছিল তার সম্পর্কে হয়তো শিরন খলজী কখনো কল্পনা করেননি। তিনি যখন রাজ্যে শান্তি ও সংহতি আনতে বৃত্ত সেই সময় আলি মর্দান,খলজী নজরবন্দি থেকে পালায়ন করে সোজা দিল্লিতে সুলতান কুতুব-উদ্দিনের শরণাপন্ন হন। প্রাণ রক্ষা হলেও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রকাশ করে যে কাজ আলি মর্দান করেছে তা মুসলমান রাজ্যের জন্য সত্যি দুঃখ জনক। নিয়তি তার পরিণামে হয়তো কিছু ভয়ংকর পরিকল্পনা করেছিল।
সুলতান কুতুব-উদ্দিন বাংলার উপর দিল্লির নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। আর দিল্লির দরবারে আলি মর্দানের পলায়ন কুতুব-উদ্দিনকে সেই সুযোগ এনে দেয়। এবং দিল্লির নিযুক্ত সেনাপতি ও সেনাবাহিনীর এই প্রথম বাংলার মুসলিম রাজধানীতে প্রবেশ। দিল্লির হস্তক্ষেপে আলি মর্দান লখনৌতির শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই শাসন ছিল স্বল্প স্থায়ীহয়, মাত্র দুই বছর আলি মর্দানতার স্বৈরতন্ত্রী শাসন চালিয়ে যান। কিন্তু তার অকথ্য অত্যাচার সহ করতে না পেরে তার নিজ লোকেরাই সংঘবদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করে। আলি মর্দানের নিধনের পর (১২১৩) বাংলার আমির-ওমরাহরা হোসেন-উদ্দিন আইয়াজ খিলজীকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করে।‘সুলতান-উল-মুয়াজুম’সুলতান-উল-নাজম’ প্রভৃতি বিভিন্ন অভিধা গ্রহণ করে নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করেন। এমনকি নিজ মুদ্রায় খলিফা আল-নাসির এর নাম খোদাই করেন।
সুলতান আইয়াজ খিলজীর শাসনকালেই (১২১৩-২৭)বাংলায় প্রকৃত স্বাধীন ও সর্বভৌম মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় গৌড় ছিল বাংলা ও বিহারের বিজিত এলাকার কেন্দ্রস্থল এবং জলপথে সব এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পক্ষেও অধিক উপযোগী তাই তিনি নিজের রাজধানী গৌড়-লখনৌতিতে স্থাপিত করেন। রাজধানীকে সুসজ্জিত করার জন্য বহু সুরাম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মুসলিম শাসন অক্ষুন্ন রাখার জন্য আইয়াজ সুষ্ঠু মুসলিম সমাজ গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এবং তার জন্য তিনি বহু জ্ঞানী-গুণী ও সুফি-সন্তরাকে সসম্মানে বাংলার বুকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাদের উপযুক্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। আইয়াজ খলজীর এই পরিকল্পনা ও নবাগত মুসলিমদের আগমন বাংলার মুসলিম সমাজকে যথেষ্ট প্রাণবন্ত করে তোলে এবং মুসলিম রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার ওপর এক দৃঢ়প্রভাব ফেলে ও মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হয়। তার শাসনকালে মুসলিম রাজ্যের সীমা অজয় নদী থেকে আরও দক্ষিণে দামোদর ও বিষ্ণুপুর সীমানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এতকিছুর পরেও কিন্তু আইয়াজ খলজী ইলতুৎমিসের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাননি।(১২২৪) খ্রিস্টাব্দে ইলতুৎমিস বাংলার দিকে অগ্রসর হন। দিল্লি সুলতান কে বাধা দেওয়ার জন্য আইয়াজ খলজী সসৈন্যে অগ্রসর হলেন।
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মিনহাজের মতে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয় এবং আইয়াজ ইলতুৎমিসের বশ্যতা স্বীকার করেন। এবং দিল্লি সুলতানের নামে কালেমা পাঠ করতে ও সুলতানের নামঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করতে রাজি হন। আর এই ভাবেই সমসাময়িক লখনৌতি রাজ্যের স্বাধীন সত্তার বিলুপ্তি ঘটে। তবে এই পরাধীনতা ছিল ক্ষুণ্নস্থায়ী।ইলতুৎমিসের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইয়াজ সন্ধি ভঙ্গ করে বিহার পুনরুদ্ধার করেন। এই ঘটনা বাংলার মুসলিম রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।দিল্লির সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ সুলতানের জন্য এক ভীষণ রকম অপমানের ইঙ্গিত দেয়। আর এই অপমানের বদলা নিতে আইয়াজের অনুপস্থিতির সুযোগে ইলতুৎমিস তার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির-উদ্দিনকে লখনৌতি আক্রমণ করার আদেশ দেন। যুবরাজ আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এই দুঃসংবাদ শুনে আইয়াজ লখনৌতির দিকে ছুটে আসেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আই আজ পরাস্ত হন এবং তাকে হত্যা করা হয়। তবে যাই হোক বাংলার রাজনৈতিক,সামাজিক,ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইয়াজ খলজীর রাজত্বকালের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।
এরপর (১২২৭-১২৮৭) খ্রিস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালের অধিকাংশ সময় লখনৌতি রাজ্য দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু এই শাসনকালের অধিকাংশ শাসক ছিলেন সুলতানদের ‘ক্রীতদাস বা মামলুক’। এরা ছিল মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীভুক্ত। এদের অনেকে দিল্লির সুলতানদের সামান্য ভৃত্য হিসেবে জীবন শুরু করে পরবর্তীতে আমির,মালিক নামে বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ পদ লাভ করেন। এই তুর্কি মামলুকদের শাসনাধীন কালে লখনৌতির রাজদরবার দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হয়। লখনৌতির শাসনক্ষমতা যিনি জোর করে দখল করতেন, তিনি দিল্লির সুলতানদের উপঢৌকন পাঠিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতেন। দিল্লি সন্তুষ্ট হয়ে যেত ,আর বাংলার মামলুক শাসক স্বাধীনভাবে তাদের শাসনকার্য পরিচালিত করত। তবে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর প্রায় ৩০ বছর দিল্লিতে এক অরাজক অবস্থা চলে। এবং এই অবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লখনৌতির শাসকরা ইচ্ছেমতো শাসন করতেন। এবং সুযোগ মতো বিদ্রোহী হতেন। পরবর্তীতে গিয়াস-উদ্দিন বলবন দিল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে বাংলার শাসনকর্তাদের ওপর কড়া নজর রাখার জন্য সর্বপ্রথম নিজের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুচর মুখেস-উদ্দিন তুঘরালকে এই পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বলবনের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলে, বলবনের প্রতি তার অনুগত্যের যুক্তি দেখিয়ে তুঘরাল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামংকিত মুদ্রা প্রচার করেন। তুঘরালের মত এমন এক প্রিয় ও একনিষ্ঠ সেবকের বিদ্রোহ বলবনের কাছে মর্মান্তিক হয়ে ওঠে।
এই বিদ্রোহের সংবাদ বলবনের আহার ও নিদ্রা কেড়ে নেয়। আনুমানিক (১২৭৯)খ্রিস্টাব্দে বলবন এক বিশাল সেনা ও অশ্ব বাহিনী নিয়ে লখনৌতি অভিযানে অগ্রসর হন। সেই সংবাদ পেয়ে তুঘরাল তার সেনা পরিবারবর্গ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পলাতক হন ও আত্মগোপন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বহু চেষ্টার পর তুঘরালকে দমন করা হয়। এবং তার সঙ্গে যোগদানকারী সকলকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। এবং বলবনের এই কর্মকর্তা প্রমাণ করে যে প্রতারণার কোন ক্ষমা নেই সে যতই বিশ্বস্ত বা একনিষ্ঠ হোক না কেন।
সমাপনী মন্তব্য
(১৩২৮) খ্রিস্টাব্দের পর থেকে লখনৌতির ইতিহাস ক্রমেই বাংলার ইতিহাসে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই যুগ ছিল বাংলায় ও বাংলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দ্রুত ও স্থায়ী মুসলিম আধিকারের সম্প্রসারণের যুগ। কিন্তু সেই যুগেও বাংলার রাজপরিবারের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বাংলার রাজনীতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এবং অন্যান্য শক্তিকে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দেয়। ক্ষমতার লড়াই বাংলার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আবার বিঘ্নিত করে। বাংলার রাজনীতির এই গোলযোগের সময় হাজী ইলিয়াস শাহের আবির্ভাব ঘটে। (১৩৪২) তিনি লখনৌতি দখল করে ইলিয়াস শাহ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই শাসন কার্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সুলতান ইলিয়াস শহ এর মৃত্যুর পর বরবক শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি যে হাবশী খোজাদের নিজের প্রভাব বিস্তার ও নিজের শাসনকার্যকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমদানি করেন। তুর্কি ক্রিতদাসদের হাতে আব্বাসীয় খলিফাদের যে হাল হয়েছিল,হাবসি ক্রীতদাসদের হাতে ইলিয়াস শাহীদের প্রায় একই হাল হয়।(১৪৮৭) খ্রিস্টাব্দে হাবশিরা সিংহাসন দখল করে এবং (১৪৯৩) খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় তারা অধিষ্ঠিত থাকে। এরপর বাংলায় মুঘলদের পদার্পণ হয়। তার সাথে সাথে পর্তুগিজ ফরাসি ও ইস্ট ইন্ডিয়ার মত বহু বিদেশি শক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের হাত ধরে বাংলার বুকে পদার্পণ করে। চট্টগ্রাম চন্দননগরের মত অঞ্চলে তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কুটির নির্মাণ করে। পরবর্তীকালে বাংলার রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটে। বাংলায় মুঘলদের শাসন আমলে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। (১৬৯০) খ্রিস্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসি বাণিজ্য কুটির প্রতিষ্ঠা। চুঁচুড়ায় কলন্দাজ বাণিজ্যকুঠির প্রতিষ্ঠা। এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই ইউরোপীয় জাতিগুলি বাংলায় নিজেদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের শাসন। (১৭৪০) খ্রিস্টাব্দে বাংলার মসনদে আলিপুর দিখা উপবিষ্ট হয় বাংলায় প্রকৃত স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা হলেও সেই সময় ইংরেজদের রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তি বেড়ে যায় সেই কারণে বাংলার রাজনৈতিক ও সামরিক শাসক গোষ্ঠী বিদেশী ও ইউরোপীয় শক্তির উপর নির্ভর হতে শুরু করে। বৈদেশিক শক্তির ওপর নির্ভরতার এই সূচনা বাংলার ভাগ্যকে এক নতুন মোড় দেয় । যার শেষ পরিণতি হল (১৭৫৭)পলাশের যুদ্ধ।