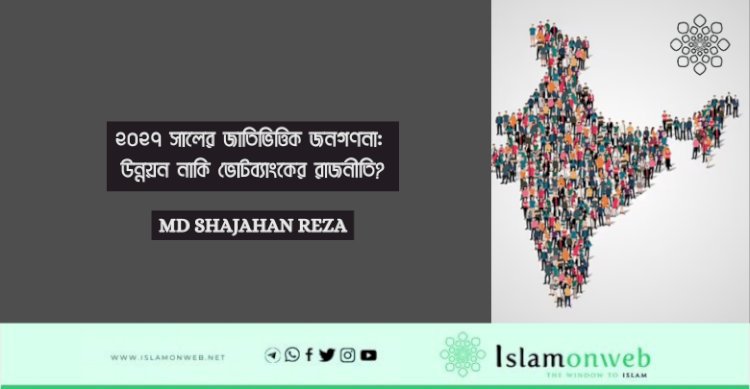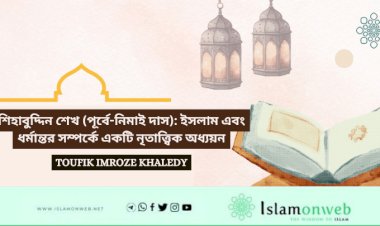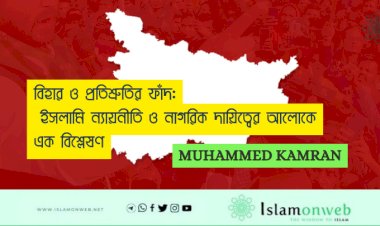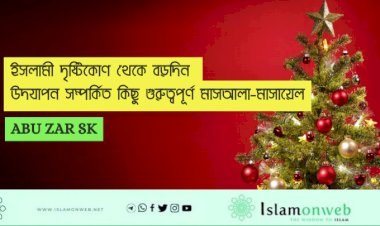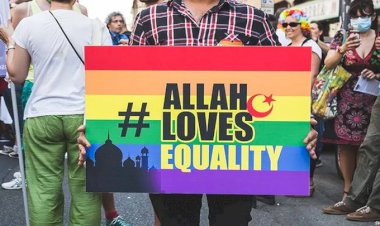২০২৭ সালের জাতিভিত্তিক জনগণনা: উন্নয়ন নাকি ভোটব্যাংকের রাজনীতি?
ভারতের ইতিহাসে ‘জাতি’ একটি এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা কেবল সমাজের সামাজিক বিন্যাসকে প্রভাবিত করেনি, বরং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাগত ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে দীর্ঘকাল ধরে উপস্থিত থেকেছে। এটি নিছক এক সামাজিক বিভাজনের প্রতীক নয়, বরং এটি ভারতীয় সমাজে সমতা ও ন্যায়ের ধারণাকে এত গভীরভাবে আঘাত করেছে যে, সংবিধানিকভাবে ঘোষিত “সমানাধিকার” কেবল একটি অলঙ্কারিক শ্লোগান হয়ে উঠেছে।
স্বাধীনতার পর ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সকল নাগরিককে সমানাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, জাতি-ভিত্তিক বৈষম্য এখনো জীবন্ত। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে যে, আমরা যদি সত্যিই একটি ন্যায্য ও সমতা-ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করতে চাই, তাহলে জাতিভিত্তিক জনগণনা কি অপরিহার্য নয়? নীতিনির্ধারণ, কল্যাণমূলক প্রকল্প ও সামাজিক ন্যায়ের বাস্তবায়নের জন্য একটি স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান কি আবশ্যক নয়? এই প্রবন্ধে সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজে জাতিভিত্তিক জনগণনার প্রয়োজনীয়তা, এর ইতিহাস, পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলি এবং এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণামসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
জনগণনার ইতিহাস ও জাতিগত শ্রেণিবিন্যাস
ভারতে আধুনিক জনগণনার সূচনা ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। ১৮৮১ সালে প্রথম সুসংগঠিত জনগণনা হয়, যেখানে ধর্ম, জাতি, পেশা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য প্রশাসনিক সুবিধা অর্জন, তথাপি এর মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের শ্রেণিগত ও গঠনমূলক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রস্তুত হয়।
১৮৮১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক দশকে পরিচালিত জনগণনায় জাতি বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকত। ১৯৩১ সালের জনগণনা ছিল শেষ, যাতে সমস্ত জাতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারত সরকার ১৯৫১ সালের জনগণনায় সিদ্ধান্ত নেয় কেবলমাত্র তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে, অন্য সকল জাতিসমূহের তথ্য উপেক্ষা করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল জাতপাতের অবসানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—যেমনটা চেয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু, সরদার প্যাটেল, বি.আর. আম্বেদকর ও আবুল কালাম আজাদ। তাঁদের যুক্তি ছিল, জাতি ভিত্তিক তথ্য সমাজে বিভাজন আরও বাড়াবে। কিন্তু বাস্তবে এটি বহু পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি থেকে বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
১৯৬১ সালে রাজ্য সরকারগুলোকে ওবিসি (অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণি) চিহ্নিত করার অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন তার রিপোর্টে জানায়, দেশের মোট জনসংখ্যার ৫২ শতাংশই ওবিসি। কিন্তু এই পরিসংখ্যানও ১৯৩১ সালের পুরনো জনগণনার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। এরপরে কোনো স্বতন্ত্র ও নির্ভরযোগ্য জাতিভিত্তিক তথ্য আর সংগৃহীত হয়নি।
১৯৯১ সালে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ওবিসি সম্প্রদায়কে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ প্রদান করে। কিন্তু পরিসংখ্যানের অভাবে এই সংরক্ষণ কখনও কিছু নির্দিষ্ট জাতির একচেটিয়া সুযোগের ক্ষেত্র তৈরি করেছে, আবার কখনো প্রকৃত দরিদ্র জাতিগোষ্ঠী বঞ্চিত থেকেছে। এই প্রেক্ষাপটে, জাতি-ভিত্তিক জনগণনাকে কেবল প্রশাসনিক নয়, বরং সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তি হিসেবেই দেখতে হবে।
জাতিগত জনগণনার বিরোধিতা ও তার বিশ্লেষণ
জাতিভিত্তিক জনগণনার বিরুদ্ধে এক শ্রেণির আপত্তি আছে। তাঁদের মতে, এই প্রক্রিয়া সমাজে আরও বিভাজন সৃষ্টি করবে এবং জাতি-সম্পর্কিত পরিচিতির কারণে বিভ্রান্তি ও সংঘাত বাড়বে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাতিভিত্তিক বিভাজন কি সমাজে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান নয়? বিভাজনের উপস্থিতি অস্বীকার করে এর স্বীকৃতি না দেওয়া কি বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার নামান্তর নয়? যেমন, আমরা যখন ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলের ভিত্তিতে জনগণনা করি, তখন জাতিকে অবজ্ঞা করা দ্বিচারিতা বৈ আর কিছু নয়। উল্লেখ্য, ১৯৫১ থেকে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের তথ্য সংগ্রহ করে সরকার কখনো কোনো সামাজিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করেনি। ফলে, জাতি ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ সংঘাতের কারণ হবে এই ধারণা ভিত্তিহীন।
আরও একটি আপত্তি হলো—যদি জাতিগত তথ্য প্রকাশ করা হয়, তবে অনেক জাতি সংরক্ষণের দাবি করবে। বাস্তবে, একটি সুনির্দিষ্ট ও নীতিনিষ্ঠ তথ্যভিত্তি থাকলে সরকার এই দাবিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল্যায়ন করতে পারবে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, জাতি নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল কাজ। কিন্তু যদি সরকার তফসিলি জাতির অন্তর্গত ১২৩৪টি জাতি ও তফসিলি উপজাতির ৬৯৮টি গোত্রকে চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে বাকি চার হাজার জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করাও অদৃশ্য নয়।
সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত
ভারতের সমাজে জাতি এখনো গভীরভাবে প্রোথিত। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশে মাত্র ৫ শতাংশ বিয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পন্ন হয়—যা প্রমাণ করে জাতি এখনো সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। নাম, পোশাক, প্রতীক, বাসস্থান—সবক্ষেত্রেই জাতিগত পরিচয়ের ছাপ বর্তমান। রাজনীতি, প্রশাসন, এমনকি মন্ত্রিসভা গঠনেও জাতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে, জাতিভিত্তিক জনগণনা সামাজিক ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণের এক অপরিহার্য শর্ত হয়ে উঠেছে।
বিগত কয়েক দশক ধরে সংরক্ষণের প্রশ্নটি বারবার আলোচনায় এসেছে, অথচ এর জন্য প্রয়োজনীয় জাতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান আজও অনুপস্থিত। সঠিক তথ্য ছাড়া সংরক্ষণ একটি অন্ধ বিতরণ ছাড়া কিছু নয়। “ক্রিমি লেয়ার” সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও জাতিগত তথ্য ছাড়া সম্ভব নয়। যেহেতু রাষ্ট্র জাতি-ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা দেয়, তাই জাতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান না থাকা ন্যায়বিচারহীন এক ধরনের অজ্ঞাত দানবৃত্তির সমান।
আগামী ২০২৭ সালের ভারতের জনগণনা ও জাতিভিত্তিক গণনার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট
ভারতের পরবর্তী জাতীয় জনগণনা ২০২৭ সালের ১ মার্চ থেকে শুরু হবে, যা দেশের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক নীতি এবং সামাজিক উন্নয়নের দিক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ বার বিশেষভাবে জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকায় দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। জাতিভিত্তিক জনগণনার সমর্থকরা মনে করেন, এটি পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা ও অবস্থার নির্ভুল তথ্য দেবে, যা তাদের জন্য ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। তবে বাস্তবতা হলো, এই জাতিভিত্তিক গণনা প্রায়ই রাজনৈতিক দলগুলোর ভোটব্যাংক রাজনীতিকে প্রজ্বলিত করে এবং জাতিগত বিভাজনকে গভীরতর করে তোলে। দীর্ঘমেয়াদে এটি সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করে এবং জাতিগত পরিচয়ের নাম করে জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। এভাবে জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ দেশের বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আসন্ন জনগণনার পরিকল্পনায় জাতিগত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি জাতীয় সংহতি, সামাজিক সাম্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।
জাতিভিত্তিক গণনা: সুবিধার লোভ নাকি সামাজিক শোষণের ফাঁদ?
২০২৭ সালের জনগণনায় জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ভারতের সমাজে বহুদিনের আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। যদিও জাতিগোষ্ঠীগুলোর সংখ্যা ও অবস্থা জানা উন্নয়নের জন্য জরুরি, তবু এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির প্রধান বাধা হিসেবেও কাজ করে আসছে। জাতিভিত্তিক গণনা দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সাময়িক সংরক্ষণ দেওয়া হলেও তাদের মূল আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নে তেমন কোন উন্নতি হয়নি। বরং এই তথ্যের মাধ্যমে অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলো জাতিগত পরিচয়ের নামে ভোটব্যাংক তৈরি করে সুবিধা অর্জনে ব্যস্ত থাকে, যা দীর্ঘমেয়াদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের শোষণ ও নির্ভরশীলতা বাড়ায়। আসন্ন জনগণনা হওয়ার কথা থাকলেও জাতভিত্তিক বিভাজনকে উৎসাহ না দিয়ে সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর নীতি প্রণয়নই হবে প্রকৃত সাফল্যের চাবিকাঠি।
উপসংহার
জাতিভিত্তিক জনগণনা নিছক একটি পরিসংখ্যানগত কর্মসূচি নয়; এটি ভারতের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের জন্য ন্যায়ের ভিত্তি গড়ার এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। জাতিভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে সেই বাস্তবতাকে দলিলবদ্ধ করা সম্ভব, যা বহুদিন ধরে অস্বীকার করা হয়েছে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থে চেপে রাখা হয়েছে। যদি সরকার সত্যিই সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আন্তরিক হয়, তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে তাদের যথার্থ পরিচয় নির্ধারণ। কারণ, পরিচয় ছাড়া উন্নয়ন কেবল একটি রাজনৈতিক স্লোগান। এই জনগণনা ভারতীয় সমাজকে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আত্মসচেতন করার একটি সাহসী প্রয়াস, যার মাধ্যমে একটি সুবিবেচিত, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব।