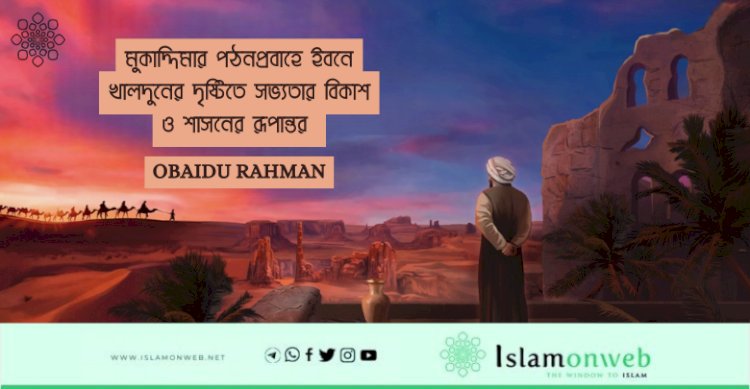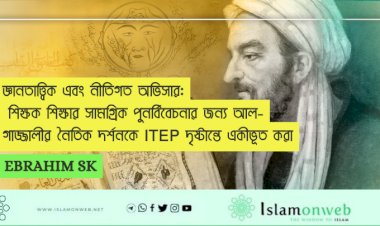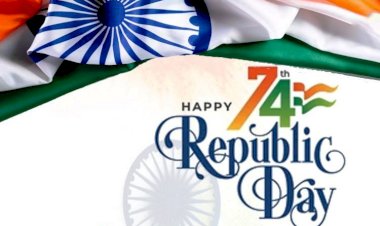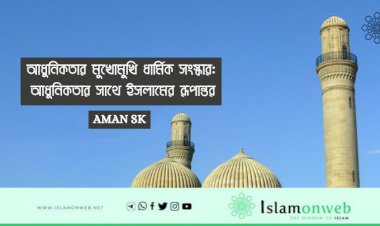মুকাদ্দিমার পঠনপ্রবাহে ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে সভ্যতার বিকাশ ও শাসনের রূপান্তর
ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রাচীন ধারার মধ্যে ইবন খালদুনের মুকাদ্দিমা হলো একটি গুরুত্ব পূর্ণ। ১৪শ শতকে রচিত হলেও এই গ্রন্থে ইবন খালদুন যেভাবে সমাজ, সভ্যতা ও রাষ্ট্রশক্তির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন, তা আজও একাডেমিক গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ক।
সভ্যতার ধারণা ও মানব সমাজের সূচনা
ইবনে খালদুন মানুষের সমাজবদ্ধ স্বভাবকে সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। মানুষের খাদ্য, নিরাপত্তা ও কাজের প্রয়োজন থেকে সহযোগিতা তৈরি হয়, যা একত্রবাস ও সামাজিক সংগঠনের জন্ম দেয়। এই প্রাকৃতিক প্রবণতা থেকেই গড়ে ওঠে পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্র। তার মতে, সভ্যতা কেবল প্রযুক্তির অগ্রগতি নয়, বরং সামাজিক সংহতি, শ্রম বিভাজন এবং নৈতিকতাভিত্তিক কাঠামোর একটি গতিশীল রূপ। ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমা-য় সভ্যতা (আল-উমরান) ধারণাটি একটি মৌলিক ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষ বাস্তবে সমাজবদ্ধ প্রাণী (madaniyyun bi'l-tabʿ) অর্থাৎ, একাকী বেঁচে থাকার সক্ষমতা মানুষের নেই। খাদ্য, নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং প্রজননের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা আবশ্যক। এই সহযোগিতার প্রক্রিয়াতেই গঠিত হয় পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্র।
ইবনে খালদুনের মতে, সভ্যতা কেবল নগরায়ণ বা নির্মাণকাজ নয়, বরং এটি মানুষের সামষ্টিক জীবনযাত্রার একটি সুসংগঠিত ও প্রক্রিয়াধর্মী রূপ। সভ্যতার বিকাশ ঘটে শ্রম বিভাজন, সামাজিক চুক্তি, নৈতিকতার বিকাশ এবং নেতৃত্ব কাঠামোর মধ্য দিয়ে। সভ্যতার এই বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে; এটি কেবল বাহ্যিক উন্নয়নের ফল নয়, বরং একটি অভ্যন্তরীণ সামাজিক চেতনায় রূপান্তর। তাঁর বিশ্লেষণে দেখা যায়, সভ্যতার বিকাশ একটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করে—যাযাবর সমাজ থেকে গ্রামীণ বসতি, এবং সেখান থেকে নগর সভ্যতা। প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি শাসন ও নৈতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক সমাজতত্ত্বের বিকাশেও প্রভাব ফেলেছে, বিশেষত এ.আর. র্যাডক্লিফ ব্রাউন বা ইমাইল দুর্খেইমের মতো চিন্তাবিদদের রচনায় এর ছায়া দেখা যায়। অতএব, সভ্যতার ধারণা ইবনে খালদুনের চিন্তায় একটি গঠনমূলক ও বহুমাত্রিক বাস্তবতা, যা মানুষের মৌলিক চাহিদা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে গড়ে ওঠে।
আসাবিয়্যা এবং সামাজিক সংহতি:
মুকাদ্দিমা-র একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল "আসাবিয়্যা" বা সামাজিক সংহতি। ইবনে খালদুন ব্যাখ্যা করেন যে কোনও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি মূলত তাদের অভ্যন্তরীণ সংহতির উপর নির্ভরশীল। যাযাবর ও বেদুঈন সমাজে এই সংহতি অত্যন্ত দৃঢ় থাকে, যা তাদের সংগ্রামী করে তোলে। এই সংহতি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে সভ্যতা যত উন্নত হয়, আসাবিয়্যা ততই দুর্বল হয় এবং এক সময় শাসনক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ইবন খালদুনের মুকাদ্দিমা-র অন্যতম মৌলিক ও প্রভাবশালী তত্ত্ব হলো আসাবিয়্যা (ʿasabiyyah) যা সামাজিক সংহতি, গোষ্ঠীগত আত্মীয়তা বা দলগত সংযুক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, কোনও সমাজ বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক প্রভাব মূলত এই আসাবিয়্যার শক্তির উপর নির্ভর করে।
আসাবিয়্যা মূলত গোষ্ঠীগত আত্মীয়তার অনুভূতি, যেখানে একে অপরের জন্য আত্মত্যাগ করার মানসিকতা থাকে। এটি বিশেষ করে বেদুঈন (যাযাবর) সমাজে দেখা যায়, যেখানে আত্মীয়তা, রক্তসম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত দৃঢ়। ইবনে খালদুন দেখান, এই সংহতি একজন নেতার চারপাশে একটি শক্তিশালী দল গঠন করে, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তবে সভ্যতা যত উন্নত হয়, বসবাস ধীরে ধীরে নগরভিত্তিক হয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রাধান্য পায়, তখন আসাবিয়্যার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ধনী ও ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সংহতি লুপ্ত হয়। ফলে, শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একসময় অন্য একটি শক্তিশালী, আসাবিয়্যা-সমৃদ্ধ গোষ্ঠী সেই শাসন ক্ষমতা দখল করে।
এই চক্রাকার প্রক্রিয়ায় ইবনে খালদুন সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্তর্নিহিত গতিশীলতা দেখিয়েছেন। আধুনিক সমাজতত্ত্বের ভাষায়, আসাবিয়্যা ধারণাটি সামাজিক পুঁজির (social capital) পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যেখানে গোষ্ঠীগত একতা একটি সংগঠনের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও প্রভাবের প্রধান নির্ধারক।
তাই ইবন খালদুনের দৃষ্টিতে, সভ্যতার বিকাশ এবং শাসনের রূপান্তর বুঝতে হলে আসাবিয়্যা ও তার ভূমিকা বোঝা অপরিহার্য।
শাসনের ধরণ ও রূপান্তর:
ইবন খালদুন মুকাদ্দিমা-তে শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও রূপান্তরকে একটি বাস্তবসম্মত ও পর্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, প্রতিটি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের একটি প্রাকৃতিক জীবনচক্র আছে, যা সাধারণত তিনটি ধাপে সংঘটিত হয়:
১. আদর্শিক শাসন (যেমন খিলাফত), যেখানে শাসন ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠতার উপর প্রতিষ্ঠিত।
এই পর্যায়ে শাসনব্যবস্থা ন্যায়, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা-নির্ভর হয়। শাসকগণ নিজেকে সেবক মনে করেন এবং জনগণের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। এই ধরনের শাসনপ্রথা বিশেষ করে নবুয়তের উত্তরসূরি হিসেবে প্রথম যুগের খিলাফতগুলোতে পরিলক্ষিত হয়।
২. রাজতান্ত্রিক শাসন (মুলুকিয়্যা)
যেখানে ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে চলে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ মুখ্য হয়ে ওঠে।
সময় গড়ালে ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হয় এবং শাসকগোষ্ঠী ধীরে ধীরে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। শাসনব্যবস্থা ধর্মীয় নীতিমালা থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজার খেয়াল ও সুবিধার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এখান থেকে শুরু হয় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বিকাশ।
৩. বিলাসিতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা
যেখানে শাসকশ্রেণি জনবিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে।এই পর্যায়ে শাসকশ্রেণি বিলাসবহুল জীবনযাপন, অপচয়, করের ভার, ও জনবিচ্ছিন্নতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। শাসকদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়, এবং শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। সামরিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো হ্রাস পায়, ফলে নতুন এক শক্তিশালী গোষ্ঠী আসাবিয়্যার জোরে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করে।
এই তিন পর্যায়েই তিনি দেখান, কীভাবে শাসকগোষ্ঠী প্রথমে সংগ্রামী ও নৈতিক থেকে পরবর্তীতে ভোগবাদী ও আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, নতুন একটি গোষ্ঠী উদয় হয় এবং পুরনো গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়। এই ধারাকে তিনি ইতিহাসের একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেন।
ইবন খালদুন এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি চক্রাকার ইতিহাসচক্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। শাসনের সূচনা সংগ্রাম ও ত্যাগে, মধ্যপর্যায়ে ক্ষমতার রক্ষণে, এবং শেষপর্যায়ে বিলাসিতা ও পতনে পরিণত হয়। এই বিশ্লেষণ আধুনিক পলিটিক্যাল সায়েন্স ও রাষ্ট্রচর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ হিসেবে বিবেচিত।
এছাড়া, তিনি প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যেও বিভিন্ন রূপান্তর দেখান—যেমন, দাসপ্রথা-নির্ভর আমলাতন্ত্র, শহরভিত্তিক করব্যবস্থা, এবং সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক পরিবর্তন ইত্যাদি। এসব উপাদান রাজনীতির বাস্তবতা ও প্রশাসনিক ধারার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
সভ্যতার চূড়ান্ত দশা ও পতনের কারণ:
সভ্যতা যখন বিলাসিতা, ফ্যান্সি পোশাক, ভদ্র জীবনযাপন এবং শ্রমবিমুখতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সেই সভ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ইবন খালদুন বলেন, এই চূড়ান্ত অবস্থায় শাসকেরা অত্যধিক কর আরোপ করে, জনগণ নিরুৎসাহিত হয় এবং সামষ্টিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়। ফলে সভ্যতার ভিত নড়ে যায় এবং নতুন শক্তির হাতে ক্ষমতা চলে যায়।
ইবন খালদুন মুকাদ্দিমা-তে সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি এর অবক্ষয় ও পতনের প্রক্রিয়াকেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, সভ্যতা একটি চক্রবদ্ধ গতিপথে বিকশিত হয় এবং একপর্যায়ে দুর্বল ও বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। এই চূড়ান্ত দশায় পতনের পেছনে তিনি কয়েকটি মৌলিক কারণ চিহ্নিত করেছেন:
১. বিলাসিতা ও ভোগবাদ
সভ্যতার বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে শাসক ও উচ্চবর্গ ভোগবিলাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পোশাক, খাদ্য, নির্মাণশৈলী ও বিনোদনে অপ্রয়োজনীয় অপচয় শুরু হয়। এই বিলাসিতাই ধীরে ধীরে কর্মনিষ্ঠার অবসান ঘটায় এবং সামাজিক উদ্যম কমিয়ে দেয়।
২. আসাবিয়্যার অবসান
প্রাথমিক পর্যায়ের দৃঢ় সামাজিক সংহতি (আসাবিয়্যা) বিলাসী জীবনে লুপ্ত হয়ে যায়। শাসক ও জনগণের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক দুর্বল হয় এবং গোষ্ঠীগত একতা হারিয়ে যায়। ফলে শাসনব্যবস্থা ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।
৩. করের ভার এবং উৎপাদনশীলতার পতন
রাজকোষ পূরণের জন্য শাসকগণ করের হার বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণ নিরুৎসাহিত হয়, এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়। কর্মসংস্থান হ্রাস পায় এবং সমাজে অসন্তোষ জন্ম নেয়।
৪. প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি
দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অযোগ্য আমলাতন্ত্রের প্রভাব প্রশাসনিক কাঠামোকে দুর্বল করে। দক্ষতা নয়, বরং আনুগত্য ও ঘুষের ভিত্তিতে পদায়ন হয়। এর ফলে জনগণের আস্থা হারিয়ে যায় এবং শাসনব্যবস্থা কার্যকারিতা হারায়।
৫. বহিরাগত আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ
একটি দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্র সহজেই বাইরের শক্তির কাছে পরাজিত হয় অথবা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের শিকার হয়। ইবন খালদুন দেখান, যখন শাসকগোষ্ঠী জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন একটি নতুন, আসাবিয়্যা-নির্ভর গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসে এবং নতুন চক্র শুরু হয়।
উপসংহার
ইবন খালদুনের দৃষ্টিতে সভ্যতা একটি প্রাণবন্ত সামাজিক সংগঠন, যার বিকাশ ও পতন মানুষের নৈতিকতা, সংহতি ও শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। মুকাদ্দিমা কেবল একটি ঐতিহাসিক বা দার্শনিক পাঠ নয়; এটি সমাজ-রাষ্ট্র বিশ্লেষণের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো। আধুনিক সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাতেও এই পাঠ অপরিহার্য প্রেক্ষাপট তৈরি করে। একাডেমিক বিশ্বে ইবন খালদুনের অবদান তাই আজও মূল্যবান ও সময়োচিত।
ইবন খালদুনের মুকাদ্দিমা শুধু মধ্যযুগীয় ইসলামী চিন্তার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত নয়, এটি সভ্যতা, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এক কালজয়ী গ্রন্থ। সভ্যতার উত্থান ও পতন, আসাবিয়্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, শাসনব্যবস্থার রূপান্তর, এবং ইতিহাসচক্রের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি একটি সামগ্রিক সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন।
এই চিন্তাভাবনাগুলি শুধু ইতিহাসের আলোকে সমাজ বিশ্লেষণই নয়, বরং সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রচর্চার জন্যও দিকনির্দেশক। আধুনিক বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বাস্তবতায়, ইবন খালদুনের তত্ত্ব আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক—বিশেষ করে রাষ্ট্রের ভিত কতটা সামাজিক সংহতির উপর নির্ভর করে, তা তাঁর লেখনী আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করায়।
অতএব, মুকাদ্দিমা কেবল অতীতের একটি দলিল নয়, বরং সভ্যতার ধারাবাহিকতার নিরীক্ষণে একটি তাত্ত্বিক আয়না, যা অতীত ও বর্তমান উভয়ের পাঠে সহায়ক। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর বিশ্লেষণ নতুন প্রজন্মের জন্য এক বিশাল বৌদ্ধিক ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
References
Ibn Khaldun. (1958). The Muqaddimah: An Introduction to History (F. Rosenthal, Trans.; N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press.
Alatas, S. H. (2006). Ibn Khaldun and Contemporary Sociology: A Study in Social Theory and History. International Islamic University Malaysia.
Issawi, C. (1950). Ibn Khaldun: An Arab Philosopher of History. Middle East Journal, 4(4), 418–426.
Mahdi, M. (1957). Ibn Khaldun and the Science of Human Society. Islamic Culture, 31(4), 345–360.
Rosenthal, F. (1942). Ibn Khaldun’s Concept of Economics. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 4(3), 268–293.