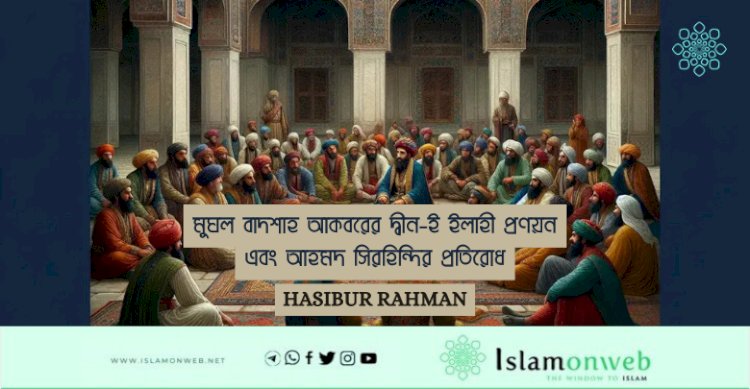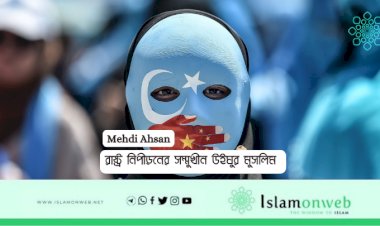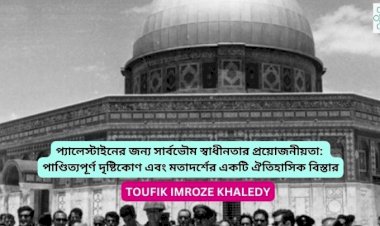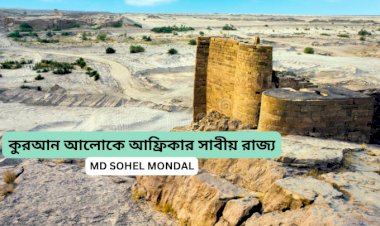মুঘল বাদশাহ আকবরের দ্বীন-ই ইলাহী প্রণয়ন এবং আহমদ সিরহিন্দির প্রতিরোধ
মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক শুরুর ইতিহাস ছিল রক্তপাত, ক্ষমতা দখল আর অভিজাত বংশের গৌরবগাথায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আকবরের শাসনকাল (১৫৫৬–১৬০৫) ছিল মুঘল ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রার সূচনা। সে সময় মুঘলরা একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শাসন করছিল, তেমনি নানা ধর্ম, ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে একই ছাতার নিচে রাখতে গিয়ে চরম নীতি-সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। আকবর এই সমস্যার সমাধানে কেবল প্রশাসনিক নয়, বরং ধর্মীয় কৌশল অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেন—একটি ‘নতুন আদর্শিক ধারা’ তৈরি করার মধ্য দিয়ে।
আকবর প্রাথমিকভাবে একজন সাধারণ মুসলিম হিসেবে জীবন শুরু করলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মীয় অনুশীলনে শিথিলতা আনেন। প্রথমে তিনি সুফিদের কাছাকাছি থাকলেও পরে বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিনিধিদের সাথে যুক্ত হয়ে এক বৈচিত্র্যময় চিন্তার দিকে ধাবিত হন। তিনি ১৫৭৫ সালে ফতেপুর সিক্রিতে প্রতিষ্ঠা করেন ‘ইবাদতখানা’—যেখানে বিভিন্ন ধর্মের বিদ্বানদের আমন্ত্রণ জানানো হতো বিতর্ক ও মতবিনিময়ের জন্য।
এই ইবাদতখানা থেকেই জন্ম নেয় ‘দীন-ই-ইলাহী’-র মতো বিতর্কিত ধারণা—যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্মের সারাংশ নিয়ে একটি রাজকেন্দ্রিক ধর্ম তৈরি করা। একদিকে এটিকে তিনি "সহনশীলতার প্রতীক" বলে দাবি করলেও, বাস্তবে এটি ছিল ইসলামের মৌলিক আক্বীদা—তাওহিদ, রিসালাত, ও আখিরাত—এই তিন ভিত্তিক স্তম্ভে সরাসরি আঘাত।
আকবর শুধু যে নিজের ধর্মীয় চিন্তায় পরিবর্তন আনেন, তা-ই নয়—তিনি ধীরে ধীরে কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর উলামাদের গুরুত্ব কমিয়ে দেন, ইসলামি শরিয়াহর জায়গায় রাজশক্তিকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব দিতে থাকেন এবং ইসলামী আইনকে বাদ দিয়ে নিজস্ব 'সাম্রাজ্যিক রীতিনীতি' প্রচলন করেন। এভাবে মুঘল দরবারে ‘দ্বীনের নামে দ্বীনবিরোধী’ এক নতুন ধারা প্রচারিত হতে থাকে, যেখানে ঈমানকে অবিশ্বাসে, আক্বীদাকে বিভ্রান্তিতে এবং তাওহিদকে সমন্বয়বাদে বিলীন করার চেষ্টা করা হয়। এই পটভূমিই তৈরি করে এক ভয়ঙ্কর ধর্মীয় ফিতনার, যার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিবাদও তখন রাজনৈতিক অপরাধে পরিণত হয়।
আকবরের দীন-ই-ইলাহী: সহনশীলতার বেশে এক নতুন ধর্ম
১৫৮২ সালে আকবর যে ধর্মটি প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম ছিল “দীন-ই-ইলাহী”—মানে ‘ঈশ্বরীয় ধর্ম’। কিন্তু প্রশ্ন হলো: এই ধর্ম আদৌ কি ‘ঈশ্বরীয়’ ছিল, না কি এটি ছিল একজন রাজার ব্যক্তিগত চিন্তা ও রাজনৈতিক কৌশলের কৃত্রিম মিলন?
আকবর এই ধর্মকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যেন সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো একত্রে এনে ‘একটি সার্বজনীন আদর্শ’ তৈরি করা যায়। এই ধর্মে কোনো নির্দিষ্ট ঈমান বা কালেমা ছিল না, বরং এতে স্থান পেয়েছিল হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্মবাদ, জৈন ধর্মের অহিংসা, খ্রিস্টানদের যিশুপ্রেম, এবং ইসলামের কিছু আংশিক উপাদান—তাও শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার খাতিরে। দীন-ই-ইলাহী ছিল মূলতঃ একটি রাজনৈতিক ধর্ম—যার উদ্দেশ্য ছিল রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্যকে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতায় রূপ দেওয়া। যারা এই ধর্ম গ্রহণ করত, তাদের ‘আকবরের একনিষ্ঠ অনুগামী’ হিসেবে শপথ করতে হতো। আকবর নিজেকে শুধু সম্রাটই নয়, বরং এক ধরনের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ও ‘ইলাহী’র প্রতিনিধি রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই ধর্মের অনুসারীরা প্রতিদিন আকবরের নামে দোয়া করত, তাকে ‘মহান আত্মা’ বা ‘ইনসানে কামেল’ হিসেবে অভিহিত করত।
এই ধর্মে নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদতের কোনো স্থান ছিল না। বরং এইসব ‘পুরাতন রীতিনীতি’ বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের বিধানকে তুলনামূলক করে দেখা হতো, এবং নবীজী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নেও অবমাননাকর ইঙ্গিত ছিল।
এইভাবে ‘সহনশীলতার বেশে দীন-ই-ইলাহী বাস্তবে হয়ে ওঠে— এক বিকৃত ধর্মীয় দর্শন, একধরনের আত্মমর্যাদা ভঙ্গকারী উপাসনা, এবং ইসলামের বিরুদ্ধে রাজকীয় ফিতনা।
মুঘল দরবারের বহু উঁচু পদস্থ ব্যক্তি, যেমন তানসেন, বীরবল, আবুল ফজল—এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হন। তারা একে জ্ঞান ও দার্শনিকতার প্রতীক হিসেবে প্রচার করে মুসলমানদের দ্বীনি আস্থায় ফাটল ধরায়। রাজা নিজে যখন ইসলামের ফরয ইবাদত ত্যাগ করেন, তখন গোটা সাম্রাজ্যে দ্বীনের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।
দীন-ই-ইলাহী শুধু একটি ভুল মতবাদ নয়—এটি ছিল আখিরি নবুওতের চ্যালেঞ্জে পরিণত হওয়া একটি ভয়ানক বিদআত। যার মধ্যে ছিল আত্মপূজা, রাজানুগত্যের ধর্মীয় মোড়ক, এবং তাওহিদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ।
এই সময় একজন আল্লাহভীরু আলেম রুখে দাঁড়ান, যিনি রাজা বা রাজসভার ভয় না পেয়ে দ্বীনের সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হননি। তিনি হলেন—ইমাম আহমদ ফারুকী সারহিন্দী (রহিমাহুল্লাহ)।
ইমাম আহমদ সারহিন্দী: একা এক বিপ্লব, কলমে এক যুদ্ধ
যখন সত্য চাপা পড়ে শক্তির নিচে, তখনই আল্লাহ তায়ালা কাউকে প্রেরণ করেন বাতিলের বুক চিরে হক প্রতিষ্ঠার জন্য। আকবরের “দীন-ই-ইলাহী” যখন ইসলামের মূল আকীদাকে বিকৃত করতে শুরু করে, তখন এক নির্ভীক মুজাহিদ কলম হাতে এগিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন—শাহ আহমদ ফারূকী সারহিন্দী (রহিমাহুল্লাহ), যিনি পরে খ্যাতি অর্জন করেন মুজাদ্দিদে আলফে সানি—দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক হিসেবে।
ইমাম সারহিন্দী ছিলেন না কোনো রাজদরবারের কবি বা পদ-লোভী উলামা। তিনি ছিলেন তাসাওফের উঁচু স্তরের সাধক, কুরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞানধারী, এবং সবচেয়ে বড় কথা—একজন নির্ভীক দাঈ, যিনি বাতিল মতবাদকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের মূলনীতি রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেন।
তিনি লিখিত ও মৌখিকভাবে দীন-ই-ইলাহীকে “ইসলামের ছদ্মবেশে এক ভয়ানক বিদআত” হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, “এটি এক ধরনের নতুন ধর্ম, যা মানুষকে আল্লাহর পথে নয়, বরং রাজার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করে।” তিনি নিজের চিঠিপত্রে (মাকতুবাত) এ ধর্মের ভিত্তি, উদ্দেশ্য ও ফলাফল—সবকিছু কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে খণ্ডন করেন।
তাঁর কলম ছিল ধারালো তরবারির চেয়েও বেশি প্রভাবশালী। তাঁর লেখনিতে ছিল এমন এক দীপ্তি, যা রাজদরবারের অলঙ্কারের ঝলকে ঢাকা পড়েনি; বরং যা সরাসরি মুসলিম হৃদয়ে আঘাত করেছিল। রাজা হোক বা দরবেশ—ইমাম সারহিন্দী কারও ভয় পাননি, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহস তাঁর ঈমান থেকেই উৎসারিত হয়েছিল।
তিনি একা ছিলেন, কিন্তু তাঁর কলমে ছিল হাজারো তাওহিদের তলোয়ার। তাঁর আন্দোলন ছিল নিঃশব্দ, কিন্তু প্রভাব ছিল ভূকম্পের মতো; যে আন্দোলনে কেঁপে উঠেছিল মুঘল সম্রাজ্যের আত্মীয়-স্বজন ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি।
রাজানুকূল ফিতনার বিরুদ্ধে এক আলেমের সংগ্রাম
আকবরের দীন-ই-ইলাহী যখন দিনকে দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল, রাজসভার বড় বড় ব্যক্তিরা যখন একে “বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি” বলে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, তখন ইমাম সারহিন্দী একা এই ফিতনার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এটি ছিল এক অসম যুদ্ধ—একদিকে বাদশাহর প্রভাব, অপরদিকে এক আলেমের তাওহিদী চেতনা। এই সংগ্রামে বাহুতে ছিল না তরবারি, ছিল না কোনো বাহিনী, কিন্তু ছিল এক অবিচল ঈমান আর সত্যের প্রতি অঙ্গীকার।
তিনি বিশ্বাস করতেন—“রাজানুগত্যের নামে যদি আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীনকে বদলানো হয়, তবে সেটি ইসলাম নয়, বরং এক ভয়ংকর বিভ্রান্তি।” দীন-ই-ইলাহীকে তিনি ফিতনা বলেই চিহ্নিত করেন, এবং বলেন—এই মতবাদ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, বিশেষত তাওহিদ, নবুওত, শারিয়াহ ও ফরয ইবাদতের প্রতি আনুগত্য।
ইমাম সারহিন্দীর এই বিপ্লব ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুরু, কিন্তু দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর চিঠিপত্র (মাকতুবাত) এতটাই যুক্তিসঙ্গত ও কুরআনসন্মত ছিল যে, বহু মানুষ আবার দ্বীনের প্রকৃত রূপ বুঝতে শুরু করে। তিনি উলামা সমাজকে আহ্বান জানান—তারা যেন বাতিলকে প্রশ্রয় না দিয়ে, দ্বীনের আসল মর্ম তুলে ধরেন।
তবে এই কাজ সহজ ছিল না। ইমাম সারহিন্দীকে কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী—কারাগারেও তিনি ছিলেন অটল। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি ছিল:
“আমি সম্রাটের বন্দি নই, আমি তো আল্লাহর পথে মুক্ত একজন সৈনিক।”
কারাগারে থেকেও তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ থামাননি। বরং সেখানেই জন্ম নেয় আরও গভীর ভাবনা, আরও সুসংহত লেখনী, যেগুলো পরবর্তীতে ইসলামি চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠে।
ইমাম সারহিন্দীর দৃষ্টিতে আকবর ও দীন-ই-ইলাহী
ইমাম আহমদ ফারূকী সারহিন্দী (রহ.) আকবরের দীন-ই-ইলাহীকে শুধুমাত্র একটি গোমরাহী নয়, বরং ইসলামের রুহানিয়াত ও আকীদার বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে মনে করতেন। তাঁর লেখনীতে বারবার উঠে এসেছে এই ধর্মের অন্তর্নিহিত বিপদ ও এর সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজির ভয়াবহতা।
তিনি বলেন—
“আল্লাহর দ্বীন এক ও অদ্বিতীয়। তাতে কোনো মিলন ঘটানো চলে না। যে ব্যক্তি সব ধর্ম মিলিয়ে নতুন ধর্ম তৈরি করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মেই বিশ্বাস রাখে না।”
(মাকতুবাত, খণ্ড ১)
আকবর যখন নিজেকে ইলাহী-র প্রতিনিধি দাবি করতেন এবং মানুষকে নিজের নামে দোয়া করতে বলতেন, তখন ইমাম সারহিন্দী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন—
“এই পথ নবুওতের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। এটি খাতামান নবিয়্যিন (সা.)-এর মর্যাদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।”
তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—আকবরের এই ধর্ম এমন একটি ফিতনা, যা শুধু ইসলামের বাহ্যিক রীতিনীতি নয়, বরং আন্তরিকতা, ঈমান, ও আখিরাতের নাজাতকেও হুমকির মুখে ফেলে দেয়।
ইমাম সারহিন্দী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন এই কারণে যে, আকবরের দরবারে যারা তাকে উৎসাহ দিচ্ছে—তারা ছিল শিক্ষিত, আলেম ও দার্শনিকের ছদ্মবেশে বিভ্রান্ত প্রচারক। তিনি এইসব দরবারি ‘আলেম’ ও ‘জ্ঞানপিপাসুদের’ ভণ্ডামি উন্মোচন করে বলেন—
“যারা দ্বীনকে রাজার রুচি অনুযায়ী বদলায়, তারা আলেম নয়, বরং ‘দুনিয়ার দাস’।”
এই চিন্তাধারাই পরবর্তীতে তাঁর বিখ্যাত উপাধি মুজাদ্দিদ আলফ সানি (দ্বিতীয় হিজরী সহস্রাব্দের সংস্কারক) প্রাপ্তির অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে।
আল্লাহর সাহায্যে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল যেভাবে
আল্লাহ তাঁর দ্বীনের হেফাজতের জন্য যুগে যুগে এমন মানুষ পাঠিয়েছেন, যারা বাতিলের প্রবল স্রোতের মধ্যেও সত্যের মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। ইমাম সারহিন্দী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন তেমনই একজন মুজাদ্দিদ, যিনি আকবরের রেখে যাওয়া বিভ্রান্তিকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবলে নয়, বরং আত্মিক সাধনা ও ইলমের জোরে রুখে দিয়েছিলেন।
আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর যখন সিংহাসনে বসেন, তখন ইমাম সারহিন্দী প্রথমদিকে তাঁর বিরাগভাজন হন। ইমামের সত্যভাষণ, বর্ণশাসনের সমালোচনা ও দ্বীন সংরক্ষণের আহ্বান অনেক সময় জাহাঙ্গীরের চোখে 'বিদ্রোহ' হিসেবে মনে হয়েছিল। ফলে তাঁকে দিল্লিতে ডেকে এনে একপর্যায়ে বন্দি করা হয় গ্বালিয়র দুর্গে।
কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—এই বন্দিত্বই পরিণত হয় আধ্যাত্মিক বিজয়ে। জাহাঙ্গীরের মন ধীরে ধীরে ইমামের প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরে ইমামকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁকে পুনরায় সম্মানিত করা হয়। তাঁর চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে সারা উপমহাদেশে। রাজদরবারের ভেতরে এবং বাইরে, এক নতুন দ্বীনি চেতনার ঢেউ তৈরি হয়।
এইভাবেই আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করেন—একজন আলেমের কারাগারের নিঃশব্দ ধ্যান, তাঁর চোখের পানিই পাল্টে দেয় রাজনীতির গতিপথ।
ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এই প্রতিরোধের তাৎপর্য
ইমাম সারহিন্দীর প্রতিরোধ কেবল একটি ইতিহাসের গল্প নয়, বরং এটি মুসলমানদের জন্য একটি চিরন্তন শিক্ষা। তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন—যখন দ্বীনের মূল আক্বীদা, তাওহিদ, ও নবুওতের পবিত্রতা হুমকির মুখে পড়ে, তখন চুপ করে থাকা হারাম হয়ে যায়।
তিনি রাজা-বাদশাহর ভয়ে সত্য বলা ছাড়েননি, বরং বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে—
"আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় যদি অন্তরে জেগে ওঠে, তবে দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা আর ভয়ঙ্কর থাকে না।"
তাঁর জিহাদ ছিল কলমের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, ও আত্মার বিশুদ্ধতার মাধ্যমে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন—ইসলামের আসল শক্তি কেবল তরোয়ালে নয়, বরং চিন্তার বিশুদ্ধতায়, অন্তরের খালিস নিয়তে।
তাঁর লিখিত রিসালাগুলোর মাধ্যমে যে ‘তাজদীদ’ বা সংস্কার আসে, তা পরবর্তী অনেক ইসলামি আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করে। মুসলমানদের আকীদা-চেতনা তাঁর মাধ্যমে পুনরায় জেগে ওঠে। তিনি একাই প্রমাণ করেছিলেন—'একজন খাঁটি মুমিনের চিন্তা’ হাজার রাজপুরুষের চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে।
ইতিহাস থেকে কী শিখব আমরা?
আকবরের দীন-ই-ইলাহী ছিল ‘সহনশীলতা’ ও ‘সমন্বয়’-এর নামে দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি ভেঙে ফেলার চেষ্টা। আজও আমরা দেখি, অনেকে 'উন্নত ইসলাম', 'গ্লোবাল ইসলাম', বা 'মডারেট ইসলাম' নাম দিয়ে ধর্মকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে চায়।
তাদের কথার ধরন আলাদা হলেও উদ্দেশ্য প্রায় এক—
ইসলামকে মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমা রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা।
ঈমানকে ব্যক্তি বিষয়ে সীমিত রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সরিয়ে ফেলা।
এই প্রেক্ষাপটে ইমাম সারহিন্দীর জীবন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—
“ইসলাম কখনো নিজের মৌলিকত্ব ছাড়ে না, বরং সত্যিকারের মুসলমান সেই, যে বাতিলের চাপেও দীনের মৌলিক আকীদাকে অটুট রাখে।”
আজ আমাদের দরকার এমন চিন্তাবিদ ও দাঈ, যারা সত্য কথা বলবে—প্রভাবশালী শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে, আত্মবিশ্বাসের সাথে। যাদের ঈমান হবে রাজদরবারের আশীর্বাদে নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
উপসংহার
ইতিহাসের প্রতিটি যুগে আল্লাহ একজন করে দাঁড় করিয়েছেন, যিনি বাতিলের অন্ধকারে দ্বীনের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ফারুকী সারহিন্দী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন এমন এক জ্যোতিষ্ক, যিনি রাজা আকবরের বানানো ধর্মীয় অন্ধকারের বিরুদ্ধে জ্বেলে দিয়েছিলেন ঈমানের বাতি।
তাঁর কলমের শক্তি, তাঁর রুহানিয়াতের গভীরতা, এবং তাঁর সত্য ভাষণের সাহস আজও আমাদের পথ দেখায়। আজকের যুবক, আলেম, দাঈ, লেখক—যার যার জায়গা থেকে যদি আমরা দ্বীনের মৌলিকতা রক্ষায় সচেষ্ট হই, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের মাধ্যমে দ্বীনকে আবার জীবিত করবেন।
শেষ করছি এক বিখ্যাত সুফি কবিতার চরণ দিয়ে, যা যেন ইমাম সারহিন্দীর জীবনের সারসংক্ষেপ:
“হক্ কা মসীর, বুলান্দ আওয়াজে কহ গয়া—
বাদশাহ কা দর নেহি, হক্ কা দার হ্যায়!”
(সত্যের পথিক উচ্চ কণ্ঠে বলেছে—এ দরবার কোনো রাজার নয়, এ তো আল্লাহর দরবার!)