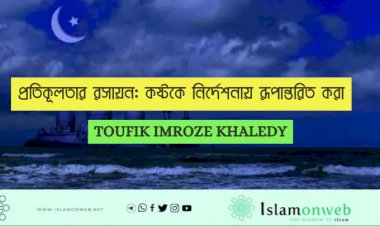অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে ইসলামি অর্থব্যবস্থা: যাকাত ও সাদাকার ভূমিকা
ভূমিকা: পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধির আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ
ইসলামি অর্থনীতির দর্শন নিছক সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব-নিকাশ কিংবা জাগতিক লেনদেনের শুষ্ক সমীকরণ নয়; বরং এটি একাধারে আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং সামাজিক সাম্যের এক অনবদ্য মহামিলন। এই দর্শনের প্রাণভোমরা হলো 'যাকাত' (الزكاة) ও 'সাদাকা'। আরবি ‘যাকাত’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি ও আধিক্য। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, সুনির্ধারিত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে, হিজরি বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে নির্দিষ্ট খাতে সম্পদের যে নির্ধারিত অংশ প্রদান করা হয়, তাকেই যাকাত বলা হয়। এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ, যা কালিমা ও সালাতের পরই মুমিনের জীবনে অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ বারবার এসেছে, যা এর গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا "তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু কল্যাণকর কাজ অগ্রে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন।" (সূরা আল-বাকারা: ১১০)
ইসলামি ফিকহ অনুযায়ী, একজন স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর কাছে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ—অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সমমূল্যের নগদ অর্থ বা ব্যবসায়িক পণ্য—এক বছরকাল গচ্ছিত থাকে, তবে তার ওপর যাকাত ফরজ হয়। এটি ধনীর সম্পদে দরিদ্রের করুণা নয়, বরং অবশ্যম্ভাবী অধিকার বা 'হক'। সম্পদের পুঞ্জীভূত পাহাড় যাতে সমাজের প্রবাহকে রুদ্ধ করতে না পারে, তার জন্যই এই স্বর্গীয় বিধান।
যাকাত: অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের এক মোক্ষম হাতিয়ার
মানবসভ্যতার ইতিহাসে অর্থনৈতিক বৈষম্য এক চিরস্থায়ী অভিশাপ। কিন্তু ইসলাম এই বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙে সাম্যের এক সুশীতল ছায়াতল নির্মাণ করতে চায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যেমন সাম্যের গানে মানবতার জয়গান গেয়েছেন, তেমনি ইসলামি অর্থনীতিও ধনের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ইনসাফ কায়েম করতে চায়। যাকাত হলো সেই চাবিকাঠি, যা ধনীর সিন্দুক থেকে সম্পদকে মুক্ত করে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে পৌঁছে দেয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যেখানে সম্পদ গুটিকতক ধনিক শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত থাকে, সেখানে ইসলাম সম্পদের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করে।
আল্লাহ তাআলা সূরা হাশরে এই অর্থনীতির মূলনীতি ঘোষণা করেছেন: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ "যাতে সম্পদ শুধুমাত্র তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা আল-হাশর: ৭)
যাকাত আদায়ের ফলে সম্পদ পবিত্র হয় এবং এতে বরকত বাড়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, দান করলে সম্পদ কমে যায়; কিন্তু গূঢ় অর্থে, এটি অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। যখন একজন বিত্তবান তার সম্পদের ২.৫ শতাংশ সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের হাতে তুলে দেন, তখন সেই অর্থ অলস পড়ে থাকে না। দরিদ্র মানুষ সেই অর্থ দিয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে—খাদ্য, বস্ত্র বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। ফলে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হয়, উৎপাদন বাড়ে এবং কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এটি অর্থনীতির ভাষায় 'গুণক প্রভাব' (Multiplier Effect) বা আয়ের আবর্তন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর সমাজচিন্তায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ের কথা বলেছেন, ইসলামি যাকাত ব্যবস্থা ঠিক তেমনিভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে।
ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান: সমস্যা ও স্বরূপ
বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান এক লজ্জাজনক অধ্যায় রচনা করেছে। আমাদের দেশেও এই চিত্র ভিন্ন নয়। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, দারিদ্র্য বিমোচন কেবল সরকার বা বিদেশী দাতা সংস্থার করুণার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের সমাজের অভ্যন্তরেই রয়েছে এই সমস্যার সমাধান। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার যাকাত আদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিপুল অর্থ যদি সুপরিকল্পিতভাবে আদায় ও বণ্টন করা হতো, তবে দারিদ্র্য জাদুঘরে স্থান পেত।
দুঃখজনকভাবে, আমাদের সমাজে যাকাত বিতরণের প্রচলিত পদ্ধতিটি অনেকটা লোকদেখানো ও অপরিকল্পিত। শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ কিংবা সামান্য কিছু টাকা ছিটিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ করার যে মানসিকতা, তা দরিদ্রকে স্বাবলম্বী করার পরিবর্তে তাকে পরনির্ভরশীলতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। এটি ইসলামের 'ইজ্জত' বা আত্মসম্মানবোধের পরিপন্থী। এর পরিবর্তে যদি নজরুল-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সেই অর্থ দিয়ে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তিকে রিকশা, ভ্যান, সেলাই মেশিন বা গবাদি পশু কিনে দিই, তবে সে ভিক্ষাবৃত্তির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটিই হলো 'শাশ্বত কল্যাণ' বা সাদাকায়ে জারিয়া।
দারিদ্র্য কেবল অর্থের অভাব নয়; এটি সুযোগের অভাবও বটে। সম্পদের অসম বণ্টনই এর মূল কারণ। ইসলামি অর্থনীতিতে যাকাত সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। বিভিন্ন দেশের সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৩-৪ শতাংশ) ধনীদের থেকে দরিদ্রদের দিকে ধাবিত হয়। এটি গিনি সহগ (Gini Coefficient) কমিয়ে সমাজে আয়ের সমতা আনতে সাহায্য করে।
সম্পদের অলস সঞ্চয় ও ইসলামের সতর্কবাণী
পুঁজিবাদ মানুষকে সম্পদ জমা করতে শেখায়, আর ইসলাম শেখায় সম্পদ ব্যয় ও বিনিয়োগ করতে। ইসলামে সম্পদকে অলসভাবে ফেলে রাখা বা 'কানয' হিসেবে জমা করে রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, অলস সম্পদ সমাজদেহে রক্ত জমাট বাঁধার মতো ক্ষতিকর।
আল্লাহ তাআলা কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পাজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। (বলা হবে), এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন আস্বাদন কর, যা তোমরা জমা করে রাখতে।" (সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪-৩৫)
এই আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয় যে, সম্পদ কুক্ষিগত করা কেবল অনৈতিকই নয়, বরং পরকালীন জীবনে ভয়াবহ শাস্তির কারণ। যাকাত ব্যবস্থা মানুষকে বাধ্য করে তার সম্পদকে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে। কারণ, সম্পদ ফেলে রাখলে যাকাত দিতে দিতে তা কমে যাবে; তাই বুদ্ধিমান মানুষ সেই সম্পদ ব্যবসায় খাটায়, যা জাতীয় উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এতিমদের সম্পদও ব্যবসায় বিনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে যাকাত দিতে গিয়ে মূলধন নিঃশেষ না হয়ে যায়।
বণ্টন ব্যবস্থা: যাকাত, সাদাকা ও ওয়াকফ
ইসলামি অর্থনীতি কেবল যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর পরিধি আরও বিস্তৃত। সাদাকা (ঐচ্ছিক দান) এবং ওয়াকফ (জনকল্যাণে স্থায়ী দান) এর অন্যতম অনুষঙ্গ। আধুনিক যুগে ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের সিএসআর (CSR) কার্যক্রম এবং যাকাত ফান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে যে ভূমিকা রাখছে, তা আশাব্যঞ্জক। 'সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট' (CZM)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যাকাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্পে ব্যয় করছে।
রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তার সাথে মিল রেখে বলা যায়, গ্রামের বিত্তবানরা যদি সম্মিলিতভাবে যাকাত ফান্ড গঠন করে স্থানীয় দরিদ্রদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন, তবে গ্রামবাংলার চেহারা পাল্টে যাবে। সরকারের রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি এই যাকাত ফান্ড হতে পারে 'সোশ্যাল সেফটি নেট' বা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সবচেয়ে বড় উৎস। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং জনসচেতনতা। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি অর্থনীতির পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় যাকাত আদায় ও বণ্টনকে স্বচ্ছ করা এখন সময়ের দাবি।
পুঁজিবাদ বনাম ইসলামি অর্থনীতি: এক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের স্বর্ণযুগে ইসলামি অর্থনীতি এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। তখন বাগদাদ, দামেস্ক বা কর্ডোভায় যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল আজকের আধুনিক অর্থনীতির আঁতুড়ঘর। চেক, প্রমিসরি নোট, লেজার, মুদারাবা (অংশীদারিত্ব), মুশারাকা—এসব আধুনিক ব্যাংকিং ধারণা মুসলিম বণিকদের হাত ধরেই ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সেই অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ইনসাফ ও নৈতিকতা, নিছক মুনাফাখোরী নয়।
অন্যদিকে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পুঁজিবাদ বা ক্যাপিটালিজম গড়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষ ও ভোগবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে। ফরাসি বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ইউরোপে যে 'মুক্তবুদ্ধি' বা সেক্যুলারিজমের জোয়ার আসে, তা অর্থনীতিকে নীতি-নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পুঁজিবাদের মূলমন্ত্র হলো—"অর্থনীতি প্রাকৃতিক নিয়মের মতো, এখানে আবেগের স্থান নেই।" তারা ডারউইনের 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' (Survival of the Fittest) তত্ত্বে বিশ্বাসী, অর্থাৎ যোগ্যরাই টিকে থাকবে, দুর্বলরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
কিন্তু ইসলাম বলে ভিন্ন কথা। ইসলামে অর্থনীতি হলো 'সারভাইভাল অফ দ্য উইকেস্ট'-এর রক্ষাকবচ। ইসলামি দর্শন মতে, সব সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ; মানুষ কেবল তার আমানতদার বা ট্রাস্টি।
পুঁজিবাদ বলে, "মানুষ কেবল স্বার্থপর প্রাণী (Economic Man), সে কেবল নিজের লাভ বোঝে।" আর ইসলাম বলে, "মানুষ খলিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি, সে অন্যের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে তুষ্টি খোঁজে।"
পুঁজিবাদ সুদভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত করে। সুদ হলো শোষণের হাতিয়ার, যা ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও নিঃস্ব করে। আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা আল-বাকারা: ২৭৫)
পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিশ্বজুড়ে আজ যে অসাম্য—যেখানে পৃথিবীর ৯০ শতাংশ সম্পদ মাত্র ১০০টি কর্পোরেশনের হাতে—তার মূল কারণ হলো এই সুদভিত্তিক অর্থনীতি। ড. উমর চাপড়ার মতো আধুনিক ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ যথার্থই বলেছেন যে, পুঁজিবাদের এই অমানবিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ফিরতে হবে মদিনার সেই সনাতন অথচ চির-আধুনিক অর্থনীতির দিকে, যেখানে নৈতিকতাই হলো ব্যবসার মূলধন।
উপসংহার: একটি আলোকিত আগামীর প্রত্যাশা
পরিশেষে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেখানে স্বার্থপরতা ও ভোগের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ইসলামি অর্থনীতি সেখানে ত্যাগ, সহানুভূতি ও ইনসাফের মিনার গড়ে তোলে। যাকাত ও সাদাকা কেবল কিছু টাকা হাতবদল করা নয়; এটি অন্তরের কার্পণ্য দূর করার এবং সমাজ থেকে বঞ্চনার বিষবাষ্প মুছে ফেলার এক ঐশী প্রক্রিয়া।
নজরুলের সেই বিদ্রোহী সত্তা যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, তেমনি আমাদেরও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে—তবে তা হতে হবে ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে। একটি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও মানবিক সমাজ গড়তে হলে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। যখন সমাজের প্রতিটি সাহেবে নিসাব ব্যক্তি তার সম্পদের হক আদায় করবে, যখন রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ইনসাফ কায়েম হবে, তখনই আমরা দেখব এক নতুন ভোর—যেখানে ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না থাকবে না, থাকবে না কোনো অধিকারবঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস। ইনশাআল্লাহ, সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, সঠিক পরিকল্পনা এবং মহান রবের বিধানের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আসুন, আমরা আমাদের সম্পদকে পবিত্র করি, সমাজকে সমৃদ্ধ করি এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের পথে ধাবিত হই।