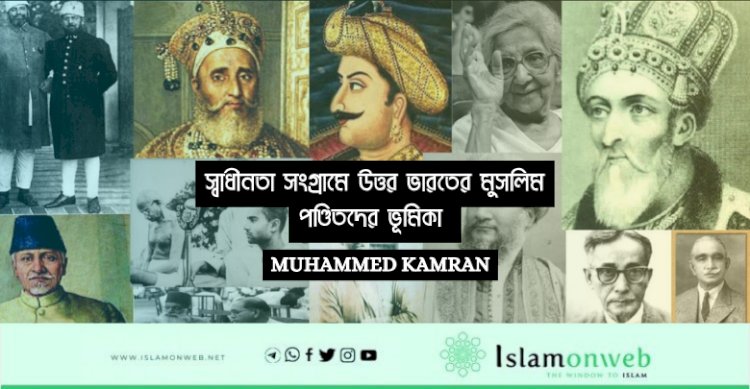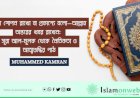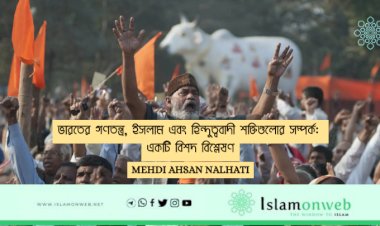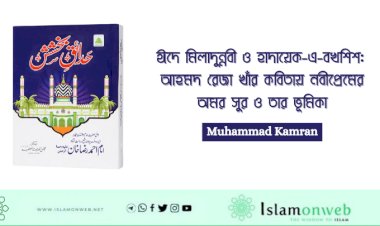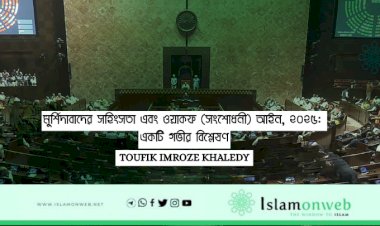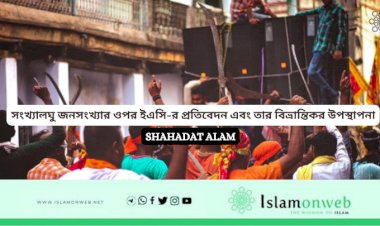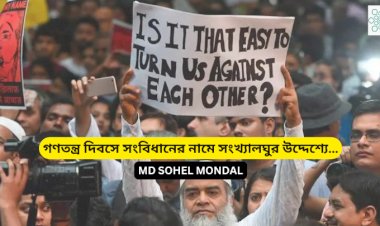স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তর ভারতের মুসলিম পণ্ডিতদের ভূমিকা
মুছে ফেলা এক ইতিহাস
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক মহাকাব্যিক ত্যাগ ও প্রতিরোধের ইতিহাস—কিন্তু এই ইতিহাসে মুসলিম আলেম ও চিন্তাবিদদের ভূমিকা বারবার উপেক্ষিত হয়েছে। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের যে আত্মত্যাগ ও আদর্শিক সংগ্রাম ছিল, তা ইতিহাসের মূলধারায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। বিশেষত সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এই অবদানগুলো আরও আড়ালে চলে গেছে। অথচ এই আলেম ও বুদ্ধিজীবীরা কেবল ধর্মীয় দায়বদ্ধতা থেকেই নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও স্বাধীন জাতির স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।
গান্ধী, নেহরু, বা প্যাটেলদের মতো নেতাদের অবদান যথার্থভাবেই স্মরণীয়। তবে মৌলানা ফজলে হক খইরাবাদি, শাহ আবদুল আজিজ, হজরত গাজী মিয়া, কিংবা দক্ষিণ ভারতের জয়নুদ্দীন মাখদুম আল-কাবিরদের নাম আজ ইতিহাসের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে—যাঁদের আত্মত্যাগ কোনো অংশে কম নয়।
এই প্রবন্ধে আমরা মূলত এমনই ২০ জনের বেশি মুসলিম আলেমের কথা বিশ্লেষণ করব—যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লব, আদর্শিক জাগরণ, সাহিত্যিক প্রতিরোধ ও শিক্ষার মাধ্যমে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তবে বিষয়বস্তুর বিস্তার ও বিশ্লেষণের স্বার্থে এই লেখাটি দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে আমরা উত্তর ভারতের আলেম ও চিন্তাবিদদের অবদান বিশ্লেষণ করব, এবং দ্বিতীয় পর্বে দক্ষিণ ভারতের আলেমদের বিল্পবী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। এভাবে আমরা ইতিহাসের সেই অন্তর্নিহিত ও উপেক্ষিত অধ্যায়গুলোকে সামনে আনতে সচেষ্ট হব—যা আজকের প্রজন্মের জানাও যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্মরণও অপরিহার্য।
১. শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (১৭৪৬–১৮২৪, দিল্লি)
শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভীর পুত্র শাহ আবদুল আজিজ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী ইসলামী ফকীহ ও আলেম। ১৮০৩ সালে, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লিসহ উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করে, তখন শাহ আবদুল আজিজ সাহসিকতার সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ফতোয়া জারি করেন। এই ফতোয়ায় তিনি ইংরেজ শাসনকে ‘দারুল হারব’ অর্থাৎ ইসলামী দৃষ্টিতে অবৈধ ও শত্রুর শাসন বলে ঘোষণা করেন। এটি নিছক ধর্মীয় আদেশ ছিল না; বরং মুসলিমদের রাজনৈতিক জাগরণের একটি বৈপ্লবিক ঘোষণাপত্রে পরিণত হয়।
তিনি দিল্লির বিখ্যাত মাদরাসা রাহিমিয়াতে শিক্ষা ও দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও শাহ ইসমাইল শহীদসহ বহু ছাত্র ও অনুসারী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন। শাহ আজিজের ফতোয়া শুধু ধর্মীয় আন্দোলনে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মত ঐতিহাসিক বিদ্রোহের বীজ রোপণ করেছিল। বৃটিশরা তাঁর কার্যকলাপের উপর কড়া নজরদারি ও দমননীতি চালালেও তাঁর আদর্শ মুসলিম সমাজে বরণীয় হয়ে ওঠে এবং বহু প্রজন্মের চিন্তা ও সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যায়।
২. মাওলানা ফজল-ই-হক খৈরাবাদী (১৭৯৭–১৮৬১, খৈরাবাদ, উত্তরপ্রদেশ)
উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে মাওলানা ফজল-ই-হক খৈরাবাদী ছিলেন একজন অনন্য দার্শনিক, কবি ও বিদ্বান আলেম। তাঁর জন্ম খৈরাবাদে হলেও তিনি শৈশব থেকেই আরবি-ফারসি সাহিত্যে অসাধারণ দখল দেখান। তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আরবি ও ফারসি ভাষার শিক্ষকতা করতেন, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত চেহারা বুঝতে পেরে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি মুসলিমদের পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের একটি ঐতিহাসিক ফতোয়া জারি করেন। এই ফতোয়া শুধু ধর্মীয় নয়, বরং রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুসলিম জনসাধারণকে জাগ্রত করে তোলে।
তিনি দিল্লি ও আওধ অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থানে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং বাহাদুর শাহ জাফরসহ বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শুধু আদর্শগত নেতৃত্ব নয়, তিনি অস্ত্র সংগঠন ও সামরিক কৌশল নির্ধারণেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ব্রিটিশরা ১৮৫৯ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ‘রাজদ্রোহী’ হিসেবে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে আন্দামান দ্বীপের সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠায়। সেখানে বন্দিজীবনে তিনি অসাধারণ ইসলামী কবিতা ও ধর্মীয় রচনা লিখে যান। অবশেষে ১৮৬১ সালে, সেই অমানবিক কারাগারেই তিনি ইন্তিকাল করেন।
তাঁর বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও জ্ঞাননির্ভর সংগ্রাম ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তির আন্দোলনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তাঁর মৃত্যু শুধু একজন আলেমের মৃত্যু নয়, বরং এক আদর্শিক বিপ্লবীর বিসর্জন।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও শওকত আলী:
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জোহর (১৮৭৮–১৯৩১) ও তাঁর বড় ভাই মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩–১৯৩৮) যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা উভয়েই খিলাফত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন এবং ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক। মুহাম্মদ আলী একজন প্রতিভাধর সাংবাদিক ও বাগ্মী, যিনি The Comrade ও Hamdard পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণকে উপনিবেশবিরোধী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সাহসিকতার সঙ্গে ঘোষণা দেন: “I will not return to a slave country,” এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন; পরে তাঁকে জেরুজালেমে দাফন করা হয়।
অন্যদিকে, শওকত আলী অল ইন্ডিয়া খিলাফত কমিটির সভাপতি হিসেবে সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন এবং গ্রামীণ মুসলিম সমাজকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহ দেন। দুই ভাই মিলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিমদের বিপুলভাবে সম্পৃক্ত করেন, যার ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যেরও অনন্য এক দৃষ্টান্ত গড়ে ওঠে। তাঁদের সংগ্রাম শুধু ধর্মীয় অধিকার রক্ষার নয়, বরং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যেও নিবেদিত ছিল।
৪. মাওলানা কাসিম নানুতভি (১৮৩২–১৮৮০, সাহারানপুর, উত্তরপ্রদেশ)
১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ইসলামী জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের এক নব দিগন্ত উন্মোচন করেন মাওলানা কাসিম নানুতভি। ১৮৩২ সালে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী কেবল একজন ফকীহ ও মুফাক্কিরই নন, বরং ১৮৫৭ সালে শামলি যুদ্ধের একজন সক্রিয় সৈনিকও ছিলেন। সামরিকভাবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও, নানুতভি উপলব্ধি করেছিলেন—ইসলামী পরিচয় টিকিয়ে রাখতে হলে চাই দীর্ঘমেয়াদি জ্ঞানভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিরোধ।
এই উপলব্ধি থেকেই ১৮৬৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ—একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে বিকশিত হয়। দেওবন্দ কেবল একটি মাদ্রাসা নয়, বরং একটি স্বাধীন ও আত্মনির্ভর মুসলিম সমাজ গঠনের স্বপ্ন ছিল যার ভিতে। এখানে শিক্ষার্থীদের ইসলামি চিন্তা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় রক্ষার মাধ্যমে উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সচেতন করা হতো।
মাওলানার এই শিক্ষা-ভিত্তিক প্রতিরোধ আন্দোলন পরে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর আত্মনির্ভর চিন্তা, আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ এবং দারুল উলূমের মাধ্যমে গড়ে ওঠা আলিমরা ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ইসলামী শিক্ষা ও জিহাদে আখলাকি চেতনার সমন্বয়ে নানুতভি ছিলেন এক ঐতিহাসিক রূপান্তরের পুরোধা।
৫. স্যার সায়্যিদ আহমদ খান (১৮১৭–১৮৯৮, দিল্লি/আলিগড়, উত্তরপ্রদেশ)
শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক হিসেবে পরিচিত হলেও, স্যার সায়্যিদ আহমদ খানের দৃষ্টিভঙ্গিমূলক অবদান ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বুনিয়াদ তৈরি করে দেয়। ১৮১৭ সালে দিল্লিতে জন্মগ্রহণকারী তিনি ব্রিটিশ প্রশাসনে বিচারক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের ওপর চালানো ব্রিটিশ নৃশংসতা তাঁর চেতনায় গভীর আঘাত হানে।
এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন, ভবিষ্যতের প্রতিরোধ কেবল অস্ত্রের মাধ্যমে নয়—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চিন্তার জাগরণেই নিহিত। ১৮৭৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মহম্মদান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ, যা পরবর্তীতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তে রূপান্তরিত হয়। তিনি মুসলিমদের আধুনিক বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করলেও, ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রাখার উপরও জোর দেন।
স্যার সায়্যিদের ধারণা ছিল, ব্রিটিশদের সঙ্গে আপাত শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে মুসলমানদের সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান মজবুত করা গেলে ভবিষ্যতে একটি চিন্তাশীল ও আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠবে, যারা উপনিবেশবাদী শাসনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। তাঁর নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষিত, সংস্কারমুখী সমাজ তৈরি করে, তা পরবর্তীতে রাজনৈতিক দাবি ও আত্মনির্ভরতার ধারায় রূপ নেয়।
সার সায়্যিদের এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রথাগত সংজ্ঞা ছাড়িয়ে, মুসলিম সমাজের একটি দীর্ঘমেয়াদি বৌদ্ধিক ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তী খেলাফত আন্দোলন ও মুসলিম লিগ গঠনের পথ প্রশস্ত করে।
৬. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮–১৯৫৮, মক্কা–কলকাতা)
মক্কায় জন্মগ্রহণ করলেও কলকাতার পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন উপনিবেশিক ভারতের অন্যতম প্রতিভাবান চিন্তাবিদ, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং কুরআনিক জ্ঞান, তাফসির ও ফিকহে গভীর দখল রাখতেন। তাঁর বৌদ্ধিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে তাঁর সম্পাদিত উর্দু সাময়িকী 'আল-হিলাল' ও 'আল-বালাগ'-এ, যেগুলো ব্রিটিশবিরোধী মতাদর্শ, মুসলিম জাগরণ এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
তিনি খেলাফত আন্দোলনে (১৯১৯–১৯২৪) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, যা ছিল উসমানি খেলাফত রক্ষার পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী প্ল্যাটফর্ম। আজাদ পরবর্তীতে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ‘পূর্ণ স্বরাজ’-এর জোরালো সমর্থক হয়ে ওঠেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে, ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতি নির্বাচিত হন।
মাওলানা আজাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসাম্প্রদায়িক ও বহুত্ববাদী ভারতের পক্ষে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমেই ভারত তার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারবে। স্বাধীনতার পর তিনি ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।
তাঁর গভীর ইসলামী জ্ঞান এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁকে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম করে তোলে। আজাদ ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের ময়দানে ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারকে নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করেছিলেন, যা তাঁকে মুসলিম সমাজে যেমন, তেমনি বৃহত্তর ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।
৭. খান আবদুল গফফার খান (১৮৯০–১৯৮৮, উৎমনজাই, – বর্তমানে পাকিস্তান)
“সীমান্ত গান্ধী” নামে পরিচিত খান আবদুল গফফার খান ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ও অহিংস প্রতিরোধের প্রবক্তা। ১৮৯০ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উৎমনজাই (বর্তমানে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখওয়া) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৯ সালে খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরের সেবক) নামে একটি শান্তিপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন গঠন করেন, যা ছিল পাঠান মুসলিমদের একটি অহিংস প্রতিরোধ বাহিনী, যারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও নাগরিক অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করতেন।
গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সহচর গফফার খান বিশ্বাস করতেন, ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই শান্তি, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতার ধর্ম। তাঁর কর্মকাণ্ড সেই ঔপনিবেশিক প্রচারণাকে চ্যালেঞ্জ করে, যা মুসলিমদের সহিংসতার সাথে যুক্ত করে উপস্থাপন করত। তাঁর নেতৃত্বে লক্ষাধিক পশতুন জনগণ অহিংস প্রতিরোধের পথে হেঁটেছিল, যদিও তারা ব্রিটিশ বাহিনীর নির্মম দমন-পীড়নের শিকার হয়।
তিনি ভারতের বিভাজনের দৃঢ় বিরোধিতা করেন, এবং আগেই সতর্ক করেছিলেন যে বিভাজন রক্তপাত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম দেবে—যা শেষ পর্যন্ত বাস্তবেই ঘটে যায়। দেশভাগের পর পাকিস্তানে তাঁকে অবহেলা ও নিগ্রহের মুখে পড়তে হয়; তবুও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে আছে—যে ইসলাম এবং অহিংসার মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং একটি ইসলামী নৈতিকতার ভিত থেকেই একটি ন্যায়ভিত্তিক অহিংস রাজনীতি গড়ে উঠতে পারে।
৮. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬, চুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ)
“বিদ্রোহী কবি” নামে পরিচিত কাজী নজরুল ইসলাম কেবল একজন কবিই ছিলেন না, বরং এক বলিষ্ঠ বিপ্লবী চেতনার অধিকারী ছিলেন, যিনি কলমের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক অবিচারের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়ায় জন্ম নেওয়া নজরুল দারিদ্র্যে বেড়ে উঠলেও অল্প বয়সেই বাংলা ও উর্দু সাহিত্যে অসাধারণ প্রতিভা দেখাতে শুরু করেন।
তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’ ও পত্রিকা ‘ধূমকেতু’-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯২৩ সালে তাঁকে “রাষ্ট্রদ্রোহিতার” অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়, যেখানে তিনি বন্দী অবস্থাতেই ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’-সহ অনেক আগুনঝরা রচনা লেখেন। তাঁর লেখা স্বাধীনতা, সাম্য, মানবিকতা এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণীতে মুখর ছিল।
নজরুলের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তাঁর কবিতার আবেগ-ভাষা যা সাধারণ জনগণের অন্তরে আগুন জ্বালাত। তিনি ইসলামি আধ্যাত্মিকতা এবং বিপ্লবী চেতনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন এক সাহিত্যিক ভাষা গড়ে তোলেন, যা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার লড়াইয়ে।
আজ তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত হলেও, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার যথোচিত স্মরণও প্রয়োজনীয়।
উপসংহার: ইতিহাসের ন্যায় প্রতিষ্ঠা
দিল্লি থেকে দেওবন্দ, বঙ্গ থেকে লাকনাউ—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম আলেমদের ভূমিকা কোনোভাবেই গৌণ ছিল না; বরং তা ছিল একেবারে ভিত্তিভূমি। এঁরা শুধু মসজিদের মিম্বরেই ভাষণ দেননি, কিংবা নির্জনে কলম চালিয়েই থেমে থাকেননি—তাঁরা সংগ্রাম করেছেন, সংগঠন গড়ে তুলেছেন, প্রতিরোধ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রেরণা যুগিয়েছেন।
এই আলেমদের অবদান আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বহুধর্মীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রের প্রমাণ বহন করে—যা আজকের বিভাজনমূলক সাম্প্রদায়িক বর্ণনায় প্রায়শই বিলুপ্ত হতে বসেছে।
এই কণ্ঠস্বরগুলিকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা কিংবা তাদের অবদানকে ক্ষুদ্র করে দেখা শুধু একাডেমিক অবিচার নয়—এটি ভারতের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে বিকৃত করার শামিল। যখন রাজনৈতিক পরিচয়ের নামে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে, তখন এই আলেমদের স্মরণ করা নিজেই একপ্রকার প্রতিরোধ। তাঁদের সাহস, প্রজ্ঞা ও আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়—ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটি সম্মিলিত স্বপ্ন ছিল, এবং তা ভবিষ্যতেও সকলের জন্য অভিন্ন ও অংশীদারিত্বমূলক হওয়া উচিত।
এই পর্বে আমরা মূলত উত্তর ভারতের মুসলিম আলেমদের অবদান নিয়ে আলোচনা করেছি তাঁদের অবদান ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছিল ঐতিহাসিকভাবে গভীর প্রভাবশালী। পরবর্তী পর্বে আমরা আলোচনা করব দক্ষিণ ভারতের মুসলিম আলেমদের সম্পর্কে—বিশেষ করে মালাবার, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং কর্নাটকের মুসলিম আলেমদের, যাঁরা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উপনিবেশবিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।