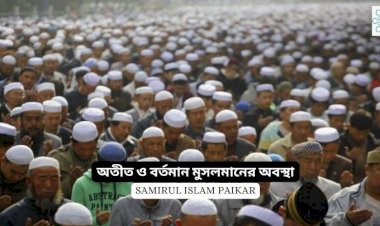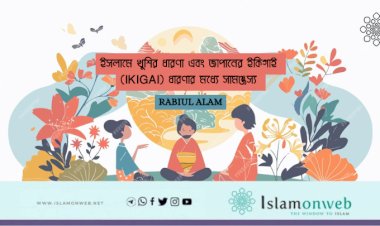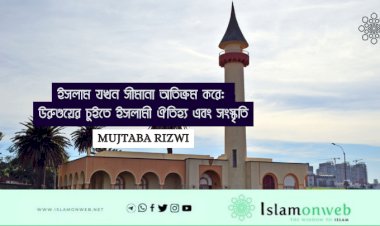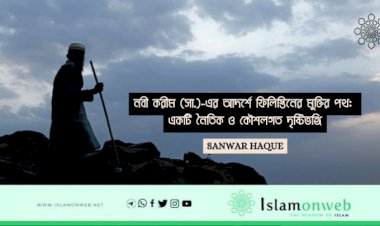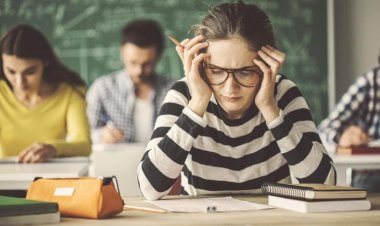ধর্ম ও শহীদদের টেনে রাজনীতি: একটি সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এক গভীর আবেগ, ইতিহাস ও আত্মত্যাগের সঙ্গে জড়িত। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদরা আমাদের জাতীয় পরিচয়ের গৌরবময় অধ্যায়, আর ধর্ম হলো এই জাতির মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। কিন্তু আজকের রাজনৈতিক বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই দুই মহান অনুভূতি—ধর্ম ও শহীদদের আত্মত্যাগ—কে ক্ষমতা ও প্রভাবের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সাম্প্রতিক বক্তব্যে উঠে এসেছে তীব্র অভিযোগ—“ধর্ম ও শহীদদের রক্তকে রাজনীতির পণ্য বানানো হচ্ছে”। এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব এই অভিযোগের প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ও এর ভয়াবহ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব।
শহীদের স্মৃতি ও ধর্মীয় আবেগ: রাজনৈতিক ব্যবহারের অস্ত্র?
মুক্তিযুদ্ধের শহীদগণের আত্মত্যাগ জাতির আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু যখন কোনো রাজনৈতিক দল তাদের আত্মত্যাগকে নিজের দলীয় প্রচারণার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তখন তা শুধু ইতিহাস বিকৃতি নয়—একটি জাতির বিবেকের অবমাননা। শহীদদের নাম ও রক্তকে ভোটের জন্য পুঁজি করবার প্রবণতা এক গভীর রাজনৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি। একইভাবে, ধর্ম—যা হৃদয়ের আলো ও অন্তরের সাধনা—তাকে যদি রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো হয়, তবে তা সমাজে বিভাজন ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আজকাল রাজনৈতিক মঞ্চে, বিশেষত নির্বাচনের প্রাক্কালে ধর্মীয় আয়োজনে অংশগ্রহণ কিংবা শহীদ স্মরণে কৃত্রিম অশ্রু বিসর্জন প্রকৃতপক্ষে এক প্রহসনের জন্ম দেয়।
রিজভীর অভিযোগের বিশ্লেষণ
রুহুল কবির রিজভীর এই সতর্কবার্তা আসলে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার এক জটিল নির্মিতিকে উন্মোচিত করে। তিনি যে “ধর্ম ও শহীদের আবেগকে ব্যবহার”‑এর কথা বলছেন, তা মূলত ভোটব্যাংক ঘিরে আবেগরাজনীতির একটি সূক্ষ্ম কৌশল—যেখানে ধর্মীয় অনুভূতি, স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরত্বগাথা ও শহীদ স্মৃতির প্রতি সম্মানকে হাতিয়ার বানিয়ে এক ধরনের নৈতিক অনাক্রম্যতা গড়ে তোলা হয়। এই অনাক্রম্যতার আড়ালে সরকার‑ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা নির্বাচনী সময়সূচি নির্ধারণ থেকে শুরু করে দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়া পর্যন্ত এমনভাবে প্রভাবিত করেন, যাতে বিরোধী কণ্ঠ ও বহুমাত্রিক ধারণাগুলি প্রান্তে ঠেলায় পড়ে। রিজভী যে “সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা”র কথা উল্লেখ করেন, তা আসলে একদলীয় আধিপত্য নিশ্চিত করার নীলনকশা, যেখানে নির্বাচনকে একটি আনুষ্ঠানিকতা বানিয়ে দেওয়া হয়—গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সৎ উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ করে রমজান মাসে নির্বাচন আয়োজনের অভিযোগটি গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এই পবিত্র মাসে সাধারণ মানুষের ধর্মাচার, কাজের চাপ ও জীবনধারায় স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন আসে, যা ভোটার উপস্থিতি ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে এমন সিদ্ধান্তকে ধর্মীয় পর্যবেক্ষণকে উপেক্ষা করে জন-অধিকারকে খর্ব করার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখছেন তিনি। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে, রিজভীর বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়—যদি নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক স্বাধীনতা হারিয়ে রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের ছায়ায় পরিচালিত হয়, তবে নির্বাচন আর গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকে না; তা পরিণত হয় ক্ষমতাসীনদের বৈধতা পুনর্নির্মাণের যন্ত্রে। সুতরাং এই বক্তব্য শুধুই সরকারের সমালোচনা নয়, বরং নাগরিক সমাজের জন্য এক সতর্ক সংকেত—গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে আবেগ ও ধর্মীয় পুঁজি যারা রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন, তাঁদের সজাগ নজরদারি ও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।
ধর্ম ও রাজনীতি: বিভাজনের রূঢ় বাস্তবতা
ধর্ম, মানবজাতির নৈতিক জাগরণ ও আত্মিক মুক্তির অন্যতম পথ, বর্তমানে বহু সমাজে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির এক ভয়ঙ্কর অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও এই বাস্তবতা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধর্মকে শান্তি, সহমর্মিতা ও মানবতার উৎস হিসেবে দেখার বদলে একদল রাজনৈতিক গোষ্ঠী এটি ব্যবহার করছে জনমানসে বিভক্তি তৈরি ও প্রতিপক্ষকে অপমানিত করার কৌশল হিসেবে। যখন কেউ নিজেকে “ধর্মরক্ষক” বলে প্রচার করে, তখন তার বিরোধী পক্ষ সহজেই “ধর্মবিরোধী”, “নাস্তিক” বা “বিশ্বাসচ্যুত” হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অমানবিক ও শত্রুতাপূর্ণ করে না, বরং ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই বিকৃত করে দেয়।
ধর্মীয় মেরুকরণের এই রাজনীতি শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে না; এটি দীর্ঘমেয়াদে সমাজের অভ্যন্তরে এক অবিশ্বাস ও ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, যেখানে ভিন্নমত মানেই ধর্মদ্রোহিতা। এর ফলে মুক্তচিন্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের সংস্কৃতি চরমভাবে বিপন্ন হয়। বিশেষ করে যখন শহীদদের নাম, স্মৃতি এবং তাঁদের আত্মত্যাগকে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার করা হয় কৌশলগত ‘সেন্টিমেন্টাল টুল’ হিসেবে, তখন তা শুধু শহীদদের প্রতি অবমাননাকর হয় না, বরং তা ইতিহাসকে ব্যবহার করে বর্তমানকে মিথ্যাচারপূর্ণ ও সুবিধাবাদী পথে পরিচালিত করে।
এই ধরনের কৌশল দেশের ঐক্য, সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রীয় ন্যায্যতার ভিত্তিকে দুর্বল করে। শহীদদের আত্মত্যাগ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সম্পদ নয়—এটি পুরো জাতির সম্মিলিত স্মৃতি ও অহংকার। তাই তাঁদের স্মৃতিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের চেষ্টা শহীদ পরিবারের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা এবং দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে একটি সংকীর্ণ, দলীয় রূপে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা।
সার্বিকভাবে, এই বাস্তবতা আমাদের সামনে এক গভীর প্রশ্ন তুলে ধরে—ধর্ম ও ইতিহাস কি শুধুই রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার সামগ্রী হয়ে থাকবে? নাকি এগুলিকে সত্যিকার অর্থে জাতির মূল্যবোধ ও ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে পুনঃস্থাপন করা যাবে? নাগরিকদের উচিত এসব বিষয় নিয়ে সচেতন থাকা, প্রশ্ন তোলা এবং এমন রাজনীতি থেকে দূরে থাকা যা ধর্ম ও শহীদের আত্মত্যাগকে কেবল মঞ্চসজ্জার উপাদানে পরিণত করে। সমাজে শান্তি ও সহাবস্থানের স্বার্থে ধর্মকে রাজনীতির হাত থেকে মুক্ত রাখা এখন সময়ের দাবি।
জাতি হিসেবে আমাদের করণীয়
ধর্ম ও শহীদ স্মৃতি কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়—এগুলো জাতির। তাই এদের ব্যবহারে চাই মর্যাদা, সংবেদনশীলতা ও সততা। নির্বাচন হতে হবে সময়োপযোগী, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক। নির্বাচন কমিশনকে হতে হবে নিরপেক্ষ ও জনঅংশগ্রহণে সচেষ্ট। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত ধর্ম ও শহীদদের নাম ব্যবহারে সংযত হওয়া এবং জনগণের প্রকৃত সমস্যা—দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্নীতি—এই বিষয়ের সমাধানে মনোযোগী হওয়া। তবেই গঠিত হবে একটি সুশাসিত, ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
উপসংহার
রুহুল কবির রিজভীর বক্তব্য আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার দর্পণ। যদি একটি জাতি তার শহীদদের রক্ত ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, তবে সেই জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আবেগ দিয়ে সাময়িক জয় সম্ভব হলেও, জনগণের আস্থা অর্জনের একমাত্র পথ হলো সেবা, সততা ও ন্যায়ের রাজনীতি। তাই আজ সময় এসেছে রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মসমালোচনার—শহীদের রক্ত আর ধর্মের মহিমাকে ভোটের সমীকরণ থেকে মুক্ত করার। যদি আমরা সত্যিই শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তবে তা হবে একটি মর্যাদাপূর্ণ, সচেতন, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের মাধ্যমে।