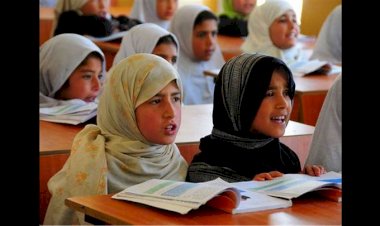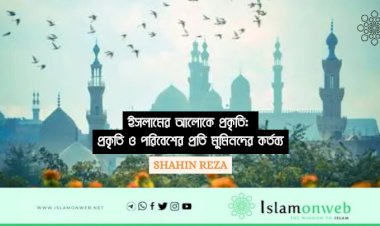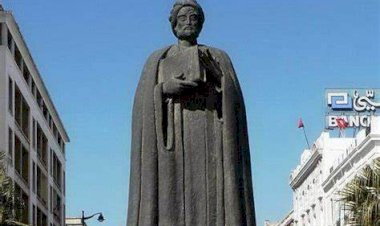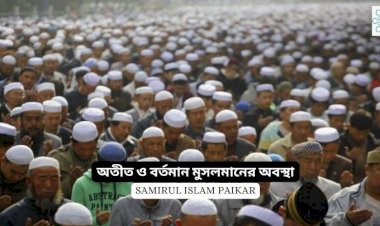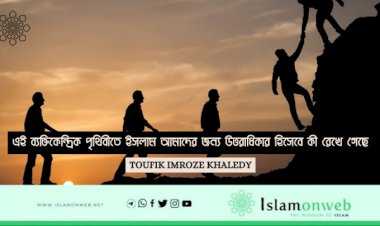জেন-জীতরুণদের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট এবং আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন
-রাশিদ পি. উস্তাদ
ক্রমবর্ধমান সুবিধা, পছন্দ এবং সংযোগের এই জগতে, প্রশ্ন জাগে - কেন আমাদের মধ্যে এত তরুণ এবং বৃদ্ধ, জীবনের অর্থ বোঝার জন্য নীরবে সংগ্রাম করছেন? এটা কি সম্ভব যে আরামের প্রাচুর্য পরিপূর্ণতার দিকে নয়, বরং এক অদ্ভুত ধরণের শূন্যতার দিকে নিয়ে গেছে? প্রশংসিত মালায়ালাম সঙ্গীতশিল্পী এবং প্রযোজক রফিক আহমেদ উম্বাচির সাম্প্রতিক একটি ফেসবুক পোস্ট এই নীরব যন্ত্রণার কণ্ঠস্বর। বুদ্ধি, আবেগ এবং দুর্বলতার সমান অংশ নিয়ে, উম্বাচি তার মেয়ে অ্যামির সাথে একটি সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন, যার শিশুসুলভ অভিযোগ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিফলনের দ্বার খুলে দেয়। একটি হাস্যকর পারিবারিক সংলাপ আধুনিক অবস্থার উপর একটি মর্মস্পর্শী ধ্যানে রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে যা শুরু হয়: সুখ এবং উত্তেজনার মধ্যে পার্থক্য, এবং কীভাবে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ই ভিন্ন কিন্তু অদ্ভুতভাবে একই উপায়ে অর্থের সাথে লড়াই করে।
অ্যামির নির্দোষ অভিযোগ: সংকটের সূচনা
গল্পটি শুরু হয় একটি সাধারণ বিকেলে। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী অ্যামি তার ভাইদের সাথে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে। তার মুখে এক অস্বাভাবিক গম্ভীরতা ফুটে ওঠে। সে ঘোষণা করে, "আমার কিছু নিয়ে আলোচনা করা দরকার।" তিন ভাইবোন, যারা সাধারণত ইংরেজিতে কথা বলে, তারা কথোপকথন শুরু করে যা দ্রুত অপ্রত্যাশিতভাবে দার্শনিক হয়ে ওঠে।
অ্যামি খোলাখুলিভাবে বলে:
"আমি এই জীবনের কাজটি করতে পারছি না। আমি বিরক্ত। আমি খুশি নই। আমি সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে চাই"
তার বড় ভাই রাবি এটিকে অস্পষ্ট বলে উড়িয়ে দেয় এবং স্পষ্টতা দাবি করে। তাদের বাবা (উম্বাচি নিজেই) আরও কোমল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, ভাবছে যে সে কি বাড়িতে - তার প্রেমময় পরিবারের সাথে - জীবনকে অসুখী মনে করে। "বাবা দুঃখ পান,"যখন তিনি স্বীকার করেন যে, "তার পরিবারের খুশি অথচ তার ছোট্ট মেয়েটি খুশি নয়।"
অ্যামি কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার হতাশা তার পরিবারের সাথে নয়, বরং তার স্কুল জীবনের রুটিন এবং পুনরাবৃত্তির সাথে। "একই স্কুল, একই শিক্ষক, একই সহপাঠী, একই সময়কাল," সে বিলাপ করে। তার ছোট ভাই আচু নির্লজ্জভাবে আরো বলে, "একই মা, একই বাবা, একই বাড়ি, একই পরিবার," তাকে পাল্টা জবাব দিতে বলে, "চুপ কর, ওরাংওটাং কোথাকার!"
উত্তেজনার মাঝে, অ্যামি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য করে।
“আমি বলছি না যে কোনও সুখ নেই। তবে কোনও উত্তেজনা নেই।”
একটি শিশুর এই সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণ তার চারপাশের প্রাপ্তবয়স্কদের নাড়া দেয় - এবং বর্ণনাকারীর নিজের হৃদয়ে আরও গভীরভাবে কিছু নাড়া দেয়।
এক শিশুর একঘেয়েমি থেকে পিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব পর্যন্ত
সেই রাতে, যখন অ্যামি একজন জ্ঞানী পারিবারিক বন্ধুর সান্ত্বনায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে, তার পিতা ঘুমোতে পারেন না। মেয়ের কথাগুলো তাকে তাড়া করে ফেরে—না, কথাগুলোর কারণে নয়, বরং সে কথাগুলো তার ভেতরে যা নাড়া দিয়েছে, সেই অজ্ঞাত এক মাঝবয়সি সংকটের কারণে, যার নাম তিনি এই প্রথম অনুভব করলেন।
তিনি বিছানায় শুয়ে কল্পনায় ভেসে যান। সেদিন সকালে তিনি রাস্তার পাশে একটি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়ি দেখেছিলেন। এখন সেই চিত্রটি তার জীবনের রূপক হয়ে ওঠে। তিনি নিজেকে কল্পনা করেন সেই মানুষ হিসেবে, যে একদিন আত্মবিশ্বাস আর স্বপ্ন নিয়ে গাড়ি চালাতেন, কিন্তু এখন পড়ে আছেন ভেঙে যাওয়া, দিশেহারা অবস্থায়। “সে ভাবেনি নেমে পড়াটা এমন হবে। আমিও ভাবিনি। আশা করছি, কোনোভাবে বাড়ি ফিরতে পারব,”—এমনটাই ভাবেন তিনি।
এই রূপক তার স্বপ্নেও ছড়িয়ে পড়ে—গাড়ি দুর্ঘটনা, বিমান দুর্ঘটনা, সবকিছুতেই যেন তিনি অথবা তার প্রিয়জনেরা জড়িয়ে পড়ছেন একেকটি করুণ পরিণতির মধ্যে।
তিনি তার বন্ধু নাযারের সঙ্গে মন খুলে বলেন। নাযারও স্বীকার করেন যে তিনিও এমন মানসিক অস্বস্তিতে ভোগেন। নাযার একে বলেন, “আত্মিক সেই ভুল চিন্তাভাবনা, যেগুলো রাত্রিকে তিক্ত করে তোলে।”
তিনি যখন ঘুমানোর চেষ্টা করেন, তখন জীবিকা, ভবিষ্যৎ, স্ত্রী, সন্তান, ছুটি—সব চিন্তা একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ে। সান্ত্বনা নয়, বরং একেকটি দুশ্চিন্তার রূপে। তিনি এই সবকিছুকে বলেন “অপমানজনক দান”—আধুনিক জীবনের এমন বোঝা, যা সুযোগের পোশাক পরে এসেছে।
“এই তো আমার অনুভূতি,”—তিনি ভাবেন—“সাগরের তীরগুলোর মতো, যা দরজার বাইরে এসে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না।”
কল্পনার ভার ও অর্থের খোঁজ
রফিকের নিজের মানসিক অবস্থার বর্ণনা কাব্যিক, কিন্তু একইসাথে হৃদয়বিদারকভাবে সৎ। তিনি বলেন, কল্পনা যেন এক উন্মত্ত ঘোড়ার মতো তাকে ঘিরে ফেলেছে ‘যদি হতো’ আর ‘যদি না হতো’—এসব ভয়ংকর সম্ভাবনার বেড়াজালে। সমস্যাটা প্রেমের অভাব নয়, আর্থিক চাপও নয়। বরং তা আরও সূক্ষ্ম—এক ধরনের আবেগগত দিশাহীনতা। তিনি লেখেন, “অনুভূতিগুলো এখন জোর দেওয়া শব্দে পরিণত হয়েছে, কল্পনাপ্রেমীদের এক অস্তিত্বহীন ভূগর্ভবাস।”
একটি আবেগঘন সাহিত্যিক পালিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে, তিনি স্মরণ করেন মালবিকাকে—এস. মাধবনের ক্যাপ্টেনস ডটার উপন্যাসের এক চরিত্র। “আমার অবস্থায় একমাত্র তাকেই দেখেছি,” তিনি লেখেন। যেন বলছেন, বাস্তব নয়—সাহিত্যই মাঝে মাঝে একজন মানুষের অন্তর্দহনকে সত্যিকারের প্রতিফলিত করতে পারে।
তার লেখাটি সমাধান দিয়ে শেষ হয় না, বরং একটি প্রশ্ন দিয়ে থামে—
“আপনাদের অবস্থা কেমন?”
এটি এক কোমল অথচ গভীর আহ্বান—
আমাদের নিজেদের নীরবতা, আমাদের অনড়, অনিদ্র রাতগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখার জন্য।
এই পোস্টের জবাবে, রফিক উম্বাচির তার মেয়ের নির্দোষ অস্তিত্বগত প্রশ্ন সম্পর্কে আবেগঘন পোস্টের গভীর চিন্তাশীল এবং সহানুভূতিশীল উত্তর দিয়ে, রাশীদ পি. উস্তাদ কেবল একটি মন্তব্যের চেয়েও বেশি কিছু লিখেছেন- যা আমাদের প্রজন্মের আত্মার প্রতি একটি আয়নার মত। একই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একজন কিশোরের সাথে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উস্তাদ আজ অনেক শিশু, যুবক এবং এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের অনুভূতি কী তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন কিন্তু তারা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেন না: বস্তুগত আরাম আত্মাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে অর্থের জন্য নীরব তৃষ্ণা জাগে।
এক বাস্তব অভিজ্ঞতা: দশম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্তিত্বগত সংকট
রশীদ পি. উস্তাদ তাঁর প্রতিফলনের শুরুতেই স্মরণ করেন একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। “চার মাস আগে,” তিনি লেখেন, “এক ভল্লিপ্পা (কাকা) আমাকে ফোন করলেন। তিনি বললেন, ‘আমার ছেলের ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। একবার আপনার সঙ্গে কথা বলা উচিত ওর।’”
উস্তাদ তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন, তবু জানতে চাইলেন—“কী ব্যাপার?”
ভল্লিপ্পা বললেন:
“সে আজকাল কিছু অদ্ভুত কথা বলে। কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। গতকাল এক শিক্ষকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে—আল্লাহ আমাকে কেন সৃষ্টি করেছেন? আমার বেঁচে থেকে কী লাভ? আমি যদি আজ গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাই, তাহলে আমার কী হবে?”
এগুলো কিশোর বয়সের কোনো সাধারণ আবদার বা দুঃখ নয়। এগুলো অস্তিত্বগত প্রশ্ন—এক তরুণ হৃদয়ের নিঃশব্দ ঝড়। বিদ্রোহ বা নজর কাড়ার কোনো প্রচেষ্টা নয়, বরং জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে এক নিঃসঙ্কোচ, আন্তরিক জিজ্ঞাসা।
এমন প্রশ্ন তখনই মাথায় আসে, যখন বাইরের জগতে তেমন কোনো দৃশ্যমান যন্ত্রণা নেই—কিন্তু অন্তরের গভীরে 'আমি কে, কেন আছি'—এই রকম প্রশ্ন অন্ধকারের মতো ঘন হয়ে আসে।
উস্তাদ বুঝিয়ে দেন—এই প্রজন্মের যেসব কিশোর-তরুণ এমন প্রশ্ন করছে, তারা পথ হারায়নি; বরং তারা খোঁজার পথে আছে। শুধু দরকার— এমন মানুষের যে তাঁদের এই নিরব প্রশ্নগুলো মন দিয়ে শোনে।
তুলনামূলক দৃশ্যপট: তখন এবং এখন
রশীদ পি. উস্তাদ গভীর ভাবনায় তুলনা টানেন তার প্রজন্মের শৈশব ও আজকের সময়ের শিশুদের মধ্যে।
তিনি এক ৯০-এর দশকের ছেলের শৈশবের কথা বলেন—হয়তো নিজেকেই বলছেন, কিংবা তাঁর চেনা কারো কথা। সে ছেলেটি বেড়ে উঠেছিল বস্তুগত দারিদ্র্যে, কিন্তু আবেগ-ভালবাসায় পরিপূর্ণ এক পরিবেশে।
তিনি স্মরণ করেন—একবার তাঁর গাল ফুঁলিয়ে থাকার কারণ ছিল এই যে, তাঁর চাচাতো ভাইয়ের জন্য উপহার এসেছিল গালফফেরত এক খালার দেওয়া নতুন লেদার চটি, অথচ তার জন্য কিছুই ছিল না।
অথবা, নতুন ঝকঝকে ব্যাগের বদলে পুরনো ব্যাগ হাতে পেয়ে সে যে ক্ষোভে কাঁদত।
দশ টাকার একটা চকোলেট কিনতে না পারার অসহায়তা—যখন বন্ধুরা স্কুল ট্যুরে যাচ্ছিল ১৫০-২০০ টাকা দিয়ে।
আরেক বন্ধুর বাবা সাইকেল কিনে দিলেন, কিন্তু তার সাইকেল তখনও ভাঙা পড়ে আছে—এই হিংসেটুকুও ছিল।
তবে এই সব অভাবের মাঝেও ছিল আকাঙ্ক্ষা—আর সেই আকাঙ্ক্ষাই জন্ম দিত উত্তেজনার।
দাদিমার চুমু, বোনের আলিঙ্গন, বাবা বা কাকুর দেওয়া একটি কলম, ঈদের দিনে কিংবা প্রতিবেশীর বিয়েতে এক প্লেট বিরিয়ানি—এসব মুহূর্ত ছিল অতল আনন্দের, হৃদয়ের গহীনে গেঁথে রাখার মতো।
উস্তাদ প্রশ্ন তোলেন—
“এর পেছনের কারণ কী?”
তিনি নিজেই বলেন,
“সেই সময়ের সঙ্গী ছিল অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আর অসহায়তা। আর তাই, পাওয়া মানেই ছিল পরিপূর্ণ আনন্দ।”
তুলনামূলকভাবে, আজকের শিশুরা আরামের মধ্যে জন্ম নেয়। তাদের চাহিদা তৈরি হওয়ার আগেই তা মিটে যায়। কোনো অপেক্ষা নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই—ফলে যখন কিছু এসে পড়ে, সেটি আর আনন্দের শিখরে পৌঁছায় না।
ইচ্ছার অর্থনীতি ধ্বসে পড়েছে,
আর তার সঙ্গে মলিন হয়ে গেছে সেই আবেগের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলো, যা একসময় জীবনকে করে তুলত রোমাঞ্চকর ও জীবন্ত।
সংকটের মূল: ইচ্ছার অনুপস্থিতি, শূন্যতার উত্থান
উস্তাদের মূল যুক্তি:
“উপভোগ এবং উত্তেজনা তখনই বিদ্যমান থাকে, যদি ইচ্ছা থাকে। আর ইচ্ছাকে টিকে থাকতে হলে, সবসময় কিছু না-পাওয়া থাকা উচিত।”
সহজভাবে বললে: অপূর্ণ ইচ্ছা না থাকলে আবেগিক প্রস্তুতি গড়ে ওঠে না, আর সেই কারণে, কোনো কিছু পাওয়ার আনন্দও হয় না।
এটি শুধু শিশুদের ব্যাপার নয়। প্রাপ্তবয়স্করাও এটি অনুভব করেন।
যখন সবকিছু পাওয়া যায়,
যখন প্রতিটি জিনিস অনলাইনে কেনা যায়,
যখন খাবার সবসময় হাতের কাছে থাকে,
যখন আমাদের ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং ওয়াই-ফাই যুক্ত—
তখন আর কী পাওয়ার অপেক্ষা থাকে?
যখন স্বাচ্ছন্দ্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন আত্মা একটি ভিন্ন প্রশ্ন ফিসফিস করে তোলে:
“এই-ই কি সব?”
এটি সেই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা, যা শরীর পূর্ণ হলেও আত্মা যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন আসে।
এই কারণেই অ্যামি কিংবা দশম শ্রেণির ছেলের মতো তরুণরাও জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে:
“আমি এখানে কেন? এর সবকিছুর অর্থ কী?”
আধুনিক বিশ্বের সমালোচনা: পরিপূর্ণতার ভ্রান্ত ধারনা
এরপর উস্তাদ একটি বৃহত্তর দার্শনিক সমালোচনার দিকে অগ্রসর হন।
“ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল বিশ্বব্যবস্থা,” তিনি লেখেন, “মানুষকে এই বিশ্বাসে অভ্যস্ত করে তুলেছে যে, তারা জীবনকে সফল করে তুলতে পারে এবং সুখী হতে পারে কেবল তারা যা চায় তা কিনে নিয়ে, যা খেতে চায় তা খেয়ে, এবং নিজেদের পছন্দের সব আনন্দ উপভোগ করে।”
এটাই ভোক্তা সংস্কৃতির মিথ্যা বাণী। এটি মানুষকে বলে—সুখ একটি পণ্য, যা কেনা যায়; এবং সাফল্য মানে হলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।
কিন্তু এই জীবনদর্শন কাঠামোগতভাবে ভ্রান্ত। এটি কাউকে ধৈর্য শেখায় না, ত্যাগ শেখায় না, আকাঙ্ক্ষা শেখায় না, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে—নিজের স্বার্থপরতার বাইরে কোনো উদ্দেশ্য শেখায় না।
যখন সব অভিজ্ঞতাকে কেবল ভোগের উপকরণে পরিণত করা হয়, এবং প্রতিটি চাহিদা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা হয়—তখন একঘেয়েমি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, এবং আরও ভয়ানকভাবে—শূন্যতা হয়ে ওঠে স্থায়ী।
অ্যামি কিংবা দশম শ্রেণির ছেলের মতো শিশুরা অকৃতজ্ঞ নয়। তারা কেবল এমন এক সংস্কৃতির শিকার—যে সংস্কৃতি অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু খুব কমই পূরণ করতে পেরেছে—
অর্থের দিক থেকে কম,
আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে কম,
ভক্তি বা বিস্ময়ের অনুভব থেকেও কম।
চূড়ান্ত প্রজ্ঞা: অর্থ দেহের গণ্ডির বাইরেই রয়েছে
তবে সমাধান কী?
উস্তাদ একটি চিরন্তন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন:
“যখন সব বস্তুগত চাহিদা মিটে যাবে এবং সব দুশ্চিন্তা শেষ হয়ে যাবে, তখন মানুষ অনুভব করবে যে তার অস্তিত্ব কেবল শারীরিক নয়, বরং অর্থহীন। তখনই তার মধ্যে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা জাগবে।”
এই তৃষ্ণা নিভানো যায় না নেটফ্লিক্স, জাঙ্ক ফুড বা নতুন আইফোন দিয়ে।
“এই সংকট কেবল তখনই অতিক্রম করা যাবে, যখন আমরা শেখাতে পারব যে মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত অর্থ রয়েছে কেবল অধিবাস্তবিক (metaphysical) স্তরে।”
ইসলামে—এবং আরও অনেক আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে—মানবসত্তাকে কেবল মাংস ও হাড়ের সত্তা হিসেবে দেখা হয় না। আমরা কেবল ভোক্তা নই—আমরা অন্বেষণকারী।
আমাদের যাত্রা তখনই পূর্ণ হয়, যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি, আমাদের উদ্দেশ্য বুঝি, এবং সত্যের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করি।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আধুনিক শিশুকে শেখাতে হবে কেবল কীভাবে সফল হতে হয় তা নয়—কেন বাঁচা দরকার, সেটিও।
উপসংহার: অর্থে ফিরে যাওয়া
রশীদ পি. উস্তাদের চিন্তাভাবনাগুলো এমন একটি মহামারির ওপর আলো ফেলেছে, যার নাম আমরা খুব কমই বলি—প্রাচুর্যের যুগে আধ্যাত্মিক শূন্যতা। অ্যামির উত্তেজনার জন্য কাতরতা, দশম শ্রেণির ছাত্রের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয়, রফিক উম্বাচির নির্ঘুম রাত—এই সবকিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।
এগুলো একই রোগের লক্ষণ:
একটি এমন জগতে অর্থহীনতার অনুভব, যেখানে সব কিছু রয়েছে—তবে কেন রয়েছে, তা কেউ জানে না।
এর সমাধান আরও ভোগে নয়, থেরাপি অ্যাপে নয়, বা মোটিভেশনাল কোটে নয়—
সমাধান রয়েছে অধিবাস্তব চেতনায় ফিরে যাওয়াতে—আত্মার স্রষ্টার সঙ্গে সংযোগ পুনরুদ্ধারে, এবং হৃদয়ের—এই মহাবিশ্বে তার অবস্থান বোঝার ক্ষমতায়।
কারণ, যখন আত্মা অনাহারে থাকে, তখন স্বর্গও নিস্তেজ মনে হয়। কিন্তু যখন আত্মা জেগে ওঠে, তখন কাকুর দেওয়া একটি কলম বা দাদুর একটি হাসিও হয়ে ওঠে এক খাঁটি ইলাহি উপহার।
আর সম্ভবত, এটাই সত্যিকারের উত্তেজনার সবচেয়ে বিশুদ্ধ রূপ।