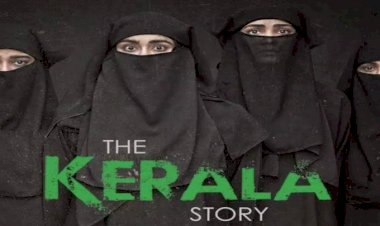ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ওলামা সমাজের অবদান
ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়েছিল ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ দিয়ে, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করে।স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক বিপ্লব নয়, বরং এটি ছিল জাতি হিসেবে আত্মচেতনার জাগরণ, উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের বিকাশ এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এ আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপে হিন্দু-মুসলিম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কৃষক-শ্রমিক, নারী-পুরুষ সমাজের নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
এই বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের এক বিশেষ ও তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত কিন্তু গভীর প্রভাববিস্তারকারী অংশীদার ছিল মুসলিম সমাজের শিক্ষিত ধর্মীয় নেতৃত্ব, যাদের আমরা “ওলামা সমাজ”। এই ওলামা সমাজ কেবল ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রচারে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ—যা অনেক ঐতিহাসিক “প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম” হিসেবে বিবেচনা করেন—তাতে ওলামা সমাজের কর্মঠ অংশগ্রহণ তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রভাবের প্রমাণ বহন করে তাঁরা একদিকে যেমন রাজনৈতিক প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছেন (যেমন শাহ আবদুল আজিজের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ‘জিহাদের ফতোয়া’, বা মৌলানা ফজল-ই-হক খৈরাবাদীর সশস্ত্র লড়াই), তেমনি অন্যদিকে তাঁরা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটি সামষ্টিক চেতনা গড়ে তুলতে সাহিত্য, ধর্মীয় বক্তৃতা ও শিক্ষার মাধ্যমে কাজ করেছেন|ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান, জেল-জুলুম সহ্য করা, স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন, এবং মুসলিম সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করে তোলা—এসব কর্মকাণ্ডে ওলামা সমাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
তাছাড়া ওলামারা শুধু ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার দায়িত্বই নেননি, বরং তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী, শোষণমূলক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি আদর্শিক ও নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ শাসন কেবল অর্থনৈতিক শোষণের বাহক নয়, বরং ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার জন্যও আসন্ন অমঙ্গলের লক্ষণ তাই তাঁদের প্রতিরোধ ধর্মীয় অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে হলেও এর জিনের পেটি ছিল জাতীয়তাবাদ ও মানবিক মর্যাদার চেতনাতেও বিস্তৃত।
ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতৃত্বের জাগরণ: ওলামাদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী অনুভূতির উদ্রেক ও তাৎপর্য
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হিসেবেও কাজ করেছে। এই দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে বহুমাত্রিক ধারা গড়ে ওঠে, তার মধ্যে ধর্মীয় নেতৃত্ব, বিশেষত মুসলিম সমাজের আলেম সমাজ তথা ওলামাদের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশবিরোধী চেতনার যে বীজ ওলামাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, তা পরবর্তীকালে এক জাগরণে রূপ নেয়, যা কেবল ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ছিল না, বরং তা ছিল একটি রাজনৈতিক আদর্শিক অবস্থানও। এই অবস্থান ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাসে এক অনন্য মাত্রা সংযোজন করে।
উনিশ শতকের শুরুতে মুসলিম শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সাথে সাথে মুসলিম সমাজ এক গভীর মানসিক সংকটে পড়ে যায়। শাসনব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম ধর্মীয় নেতারা—বিশেষ করে ওলামারা—এই দখলদার শাসনকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে শুরু করেন। ১৮০৩ সালে দিল্লি ব্রিটিশদের দখলে চলে গেলে প্রসিদ্ধ আলেম শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী এক ঐতিহাসিক ফতোয়া জারি করেন, যেখানে তিনি ভারতবর্ষকে “দারুল হারব” হিসেবে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে ধর্মীয়ভাবে ব্রিটিশ শাসনের অবৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সশস্ত্র প্রতিরোধের নৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়।
এই নৈতিক ভিত্তির ওপর ভর করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে ওলামাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বহু আলেম সেই বিদ্রোহে কেবল সমর্থনই দেননি, সরাসরি নেতৃত্বও দিয়েছেন। মাওলানা ফজল-ই-হক খৈরাবাদী, মাওলানা রহমত আলী প্রমুখ আলেমরা ফতোয়া প্রদান, প্রচারণা ও বিদ্রোহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে ধর্মীয় নেতৃত্ব কেবল মসজিদ বা মাদ্রাসায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাজনৈতিক শোষণ ও দখলের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ তাদের দায়িত্বের অংশ। যদিও ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হয়, কিন্তু এই আন্দোলনের মাধ্যমে ওলামাদের চেতনার যে বিকাশ ঘটে, তা পরবর্তীতে নতুন কৌশলে রূপ নেয়—এবং সেই কৌশল ছিল শিক্ষা, আদর্শিক নির্মাণ ও সাংগঠনিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ আধিপত্যের মোকাবিলা।
এই চেতনার ধারাবাহিকতায় ১৯০৪ সালে “মানযারে ইসলাম” প্রতিষ্ঠিত হয়, যা উপমহাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার এক বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বেরেলি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ যেমন—মাওলানা আহমেদ রেজা খান ও মাওলানা আমজাদ আলী—ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিম সমাজে ব্রিটিশবিরোধী আত্মপরিচয়ের বিকাশে ভূমিকা রাখেন। তাঁরা ব্রিটিশ শিক্ষা, বিচার ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণে উদ্যোগ নেন। এই আন্দোলন মুসলিম সমাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার বীজ বপন করে, যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অন্তঃসলিলা প্রতিরোধের অংশ হয়ে ওঠে।
পরবর্তী সময়ে এই ধর্মীয় চেতনার রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটে খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯১৯ সালে এই আন্দোলনে ওলামারা ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত হন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মাওলানা মাহমুদ হাসান এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে প্রমাণ করেন যে ধর্মীয় নেতৃত্বও ব্রিটিশবিরোধী জাতীয় ঐক্যের কাণ্ডারী হতে পারে। খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ওলামাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃহত্তর মুসলিম জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং জাতীয় আন্দোলনের একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।
এই ধারাকে আরও সংগঠিত করে তোলে ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে উলেমা-এ-হিন্দ। সংগঠনটি ধর্মীয় দায়িত্ববোধ ও জাতীয় রাজনৈতিক দায়িত্ববোধকে সমন্বিত করে একটি বৃহত্তর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে। ওলামারা কেবল ধর্মীয় ফতোয়া ও বক্তব্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সক্রিয়ভাবে অসহযোগ আন্দোলন, শিক্ষা বর্জন ও সামাজিক বয়কটের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাদের প্রচারে মুসলিম সমাজে জাতীয়তাবাদের বোধ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সংহতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।
ওলামাদের মধ্যে এই ব্রিটিশবিরোধী চেতনার তাৎপর্য বহুমাত্রিক। প্রথমত, এটি ধর্মীয় চিন্তাকে কেবল আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করে। দ্বিতীয়ত, এটি মুসলিম সমাজে আত্মপরিচয়ের ধারণাকে জাগ্রত করে, যা ঔপনিবেশিক শাসনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলায় অপরিহার্য ছিল। তৃতীয়ত, ওলামাদের নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন করে এবং রাজনৈতিক ঐক্যের একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও, ব্রিটিশবিরোধী ফতোয়া, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, বিদেশে গমন করে সংগঠনের প্রচার ও সহিংস-অসহিংস উভয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ—সব মিলিয়ে ওলামাদের এই চেতনা ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক প্রতিরোধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়।
এই প্রেক্ষাপট থেকে বলা যায়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নৈতিকতা ও ধর্মীয় বৈধতা প্রতিষ্ঠায় ওলামাদের ফতোয়া ও ব্যাখ্যা ছিল কেবল সহায়ক নয়, বরং এক অপরিহার্য ও নির্ণায়ক উপাদান। এসব ধর্মীয় রায় ও ব্যাখ্যা মুসলিম সমাজের কাছে মুক্তিসংগ্রামকে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে নয়, বরং ঈমানি দায়িত্ব ও ন্যায়ের লড়াই হিসেবে তুলে ধরেছিল। এর ফলে সাধারণ মুসলমানদের মনে স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। ওলামাদের এই ভূমিকা উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামে মুসলিম সমাজের সক্রিয় ও ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শিক ও নৈতিক ভিত্তিকে সুসংহত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটি দৃঢ় ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রচনা করেছিল।