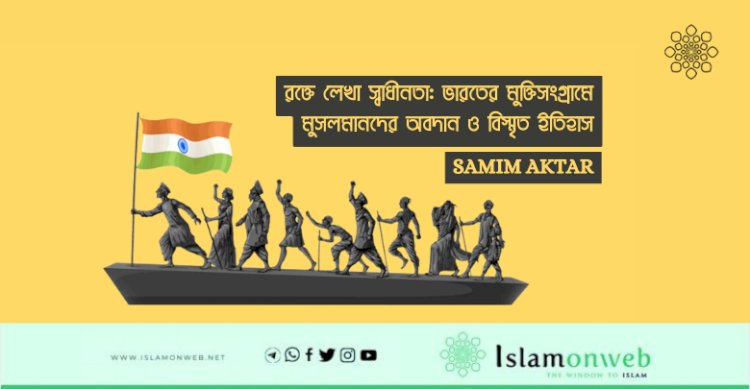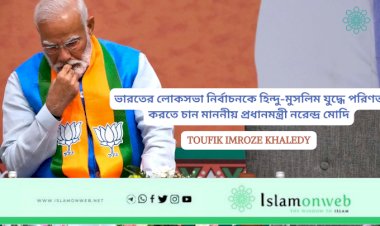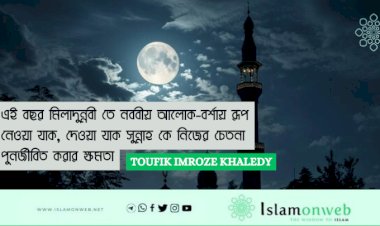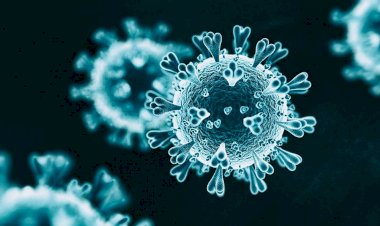রক্তে লেখা স্বাধীনতা: ভারতের মুক্তিসংগ্রামে মুসলমানদের অবদান ও বিস্মৃত ইতিহাস
ভূমিকা:
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের সকলের গর্বের একটি অধ্যায়। এই সংগ্রাম ছিল বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষার মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই ইতিহাসের পাতায় কিছু নাম উজ্জ্বলভাবে জ্বলজ্বল করে, আবার অনেক নামই ধুলায় ঢাকা পড়ে যায়। বিশেষ করে মুসলিম সমাজের ভূমিকাকে আজও ইতিহাসের মূল স্রোত থেকে অনেক সময়েই সরিয়ে রাখা হয়।
এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক কুশবন্ত সিং একবার লিখেছিলেন: "ভারতের স্বাধীনতা মুসলিম রক্তে লেখা, কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি ছিল।
বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে একটি গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী, ইতিহাসকে বিকৃত করে মুসলিমদের ‘বিদেশি’, ‘দেশবিরোধী’ বা ‘বিভাজনের দায়ী’ বলে প্রচার করছে। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতাকে যদি আমরা খুঁজি, তবে দেখতে পাবো—মুসলমানরা ছিলেন এই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী যোদ্ধা, শিক্ষা সংস্কারক, ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় পথপ্রদর্শক এবং সর্বোপরি দেশের গর্বিত সন্তান।
মুসলিমদের অবদান কেবল কংগ্রেস বা খেলাফত আন্দোলনের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা অংশ নিয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবে, উদারপন্থী রাজনীতিতে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় গণজাগরণে এবং সংবাদপত্রের কলম ধরেও। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা অর্জনের দিন পর্যন্ত, ভারতের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য।
এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করবো সেই সব বিস্মৃত, ভুলে যাওয়া মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাহিনী তুলে ধরতে। যারা শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং মানবতা, ন্যায়বিচার ও সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন। আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস জানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি একটি সমন্বিত, ধর্মনিরপেক্ষ ভারত নির্মাণে এই অধ্যায়গুলো চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি।
প্রতিরোধ (১৭৫৭–১৮৫৭)
নবাব সিরাজউদ্দৌলা থেকে শুরু করে টিপু সুলতান ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত মুসলিমদের প্রথম প্রতিবাদ
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই—১৯৪৭ সালে নয়, এমনকি ১৮৫৭ সালেও নয়। এর বীজ রোপিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালে, পলাশীর যুদ্ধে। আর সেই ইতিহাসের প্রথম সাহসী প্রতিরোধকারী ছিলেন একজন মুসলিম শাসক—নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রতিরোধ (১৭৫৭)
সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রভাব এবং সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং ইংরেজদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তাঁর নিজ সেনাবাহিনীর একাংশ (বিশেষত মীর জাফর) ইংরেজদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলেই পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন এবং ব্রিটিশরা বাংলায় তাদের শাসনের ভিত্তি গড়ে তোলে। সিরাজউদ্দৌলার প্রতিবাদ ছিল স্বাধীনতার প্রথম জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ। যদিও পরাজয় আসে, তাঁর সাহস আজও স্মরণীয়।
হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের সংগ্রাম (১৭৬০–১৭৯৯)
পলাশীর পর ব্রিটিশ শাসন ধীরে ধীরে দক্ষিণ ভারতের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানে তাদের শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হায়দার আলী এবং তাঁর পুত্র টিপু সুলতান—দুইজনেই ছিলেন মহীশূরের শাসক।
টিপু সুলতান , যাঁকে “শের-ই-মাইসুরু” বা মাইসোরের বাঘ বলা হয়, ছিলেন ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তিনি চারটি ইংরেজ-মহীশূর যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। তিনি প্রথম ভারতীয় শাসক যিনি লোহার আবরণযুক্ত রকেট ব্যবহার করেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক সংস্কার, এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় মনোভাব তাঁকে ইতিহাসে অনন্য করে তোলে। ১৭৯৯ সালে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতান শহীদ হন। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন—
“আমি একদিন সিংহের মতো বাঁচতে চাই, গাধার মতো একশো বছর নয়।” এই বীরত্বপূর্ণ উক্তি আজও দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে আছে।
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ – ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ
১৮৫৭ সালে শুরু হয় ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় বিদ্রোহ— “সিপাহী বিদ্রোহ” বা “প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম”। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। যদিও তিনিও প্রবীণ এবং অনেকটাই প্রতীকী নেতা ছিলেন, তবু হিন্দু-মুসলিম সিপাহীরা একবাক্যে তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে মান্য করেন।
বহু মুসলিম আলেম, সৈনিক ও সাধারণ মানুষ এই বিদ্রোহে যোগ দেন। বিশেষত দিল্লি শহর ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ব্রিটিশরা মুসলমানদের উপর কঠোর প্রতিশোধ নেয়। দিল্লির প্রাচীন মসজিদগুলোকে অপমানজনকভাবে ঘোড়ার আস্তাবল, বেকারি ও স্টোররুম বানানো হয়। হাজার হাজার মুসলমানকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।
মাওলভি মোহাম্মদ বাকির ছিলেন দিল্লির একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক যিনি ‘দিল্লি উর্দু আখবার’ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী লেখালেখির জন্য ভারতের প্রথম শহীদ সাংবাদিক হিসেবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।
এক গবেষণায় জানা যায়, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ৬৫% শহীদ ছিলেন মুসলিম, যদিও তারা মোট জনসংখ্যার ২৫% ছিল মাত্র। ইতিহাসবিদ সাইয়েদ উবাইদুর রহমান তাঁর বই Biographical Encyclopedia of Indian Muslim Freedom Fighters-এ এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন।
১৮৫৭–১৯০০: সাংগঠনিক রূপ
১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকরা মুসলিম সমাজকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। কারণ ব্রিটিশদের বিশ্বাস ছিল যে এই বিদ্রোহের মূল নেতৃত্বে ছিল মুসলমানরাই। ফলস্বরূপ, বহু মুসলিম পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়, মসজিদ-মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যেই দুটি ধারা তৈরি হয়—একটি ধারা ছিল সরাসরি প্রতিরোধ ও বিপ্লবের পক্ষে, আরেকটি ধারা বিশ্বাস করতো ধৈর্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির মাধ্যমে ব্রিটিশদের মোকাবিলা করতে হবে।
এই সময়ে মুসলমান সমাজে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজ তখন সরাসরি প্রতিরোধের মতো অবস্থায় ছিল না। তাই তিনি শিক্ষাকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে বেছে নেন। তিনি মুসলিম সমাজকে আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানমুখী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে আলিগড়ে ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, যা পরে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত হয়।
স্যার সৈয়দ আহমদ খান মনে করতেন—
“যদি মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ না করে, তাহলে তারা চিরকাল পিছিয়ে পড়বে এবং অন্য জাতিগুলোর তুলনায় দুর্বল থাকবে।”
তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলিগড় আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা, যেন তারা সরকারি চাকরি ও সমাজে মর্যাদা অর্জন করতে পারে। তবে, তাঁর এই ধারা নিয়ে বিতর্কও ছিল। অনেক মুসলিম নেতা মনে করতেন, তিনি ইংরেজদের খুব বেশি কাছাকাছি চলে গেছেন এবং রাজনীতি থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।
মৌলভী আবদুল লতিফ:
এই সময়েই আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব ছিলেন মৌলভী আবদুল লতিফ । তিনি ১৮৬২ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রথম মুসলিম সদস্য হন। সেখানে তিনি সরাসরি কৃষকদের পক্ষে কথা বলেন এবং একটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, যা জমিদারদের স্বার্থে ছিল।
খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯–১৯২৪)
১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ ও তার পরবর্তী কঠিন সময় পার করে মুসলমানরা আবার নতুনভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে সক্রিয় হতে শুরু করে। এই সময় দুটি প্রধান আন্দোলনের জোয়ার দেখা যায়: খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন, যেগুলির নেতৃত্বে ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট মুসলিম নেতা। এই আন্দোলনগুলি ছিল শুধু ব্রিটিশবিরোধী নয়, বরং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক সোনালি অধ্যায়ও বটে।
খেলাফত আন্দোলন
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা তুরস্কের উসমানিয়া খেলাফতের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং খেলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্তির পথে এগোয়। তুরস্কের খলিফা ছিলেন মুসলিম বিশ্বে এক আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক। ফলে, ভারতের মুসলিমদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা খিলাফতের সমর্থনে আন্দোলনে নামেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন দুইজন মুসলিম নেতা— মওলানা মুহাম্মদ আলী এবং শওকত আলী , তাঁদের মা
অসহযোগ আন্দোলন
খেলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় মহাত্মা গান্ধী -র নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলন, যা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, সরকারি চাকরি ও স্কুল বর্জনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে। গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমানদের এই ঐক্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন।
গান্ধীজি এই সময় বলেছিলেন:
“যদি আমি একমাত্র মুসলমানদের সাহায্যেই ব্রিটিশদের ভারত থেকে তাড়াতে পারি, তাহলে আমি তা করতে প্রস্তুত। কারণ এটাই ন্যায় ও সত্যের পথ।”
বিপ্লবী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা
“ইনকিলাব জিন্দাবাদ” থেকে “জয় হিন্দ” — মুসলিম বিপ্লবীদের ভূমিকা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শুধু অহিংস আন্দোলনই ছিল না, বরং একই সঙ্গে চলে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ। বিশেষত তরুণ মুসলমান বিপ্লবীরা এ সময় সাহসিকতার সঙ্গে অস্ত্র হাতে ব্রিটিশদের মোকাবিলা করেন। তাঁরা আত্মবলিদানকেই স্বাধীনতার চূড়ান্ত পথ বলে বিশ্বাস করতেন।
আশফাকউল্লা খান:
আশফাকউল্লা খান, হিন্দু বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল -এর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে কাকোরি ট্রেন ডাকাতি (১৯২৫) সংঘটিত করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের সরকারি কোষাগার লুট করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অর্থ জোগাড় করা।
আশফাকউল্লা ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ মুসলমান দেশপ্রেমিক, যিনি সাহসের সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন। ফাঁসির আগের দিন তিনি বলেছিলেন—
“আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি। আমার প্রাণ ভারতের জন্য উৎসর্গিত।”
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ:
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুসলিম নেতা, যিনি ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে কংগ্রেস সভাপতি হন—সবচেয়ে কম বয়সে এই পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি।
আজাদ ছিলেন একাধারে ইসলামি চিন্তাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাংস্কৃতিক দূত। তাঁর বিখ্যাত উক্তি—
“আমি গর্বিত যে আমি একজন মুসলমান। কিন্তু আমি তার চেয়েও বেশি গর্বিত যে আমি একজন ভারতীয়।”
তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং কট্টরভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।
খান আব্দুল গফফার খান:
খান আব্দুল গফফার খান, যিনি “ফ্রন্টিয়ার গান্ধী” নামে পরিচিত, ছিলেন পাখতুন সমাজের এক অহিংস সংগ্রামী নেতা। তিনি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন “খুদাই খিদমতগার” আন্দোলন—এটি ছিল এক শান্তিপূর্ণ পাঞ্জাবি–পাখতুন আন্দোলন, যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি করে।
তাঁদের স্লোগান ছিল:
“সত্য ও অহিংসার পথেই প্রকৃত বিজয় সম্ভব।”
গান্ধীজির Salt March ও অন্যান্য অহিংস আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ভারতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সীমান্ত বিভাজন তাঁকে আফগানিস্তানের দিকে ঠেলে দেয়।
উপসংহার:
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মুসলিমদের অবদান এক ঐতিহাসিক সত্য — কিন্তু আজ সেই সত্য প্রায় বিস্মৃত। স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা তাঁদের জীবন, সময়, মেধা ও রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য লড়েছেন। আজ যখন ইতিহাস বিকৃত করে বলা হয় যে মুসলমানরা এই দেশের শত্রু ছিল, তখন আমাদের এই ভুলে যাওয়া ইতিহাস” নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা জরুরি। কারণ—
“যে জাতি তার সত্য ইতিহাস জানে না, সে জাতি কখনোই ভবিষ্যতের পথ চিনতে পারে না।”
শেষে একটাই কথা বলা যায় —ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস মুসলিমদের রক্ত ও আত্মত্যাগ ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাঁদের স্মরণ করাও দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের এক রকম দায়িত্ব।