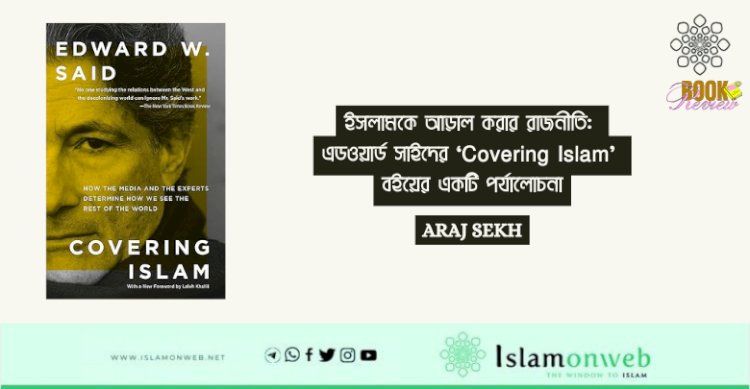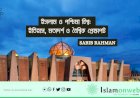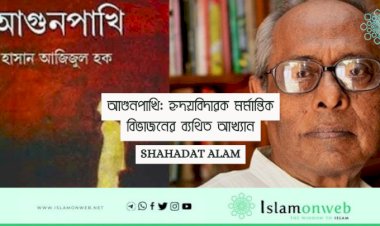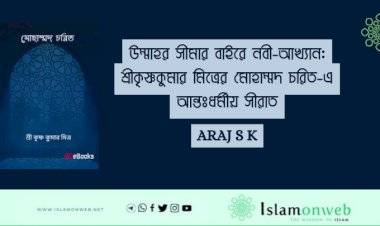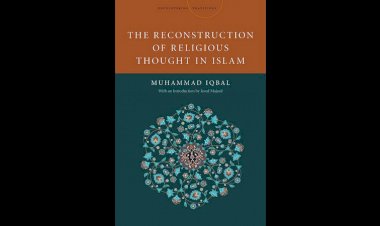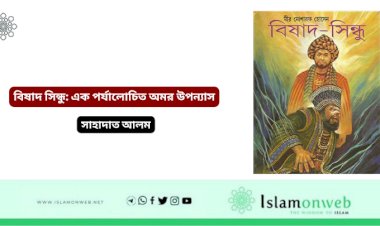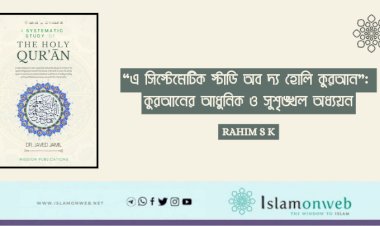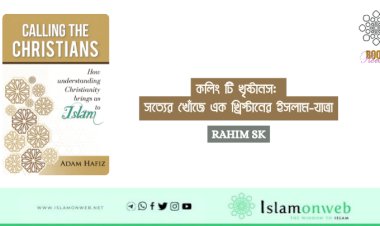ইসলামকে আড়াল করার রাজনীতি: এডওয়ার্ড সাইদের ‘Covering Islam’ বইয়ের একটি পর্যালোচনা
সূচনা
এডওয়ার্ড সাইদ-এর “Covering Islam” নামক বইটি ইসলাম, মুসলমান এবং পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক নিয়ে রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রয়ীর (তিন খণ্ডের গ্রন্থমালা) শেষ বই। এই ত্রয়ীর অন্য দুটি বই হলো: Orientalism (১৯৭৮) এবং The Question of Palestine (১৯৭৯)। এই বইটি মূলত ইসলাম সম্পর্কে ‘অশুভ সাধারণীকরণ’ এবং মুসলমানদের ‘উন্মাদ, হিংস্র, কামুক ও অযৌক্তিক’ হিসেবে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের বিষয়ে লেখা। বইটিতে সাইদ আমাদের ইরানী বিপ্লব, জিম্মি সংকট, উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১৯৯৩ সালের বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে নিয়ে যান এবং এসব ঘটনার পর যেভাবে পশ্চিমা গণমাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচার চালিয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন।
এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে, ইরানী বিপ্লব এবং জিম্মি সংকটের পরপরই। ১৯৯৭ সালে এর একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যেখানে নতুন একটি ভূমিকা যোগ করা হয় এবং বইটি হালনাগাদ করা হয়। ১৯৮১ বা ১৯৯৭ সালে যেমন ছিল, আজও ইসলাম একটি তীব্রভাবে আলোচিত এবং গণমাধ্যমের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বিষয়।
ইসলামকে জীবন্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে বোঝার প্রতিবন্ধকতা
Covering Islam বইটির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে Orientalism নামক তার বিখ্যাত বইয়ের কেন্দ্রীয় ধারণাগুলোর সম্প্রসারণ। সেই বইতে সাইদ আলোচনা করেন যে, ‘জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক’ রয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের যে জ্ঞান, তা মূলত আধিপত্য, সংঘর্ষ এবং সাংস্কৃতিক বৈরিতার মাধ্যমে গঠিত। ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পূর্ণ বিপরীত – এক ‘অপর’ হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি কাঠামো তৈরি করে যা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের পথ কঠিন করে তোলে। সাইদের মতে, যতক্ষণ এই কাঠামো কাজ করে, ইসলামকে একজন জীবন্ত ও জাগ্রত অভিজ্ঞতা হিসেবে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, ওরিয়েন্টালিজম নামক একাডেমিক শাখার সবচেয়ে বড় ভুল হলো ইসলামকে একটি একক, সার্বজনীন রূপে উপস্থাপন করা। এটি ইসলামের ও মুসলমানদের ওপর এক ধরনের ‘সহিংস আক্রমণ’ যা তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর চাপিয়ে দেওয়া ভূমিকার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বাধ্য করে।
Covering Islam বইটিতে তিনটি মুখ্য অধ্যায় আছে: Islam as News, The Iran Story এবং Knowledge and Power। Islam as News অধ্যায়ে সাইদ ইসলাম এবং খ্রিস্টান পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্কের ইতিহাস এবং বিশেষ করে ইউরোপে ইসলামী বাহিনীর আক্রমণ থেকে যে হুমকি অনুভূত হতো তার কথা বলেন। এই হুমকির ধারণা এখনও পশ্চিমা বিশ্বের মনোজগতে বিদ্যমান বলে তিনি দাবি করেন। ইসলাম সম্পর্কে এই ভয় এবং হুমকির ধারণার শিকড় রয়েছে ধর্মীয় ইতিহাসে, যেখানে ইসলামকে খ্রিস্টধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে তেলের দাম বেড়ে যাওয়াকে মুসলিম বিশ্বের একটি বিশ্বজয় করার চেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যা পশ্চিমকে আতঙ্কে ফেলে দেয়। এই হুমকির অনুভূতি পশ্চিমা সমাজে ব্যাপক ইসলামবিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে এডওয়ার্ড সাইদ তার বইতে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে পশ্চিমা গণমাধ্যম ইসলামকে প্রতিনিয়ত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, এবং এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের জটিল মিশ্রণ।
এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে যে ইসলাম ও মুসলমানরা আমেরিকানদের — এবং প্রসারিতভাবে পুরো পশ্চিমা বিশ্বের — কাছে বেশিরভাগই অজানা। পশ্চিমারা ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জানে, তা মূলত কিছু ‘সংবাদযোগ্য ঘটনা’র মাধ্যমে, যেমন – তেল, ইরান, আফগানিস্তান কিংবা সন্ত্রাসবাদ। মিডিয়া যেসব বিষয়কে সংবাদযোগ্য মনে করে এবং ইসলাম বা মুসলমানদের নিয়ে যেসব খবর প্রচার করে, তা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আসল রূপটিকেই আড়াল করে দেয়। এই কারণে “Covering Islam” শিরোনামটি দ্ব্যর্থবোধক: ‘কভার করা’ অর্থাৎ খবর লেখা এবং একইসঙ্গে আড়াল করা বা ঢেকে রাখা। সাইদ বলেন, এটি সেই সব কিছুর বিপরীত, যা ‘প্রকাশিত’ হওয়া উচিত। মুসলমানদের শুধুই ‘সম্ভাব্য সন্ত্রাসী’ কিংবা ‘তেলের জোগানদাতা’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং এর ফলে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ঐতিহ্য, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলিমদের অগ্রণী ভূমিকা এবং অ্যালজেবরার আবিষ্কারের ইতিহাস ধামাচাপা পড়ে যায়।
মিডিয়ার পক্ষপাত এবং সত্যের আড়ালে থাকা দিকসমূহ
“Islam as News” অধ্যায়ে এডওয়ার্ড সাইদ দেখিয়েছেন, কীভাবে ‘সংবাদযোগ্য বিষয়’ নির্ধারিত হয়। সাইদের মতে, সংবাদ কেবল বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়, বরং এটি একটি জটিল এবং সচেতন নির্বাচনের প্রক্রিয়া। সাংবাদিকরা, সংবাদ সংস্থাগুলো এবং টিভি নেটওয়ার্কগুলো সচেতনভাবে ঠিক করে যে কী উপস্থাপন করা হবে, কীভাবে উপস্থাপন করা হবে, এবং কী বাদ যাবে। সাইদ বলেন, আমেরিকান মিডিয়া ও সাংবাদিকরা বিশ্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য সংগ্রহ করে, তা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে পড়ে যায় যা সরকারী নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, সংবাদযোগ্য বিষয়গুলোর পেছনে থাকে তেলের কোম্পানিগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ, ইহুদিবাদী গোষ্ঠী, এবং প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা মহলের প্রভাব।
সাইদ মনে করেন, মিডিয়া সব সময় আমেরিকার জনগণের কাছে সত্য সহজে প্রকাশ করে না। তার কথায়, ‘ছবি ও ধারণা বাস্তবতা থেকে সরাসরি আমাদের চোখে-মস্তিষ্কে এসে যায় না; সত্য সহজলভ্য নয়।’ তিনি বলেন, মিডিয়া সত্যের কিছু নির্দিষ্ট দিকের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অন্য দিকগুলোকে উপেক্ষা করে — এভাবেই একটি পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়।
ইরান ও পশ্চিমা গণমাধ্যমের প্রতিবেদন
পরবর্তী অধ্যায় “The Iran Story” তে সাইদ পশ্চিমা বিশ্বের ইরানী বিপ্লব, রেজা শাহ পাহলভীর অপসারণ ও জিম্মি সংকটকে কেমনভাবে উপস্থাপন করেছে তা বিশ্লেষণ করেন। জিম্মি সংকটের সময় ইরান সম্পর্কিত মিডিয়া কাভারেজ বর্ণনা করতে গিয়ে সাইদ বলেন, সেখানে ‘ঘরানাগত কথাবার্তা, বিকৃত চিত্রায়ণ, অজ্ঞতা, অযাচিত জাতিগত অহংকার ও ভুল তথ্য’ মারাত্মকভাবে বিদ্যমান ছিল। যেখানে ‘আমরা’ ছিলাম ‘স্বাভাবিক’, সেখানে ‘তারা’ ছিল ‘আত্মমগ্ন উন্মত্ততায় মোহগ্রস্ত’, ‘শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পাগলপ্রায়’। আমেরিকান মিডিয়াতে খোমেনিকে উপস্থাপন করা হয়েছিল এক গম্ভীর, পাগড়ি পরা মধ্যযুগীয় শাসক হিসেবে, যিনি ইরানকে সপ্তম শতাব্দীতে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছেন। খোমেনি ও ইরান তখন যেন ইসলামের সব অস্বস্তিকর দিক – সন্ত্রাসবাদ থেকে শুরু করে পশ্চিমবিরোধিতা – এর প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বিপ্লবকারীদের উপস্থাপন করা হয়েছিল শাহ-এর আধুনিকায়নের বিরোধী হিসেবে। যেন এটি ছিল ‘নিয়ন্ত্রণহীন ইসলাম’ – একধরনের হুমকি, যেমনটা ছিল কমিউনিজম। এমনকি কিছু বিশেষজ্ঞও ইরান বিপ্লবকে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সমতুল্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, এবং দাবি করেন যে, এই বিশৃঙ্খলা ইসলাম ধর্মের ভিতরেই নিহিত।
মিডিয়াতে প্রকাশিত শিরোনাম যেমন: ‘Iran Sucks’, ‘Militant Islam’, ‘The Dagger of Islam’, ‘Ayatollah’s Mein Kampf’ বা ‘The New Barbarians are loose in Iran’ — এসব গল্প একটি জাতীয় উন্মাদনার জন্ম দেয়, যার ফলে জনগণের মধ্যে সামরিক হস্তক্ষেপের দাবি ওঠে এবং এমনকি ‘Nuke Tehran’ লেখা ব্যাজও প্রচলিত হয়। সাইদের বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, একটি জটিল আন্তর্জাতিক ঘটনাকে অত্যন্ত সরল নাটকীয় কাহিনীতে পরিণত করা হয়েছিল। তথাকথিত ‘বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ’-এর মাধ্যমে আমেরিকান জনগণকে অন্য একটি জাতির বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক অবস্থানে দাঁড় করানো হয়, অথচ সেই ঘটনাগুলোর পেছনের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে তারা সামান্যই জানত।
ইরানের রাজনীতিতে আমেরিকার দীর্ঘদিনের হস্তক্ষেপ – বিশেষ করে শাহ-কে ক্ষমতায় বসানো এবং দীর্ঘদিন ধরে তাকে টিকিয়ে রাখার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা – এসব ইতিহাস সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অংশ হয়ে ওঠেনি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইরানের ১৬০০ মাইল দীর্ঘ সীমান্তের মতো কৌশলগত কারণও খুব কমই আলোচিত হয়েছে। এভাবেই সাইদ দেখিয়েছেন, কীভাবে মিডিয়া সাধারণ মানুষকে একপাক্ষিক ও বিকৃত তথ্য দিয়ে গঠন করে এবং একটি জাতির প্রতি বিদ্বেষ গড়ে তোলে।
জ্ঞান উৎপাদনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব
পরবর্তী অধ্যায় “Knowledge and Power”-এ আলোচনা করা হয়েছে যে, কীভাবে পশ্চিমা ‘বিজ্ঞান’ বা তথাকথিত ‘বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনার জন্য তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি’ ব্যবহার করে ইসলাম নামক এক ‘দূরবর্তী ও ভিন্ন সংস্কৃতির সমাজ’-কে ভুলভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। সাইদ লেখেন, ‘ইসলাম সম্পর্কে কোনো পেশাদার স্কলার যা-ই লিখুন না কেন, তা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও সরকার—এই তিনটি শক্তির প্রভাবের বাইরে নয়। এই শক্তিগুলোর প্রত্যেকটি ইসলামের ব্যাখ্যা নির্ধারণে এবং সেই অনুযায়ী ইসলাম সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে ‘জাতীয় স্বার্থে’ কাঙ্ক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।’
অর্থাৎ, ইসলামি বিশ্বের জ্ঞান ও উপস্থাপনাকে যুক্তরাষ্ট্রে মূলত নির্ধারিত করে ভূ-রাজনীতি ও অর্থনৈতিক স্বার্থ। ইসলামকে ‘মধ্যযুগীয়, বিপজ্জনক, শত্রুভাবাপন্ন ও হুমকিস্বরূপ’ হিসেবে দেখানোর ধারণা এতটাই প্রচলিত যে এটি একপ্রকার ‘আধুনিক মিথ’ বা প্রতিষ্ঠিত বর্ণনার রূপ পেয়েছে। এই দীর্ঘ ইসলাম-বিরোধী বর্ণনার বিপরীতে এডওয়ার্ড সাইদ আহ্বান জানান এক নতুন ধরনের জ্ঞানের, যাকে তিনি বলেন ‘antithetical knowledge’ বা ‘বিরোধী জ্ঞান’। তিনি এটিকে সংজ্ঞায়িত করেন এমন একটি জ্ঞান হিসেবে, যা তারা সৃষ্টি করেন যারা সচেতনভাবে প্রচলিত মতবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রথার বিরুদ্ধে লিখছেন। এখানে ওরিয়েন্টালিজমের ‘পদ্ধতিগত নীরবতা’র পরিবর্তে স্কলারশিপের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে সরাসরি আলোচনা করা হয়।
এই ধরণের ‘বিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা’-তে ইসলামকে আর সংকুচিত বা একরঙা হিসেবে তুলে ধরা হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই ধরনের একজন চিন্তক তার জ্ঞানকে ক্ষমতার সেবায় নয়, বরং সমালোচনা, সমাজ, সংলাপ এবং নৈতিক উপলব্ধির সেবায় নিয়োজিত করেন। এভাবেই সাইদ বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে ন্যায্য ও নৈতিক ভিত্তিতে জ্ঞানের চর্চা করতে হবে।