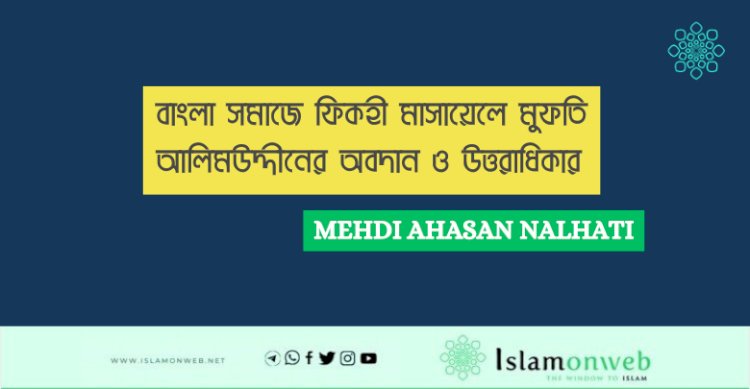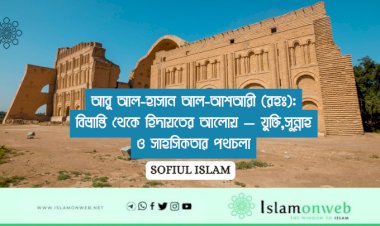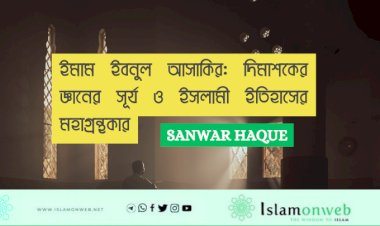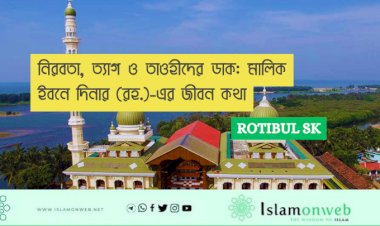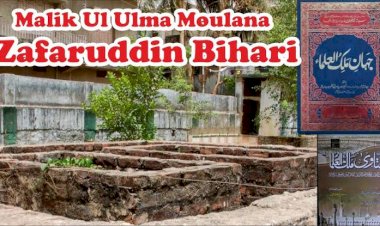বাংলা সমাজে ফিকহী মাসায়েলে মুফতি আলিমউদ্দীনের অবদান ও উত্তরাধিকার
ইসলামী জীবনের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নির্ধারণে ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ফিকহ। এ শাস্ত্র চর্চায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের বলা হয় ফকীহ, আর যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের মাধ্যমে জনগণকে সমাধান প্রদান করেন, তিনি হলেন মুফতি। বাংলা উপমহাদেশে এমন বহু আলেম ও ফকীহ ছিলেন যাঁরা এদেশের ফিকহী ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুফতি আলিমউদ্দীন রহ. একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত। তিনি কেবল ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে সমাজকে দিকনির্দেশনা দেননি, বরং পুরো একটি প্রজন্মকে ফিকহী আলোচনার পথে পরিচালিত করেছেন।
বাংলা মুসলিম সমাজে ফিকহী সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা, স্থানীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদ, ফতোয়া, এবং শরঈ সমাধান প্রদান, ইলমে ফিকহের শিক্ষাদান ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার, এসবই তাঁকে একটি ঐতিহাসিক উচ্চতায় স্থাপন করেছে। এই প্রবন্ধে আমরা মুফতি আলিমউদ্দীনের ফিকহী উত্তরাধিকার ও অবদানের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করব, যাতে করে বাংলা সমাজে তাঁর প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করা যায়।
জন্ম ও পারিবারিক পটভূমি
মুফতি আলিমউদ্দীনের জন্ম ১৯০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার একটি ছোট গ্রামে, একটি ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষানুরাগী পরিবারে। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আলিমউদ্দীন আহমদ। পিতা মাওলানা আব্দুল লতিফ ছিলেন স্থানীয় জামে মসজিদের ইমাম ও ফতোয়া প্রদানকারী, আর দাদা ছিলেন প্রখ্যাত আলেম, যিনি গ্রামীণ এলাকায় শরঈ সমাধান প্রদানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। পরিবারের শিক্ষিত পরিবেশ ও ইসলামী অনুশাসনের ধারাবাহিকতা তাঁর চরিত্র ও জ্ঞানপিপাসায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা
প্রাথমিক কুরআন শিক্ষা তিনি নিজ গ্রামের মক্তবে শুরু করেন। এরপর স্থানীয় দারুল উলূম মাদ্রাসায় নাহু-সরফ, ফারসি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ফিকহ, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে প্রাথমিক দীক্ষা নেন। ১৯২২ সালে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন, যেখানে তিনি হাদীস, উসূলুল ফিকহ, কিয়াস ও ইজতিহাদের উন্নত পাঠ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদনী, মুফতি কিফায়তুল্লাহ, এবং অন্যান্য বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ।
কর্মজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৩০ সালে তিনি মালদহে ফিরে এসে প্রথমে মাদ্রাসা আরাবিয়া রহমানিয়া-তে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে তিনি জামিয়া সিদ্দিকিয়া দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলা অঞ্চলে ফিকহ শিক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসাতে ফিকহের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং রাজ্যের দারুল ইফতার প্রধান মুফতি ছিলেন।
শিক্ষাগত জীবনী ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি
মুফতি আলিমউদ্দীনের জন্ম বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এক ধর্মপরায়ণ পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও হালকা পর্যায়ের ফতোয়া প্রদানকারী। ছোটবেলা থেকেই ইসলামি পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাঁকে দীনী ইলমের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। প্রাথমিক কুরআন শিক্ষার পর তিনি স্থানীয় মক্তব ও মাদ্রাসায় আরবি ভাষা ও ফারসি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন।
তাঁর উচ্চতর পড়াশোনা শুরু হয় কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায়। পরবর্তীতে তিনি ভারতের বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং সেখানে হাদীস, তাফসীর, উসূলে ফিকহ এবং কিয়াস-ইজতিহাদ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন তৎকালীন উপমহাদেশের বরেণ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ, যেমন মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী ও মুফতি কিফায়তুল্লাহ।
দেওবন্দের শিক্ষাজীবনে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক রুচি গড়ে ওঠে যুক্তিনির্ভর ফিকহ চর্চার দিকে। তিনি কেবলমাত্র দলীল মুখস্থ করা নয়, বরং দলীল বিশ্লেষণ, মতপার্থক্যের ঐতিহাসিক পটভূমি, এবং নতুন ঘটনার ক্ষেত্রে শরঈ নির্দেশনার প্রয়োগ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। এই মনোভাব তাঁকে একজন চিন্তাশীল ফকীহ ও প্রাজ্ঞ মুফতির পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করে।
ফতোয়ার ধারা ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ
বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা ছিল বিশেষভাবে জটিল ও বহুমাত্রিক। মুফতি আলিমউদ্দীন এই অঞ্চলের জনগণের ফিকহী সমস্যাবলি অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে নিরসন করতেন। তাঁর দেওয়া ফতোয়াগুলো ছিল অত্যন্ত সংযত ভাষায়, সুদৃঢ় দলীলভিত্তিক, এবং জনগণের মানসিকতা ও জীবনধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
তিনি বিশ্বাস করতেন, ফতোয়া কেবল দলীল নয়—সাথেই চাই বাস্তবতা উপলব্ধি ও সামাজিক কল্যাণের প্রতি দায়িত্ববোধ। উদাহরণস্বরূপ, জমিদারদের সঙ্গে কৃষকের সংক্রান্ত লেনদেন, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থা, ইচ্ছাকৃত তালাক ও নারীর অধিকার সংক্রান্ত ইস্যুতে তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।
তিনি ‘فتاویٰ علاء الدينية’ নামে একটি সুপরিচিত ফতোয়া সংকলন রচনা করেন, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরের জিজ্ঞাসার জবাব দলীলসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োগ ও স্থানীয় অনুশীলন ছিল সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ।
শিক্ষাদান ও প্রাতিষ্ঠানিক অবদান
মুফতি আলিমউদ্দীন কেবল ফতোয়া প্রদানে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একাধিক মাদ্রাসা ও দারুল ইফতা, যেখানে ছাত্রদের ফিকহ, উসূল, কিয়াস ও তর্জমার মাধ্যমে শরীয়তের গভীরতা বোঝানো হতো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে আজও ফতোয়া বিভাগ চালু রয়েছে, যেখানে তাঁর সংকলিত দলীল, মসআলা এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শেখানো হয়।
তিনি ছাত্রদের আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্লেষণী ফকীহ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে যুক্তির চর্চা, মতভেদ বোঝা, দলীল উপস্থাপন এবং ইজতিহাদের ব্যাকরণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শেখানো।
সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও তাঁর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি
উপনিবেশিক শাসন, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবক্ষয়ের সময়ে ফিকহ চর্চা সহজ ছিল না। তখনকার মুসলিম সমাজ অনেকাংশেই বিভ্রান্ত ছিল আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের টানাপোড়েনে। এই পরিস্থিতিতে মুফতি আলিমউদ্দীন যুগোপযোগী ও সময়ের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনাভিত্তিক ফিকহ চর্চার উদাহরণ স্থাপন করেন।
তিনি যেমন ব্যাংকের সুদের সাথে ইসলামী লেনদেনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন, তেমনি কলকারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্কেও শরঈ নির্দেশনা প্রদান করেন। নারীদের তালাক পরবর্তী অধিকার, যৌথ পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় তাঁর ফতোয়া ছিল আধুনিক সমাজের প্রশ্নের জবাব।
উত্তরাধিকার ও ভাবাদর্শের সম্প্রসারণ
মুফতি আলিমউদ্দীনের সর্ববৃহৎ অবদান ছিল তাঁর চিন্তা ও চর্চার উত্তরাধিকার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তর। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই উপমহাদেশজুড়ে নামকরা মুফতি, বিচারপতি ও শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।
তাঁর ফতোয়া ও শিক্ষাদর্শ আজও বিভিন্ন মাদ্রাসা ও ইসলামী গবেষণাকেন্দ্রে পড়ানো হয়। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের মধ্যে তাঁর নাম একপ্রকার আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর জীবনী ও কর্মপদ্ধতি আজকের যুগের ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত।
ফিকহী সমস্যার সমাধানে তাঁর পদ্ধতি ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি
মুফতি আলিমুদ্দিন (রহ.)-এর ফিকহী অবদানের অন্যতম প্রধান দিক হলো—তিনি যেভাবে জটিল ও সমসাময়িক মাসায়েলের সমাধানে সুস্পষ্ট ও সুসংহত একটি পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তাঁর ফতোয়ার নীতিমালায় দেখা যায় যে, তিনি কেবল কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে সিদ্ধান্ত দিতেন না; বরং ইজমা, কিয়াস, উর্ফ ও মাসলাহার মতো ফিকহী মূলনীতিগুলোকেও যথাযথভাবে কাজে লাগাতেন। তাঁর বিচার বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই প্রশস্ত ছিল যে, সমকালীন অনেক বিতর্কিত বিষয়ে তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য মতামত প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন।
তাঁর ফতোয়ায় একটি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়—তিনি স্থানীয় জনমানস ও সামাজিক বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন না। বরং একটি মাসআলার নির্ধারণে তিনি উরফ তথা স্থানীয় রীতিনীতিকেও বিবেচনায় নিতেন, যা ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরবঙ্গের কিছু উপজাতি অঞ্চলে সম্পত্তি বণ্টন ও বিবাহ-সংক্রান্ত কিছু ঐতিহ্য ছিল, যেগুলো শরীয়তের মূলনীতির সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সেখানে মুফতি আলিমুদ্দিন (রহ.) ত্বরিৎ হস্তক্ষেপ করে শরীয়তের আলোকে মাসআলা নির্ধারণ করেন এবং সংশ্লিষ্টদের তা বোঝাতে সক্ষম হন।
তিনি ইখতিলাফি মাসায়েলেও একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তাঁর ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, তিনি একাধিক মতের মাঝে প্রাধান্য নির্ধারণে দলীল, গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তবতার সমন্বয় করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘তালাক-ই-সালাসা’ তথা একসাথে তিন তালাক দেওয়ার মাসআলায় তিনি ঐতিহ্যবাহী হানাফী মতকে সমর্থন করলেও, সমাজে এর অপব্যবহার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির পক্ষে থাকতেন এবং প্রয়োজনে বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খুঁজতেন।
তাঁর ফিকহী কর্মকাণ্ডে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—‘মাসলাহা মুর্সালা’ তথা জনকল্যাণের উপযোগিতা নির্ণয়ে তাঁর দক্ষতা। অনেক সময় কোনো মাসআলার শরয়ি মূলনীতির বিশ্লেষণে তিনি এই দিকটিকে প্রাধান্য দিতেন, বিশেষত যখন তা মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণে ভূমিকা রাখে।
মুফতি আলিমুদ্দিন (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, ফতোয়া কেবলমাত্র একটি আইনি মত নয়, বরং এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক দিকনির্দেশনা, যা মানবজীবনের ধর্মীয় ও দুনিয়াবি উভয় প্রেক্ষাপটেই ভারসাম্য সৃষ্টি করে। তাই তাঁর ফতোয়াসমূহে কেবল গ্রন্থগত উদ্ধৃতি নয়, বরং যুক্তি, দালিলিক বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষিত-ভিত্তিক যুক্তি দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে একজন প্রাজ্ঞ ও জনদরদী ফিকহবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
উপসংহার
মুফতি আলিমউদ্দীন ছিলেন একাধারে গবেষক, মুফতি, শিক্ষক ও চিন্তাবিদ। তিনি বাংলা সমাজে ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন এবং জনগণের জন্য শরঈ দিকনির্দেশনার এক প্রজ্ঞাবান সেতুবন্ধন স্থাপন করেন।
তাঁর ফতোয়া, শিক্ষাদান ও দারুল ইফতার উন্নয়ন আজও বহু মানুষকে প্রভাবিত করছে। তাঁর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়, কিভাবে শরীয়ত ও বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা যায়। তিনি শুধু তাঁর সময়ের একজন আলেম ছিলেন না, বরং ছিলেন এক চলমান দৃষ্টান্ত, যা প্রজন্মান্তরে চর্চিত হবে।
বাংলা সমাজে ফিকহী মাসায়েলে মুফতি আলিমউদ্দীনের অবদান ও উত্তরাধিকার
ইসলামী জীবনের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নির্ধারণে ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ফিকহ। এ শাস্ত্র চর্চায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদের বলা হয় ফকীহ, আর যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের মাধ্যমে জনগণকে সমাধান প্রদান করেন, তিনি হলেন মুফতি। বাংলা উপমহাদেশে এমন বহু আলেম ও ফকীহ ছিলেন যাঁরা এদেশের ফিকহী ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুফতি আলিমউদ্দীন রহ. একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত। তিনি কেবল ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে সমাজকে দিকনির্দেশনা দেননি, বরং পুরো একটি প্রজন্মকে ফিকহী আলোচনার পথে পরিচালিত করেছেন।
বাংলা মুসলিম সমাজে ফিকহী সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা, স্থানীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদ, ফতোয়া, এবং শরঈ সমাধান প্রদান, ইলমে ফিকহের শিক্ষাদান ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার, এসবই তাঁকে একটি ঐতিহাসিক উচ্চতায় স্থাপন করেছে। এই প্রবন্ধে আমরা মুফতি আলিমউদ্দীনের ফিকহী উত্তরাধিকার ও অবদানের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করব, যাতে করে বাংলা সমাজে তাঁর প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করা যায়।
জন্ম ও পারিবারিক পটভূমি
মুফতি আলিমউদ্দীনের জন্ম ১৯০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার একটি ছোট গ্রামে, একটি ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষানুরাগী পরিবারে। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল আলিমউদ্দীন আহমদ। পিতা মাওলানা আব্দুল লতিফ ছিলেন স্থানীয় জামে মসজিদের ইমাম ও ফতোয়া প্রদানকারী, আর দাদা ছিলেন প্রখ্যাত আলেম, যিনি গ্রামীণ এলাকায় শরঈ সমাধান প্রদানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। পরিবারের শিক্ষিত পরিবেশ ও ইসলামী অনুশাসনের ধারাবাহিকতা তাঁর চরিত্র ও জ্ঞানপিপাসায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা
প্রাথমিক কুরআন শিক্ষা তিনি নিজ গ্রামের মক্তবে শুরু করেন। এরপর স্থানীয় দারুল উলূম মাদ্রাসায় নাহু-সরফ, ফারসি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ফিকহ, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে প্রাথমিক দীক্ষা নেন। ১৯২২ সালে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন, যেখানে তিনি হাদীস, উসূলুল ফিকহ, কিয়াস ও ইজতিহাদের উন্নত পাঠ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদনী, মুফতি কিফায়তুল্লাহ, এবং অন্যান্য বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ।
কর্মজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৩০ সালে তিনি মালদহে ফিরে এসে প্রথমে মাদ্রাসা আরাবিয়া রহমানিয়া-তে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে তিনি জামিয়া সিদ্দিকিয়া দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলা অঞ্চলে ফিকহ শিক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসাতে ফিকহের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং রাজ্যের দারুল ইফতার প্রধান মুফতি ছিলেন।
শিক্ষাগত জীবনী ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি
মুফতি আলিমউদ্দীনের জন্ম বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এক ধর্মপরায়ণ পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও হালকা পর্যায়ের ফতোয়া প্রদানকারী। ছোটবেলা থেকেই ইসলামি পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাঁকে দীনী ইলমের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। প্রাথমিক কুরআন শিক্ষার পর তিনি স্থানীয় মক্তব ও মাদ্রাসায় আরবি ভাষা ও ফারসি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন।
তাঁর উচ্চতর পড়াশোনা শুরু হয় কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায়। পরবর্তীতে তিনি ভারতের বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং সেখানে হাদীস, তাফসীর, উসূলে ফিকহ এবং কিয়াস-ইজতিহাদ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন তৎকালীন উপমহাদেশের বরেণ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ, যেমন মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী ও মুফতি কিফায়তুল্লাহ।
দেওবন্দের শিক্ষাজীবনে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক রুচি গড়ে ওঠে যুক্তিনির্ভর ফিকহ চর্চার দিকে। তিনি কেবলমাত্র দলীল মুখস্থ করা নয়, বরং দলীল বিশ্লেষণ, মতপার্থক্যের ঐতিহাসিক পটভূমি, এবং নতুন ঘটনার ক্ষেত্রে শরঈ নির্দেশনার প্রয়োগ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। এই মনোভাব তাঁকে একজন চিন্তাশীল ফকীহ ও প্রাজ্ঞ মুফতির পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করে।
ফতোয়ার ধারা ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ
বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা ছিল বিশেষভাবে জটিল ও বহুমাত্রিক। মুফতি আলিমউদ্দীন এই অঞ্চলের জনগণের ফিকহী সমস্যাবলি অত্যন্ত সংবেদনশীলতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে নিরসন করতেন। তাঁর দেওয়া ফতোয়াগুলো ছিল অত্যন্ত সংযত ভাষায়, সুদৃঢ় দলীলভিত্তিক, এবং জনগণের মানসিকতা ও জীবনধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
তিনি বিশ্বাস করতেন, ফতোয়া কেবল দলীল নয়—সাথেই চাই বাস্তবতা উপলব্ধি ও সামাজিক কল্যাণের প্রতি দায়িত্ববোধ। উদাহরণস্বরূপ, জমিদারদের সঙ্গে কৃষকের সংক্রান্ত লেনদেন, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থা, ইচ্ছাকৃত তালাক ও নারীর অধিকার সংক্রান্ত ইস্যুতে তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।
তিনি ‘فتاویٰ علاء الدينية’ নামে একটি সুপরিচিত ফতোয়া সংকলন রচনা করেন, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরের জিজ্ঞাসার জবাব দলীলসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োগ ও স্থানীয় অনুশীলন ছিল সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ।
শিক্ষাদান ও প্রাতিষ্ঠানিক অবদান
মুফতি আলিমউদ্দীন কেবল ফতোয়া প্রদানে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একাধিক মাদ্রাসা ও দারুল ইফতা, যেখানে ছাত্রদের ফিকহ, উসূল, কিয়াস ও তর্জমার মাধ্যমে শরীয়তের গভীরতা বোঝানো হতো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে আজও ফতোয়া বিভাগ চালু রয়েছে, যেখানে তাঁর সংকলিত দলীল, মসআলা এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি শেখানো হয়।
তিনি ছাত্রদের আত্মবিশ্বাসী ও বিশ্লেষণী ফকীহ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে যুক্তির চর্চা, মতভেদ বোঝা, দলীল উপস্থাপন এবং ইজতিহাদের ব্যাকরণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শেখানো।
সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও তাঁর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি
উপনিবেশিক শাসন, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবক্ষয়ের সময়ে ফিকহ চর্চা সহজ ছিল না। তখনকার মুসলিম সমাজ অনেকাংশেই বিভ্রান্ত ছিল আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের টানাপোড়েনে। এই পরিস্থিতিতে মুফতি আলিমউদ্দীন যুগোপযোগী ও সময়ের প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনাভিত্তিক ফিকহ চর্চার উদাহরণ স্থাপন করেন।
তিনি যেমন ব্যাংকের সুদের সাথে ইসলামী লেনদেনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন, তেমনি কলকারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্কেও শরঈ নির্দেশনা প্রদান করেন। নারীদের তালাক পরবর্তী অধিকার, যৌথ পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় তাঁর ফতোয়া ছিল আধুনিক সমাজের প্রশ্নের জবাব।
উত্তরাধিকার ও ভাবাদর্শের সম্প্রসারণ
মুফতি আলিমউদ্দীনের সর্ববৃহৎ অবদান ছিল তাঁর চিন্তা ও চর্চার উত্তরাধিকার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তর। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই উপমহাদেশজুড়ে নামকরা মুফতি, বিচারপতি ও শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।
তাঁর ফতোয়া ও শিক্ষাদর্শ আজও বিভিন্ন মাদ্রাসা ও ইসলামী গবেষণাকেন্দ্রে পড়ানো হয়। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের মধ্যে তাঁর নাম একপ্রকার আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর জীবনী ও কর্মপদ্ধতি আজকের যুগের ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত।
ফিকহী সমস্যার সমাধানে তাঁর পদ্ধতি ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি
মুফতি আলিমুদ্দিন (রহ.)-এর ফিকহী অবদানের অন্যতম প্রধান দিক হলো—তিনি যেভাবে জটিল ও সমসাময়িক মাসায়েলের সমাধানে সুস্পষ্ট ও সুসংহত একটি পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তাঁর ফতোয়ার নীতিমালায় দেখা যায় যে, তিনি কেবল কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে সিদ্ধান্ত দিতেন না; বরং ইজমা, কিয়াস, উর্ফ ও মাসলাহার মতো ফিকহী মূলনীতিগুলোকেও যথাযথভাবে কাজে লাগাতেন। তাঁর বিচার বিশ্লেষণমূলক ক্ষমতা ও ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই প্রশস্ত ছিল যে, সমকালীন অনেক বিতর্কিত বিষয়ে তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য মতামত প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন।
তাঁর ফতোয়ায় একটি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়—তিনি স্থানীয় জনমানস ও সামাজিক বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন না। বরং একটি মাসআলার নির্ধারণে তিনি উরফ তথা স্থানীয় রীতিনীতিকেও বিবেচনায় নিতেন, যা ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরবঙ্গের কিছু উপজাতি অঞ্চলে সম্পত্তি বণ্টন ও বিবাহ-সংক্রান্ত কিছু ঐতিহ্য ছিল, যেগুলো শরীয়তের মূলনীতির সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সেখানে মুফতি আলিমুদ্দিন (রহ.) ত্বরিৎ হস্তক্ষেপ করে শরীয়তের আলোকে মাসআলা নির্ধারণ করেন এবং সংশ্লিষ্টদের তা বোঝাতে সক্ষম হন।
তিনি ইখতিলাফি মাসায়েলেও একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। তাঁর ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, তিনি একাধিক মতের মাঝে প্রাধান্য নির্ধারণে দলীল, গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তবতার সমন্বয় করতেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘তালাক-ই-সালাসা’ তথা একসাথে তিন তালাক দেওয়ার মাসআলায় তিনি ঐতিহ্যবাহী হানাফী মতকে সমর্থন করলেও, সমাজে এর অপব্যবহার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির পক্ষে থাকতেন এবং প্রয়োজনে বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খুঁজতেন।
তাঁর ফিকহী কর্মকাণ্ডে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—‘মাসলাহা মুর্সালা’ তথা জনকল্যাণের উপযোগিতা নির্ণয়ে তাঁর দক্ষতা। অনেক সময় কোনো মাসআলার শরয়ি মূলনীতির বিশ্লেষণে তিনি এই দিকটিকে প্রাধান্য দিতেন, বিশেষত যখন তা মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণে ভূমিকা রাখে।
মুফতি আলিমুদ্দিন (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, ফতোয়া কেবলমাত্র একটি আইনি মত নয়, বরং এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক দিকনির্দেশনা, যা মানবজীবনের ধর্মীয় ও দুনিয়াবি উভয় প্রেক্ষাপটেই ভারসাম্য সৃষ্টি করে। তাই তাঁর ফতোয়াসমূহে কেবল গ্রন্থগত উদ্ধৃতি নয়, বরং যুক্তি, দালিলিক বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষিত-ভিত্তিক যুক্তি দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে একজন প্রাজ্ঞ ও জনদরদী ফিকহবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
উপসংহার
মুফতি আলিমউদ্দীন ছিলেন একাধারে গবেষক, মুফতি, শিক্ষক ও চিন্তাবিদ। তিনি বাংলা সমাজে ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন এবং জনগণের জন্য শরঈ দিকনির্দেশনার এক প্রজ্ঞাবান সেতুবন্ধন স্থাপন করেন।
তাঁর ফতোয়া, শিক্ষাদান ও দারুল ইফতার উন্নয়ন আজও বহু মানুষকে প্রভাবিত করছে। তাঁর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়, কিভাবে শরীয়ত ও বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা যায়। তিনি শুধু তাঁর সময়ের একজন আলেম ছিলেন না, বরং ছিলেন এক চলমান দৃষ্টান্ত, যা প্রজন্মান্তরে চর্চিত হবে।