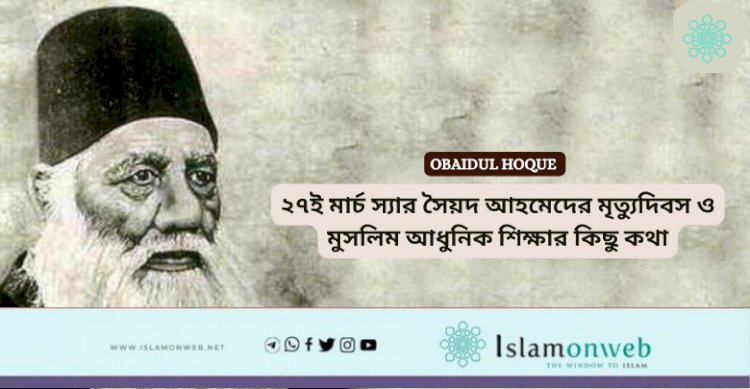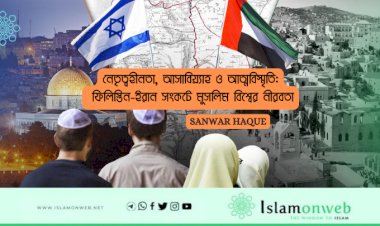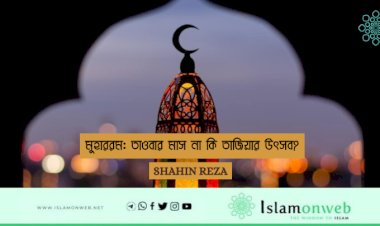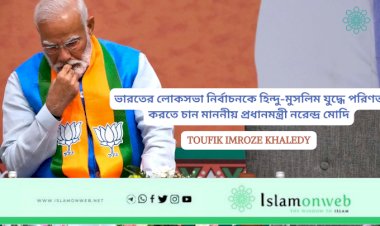২৭ই মার্চ স্যার সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুদিবস ও মুসলিম আধুনিক শিক্ষার কিছু কথা
আজ ভারতে এক অন্যতম মুসলিম শিক্ষাবিদের মৃত্যুবার্ষিকী। ২৭ মার্চ ১৮৯৮ স্যার সৈয়দ আহমদ খান ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি সত্যিকার অর্থেই আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন। উপমহাদেশের মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খানকে কেউ ভালো আর কেউ খারাপ বলে মন্তব্য করে থাকে। প্রায় এক শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও আজও তার নাম বেঁচে আছে। তিনি ছিলেন ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। স্যার সৈয়দ এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার সময়ের চেয়ে এক শতাব্দী এগিয়ে কথা বলতেন। তিনি উনিশ শতকের এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। তবে তিনার জীবন বিতর্ক ও সমালোচনার থেকে মুক্ত নয়। তিনি নানা কারণে ইতিহাসে সমালোচিত কিন্তু এই লেখনীতে শুধু মাত্র আমরা তার শিক্ষা ও সমাকল্যাণ ভিত্তিক চিন্তার আলোচনা করব।
মুসলিম শিক্ষার প্রতি মনোযোগ:
স্যার সৈয়দ আহমেদ খান জ্ঞান অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা, যার জন্য তিনি কবিতা ও সাহিত্যকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ভারতের ইতিহাসে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক যা। জাতি নিয়ে উদ্বিগ্ন জনগণকে ভাবতে বাধ্য করেছে।রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত অবস্থার উপলব্ধি, পরিবর্তিত চাহিদা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে।তাদের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো বেড়ে উঠছিল তা অনুধাবন করতে না পেরে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে মুসলমানরা তাদের মর্যাদা হারাচ্ছিল।অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস যা ছিল সবই তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।তিনি সমস্ত দায়ভার মুসলমানদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। এই অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, যার প্রভাব এখনও কোথাও কোথাও বিদ্যমান।এটি ছিল মুসলমানদের জন্য চিন্তার মুহূর্ত।তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম স্যার সৈয়দ আহমদ খান, যিনি এই দলের নেতা ছিলেন।তিনি তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মুসলমানদের কল্যাণ এবং তাদের সংস্কারের জন্য নিবন্ধগুলি দেখায় যে স্যার সৈয়দ একজন বিশেষজ্ঞর মতো মুসলমানদের দৃশ্যমান শিরাকে চিনতে পেরেছিলেন।
আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়: একটি নিবারণ
এখন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (যাকে সাধারনত আমরা এএমইউ নামে চিনি) কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে একশ বছর পূর্ণ করেছে। মূলত স্যার সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৫ সালে মুহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, এটি সংসদের একটি আইন দ্বারা ১৯২০ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।
এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে একত্রিত করা। তিনি কোনো সরকারি অর্থায়ন মুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন। এটি শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে ইংরেজিকে শেখার মাধ্যম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অভিযোজিত করে মুসলিম শিক্ষার আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। আন্দোলন মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করেছিল এবং তাদের একটি সাধারণ ভাষা উর্দু প্রদান করেছিল। এই শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বৃহত্তর আলীগড় আন্দোলনের একটি প্রানবিন্দু। আলিগড় আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য একটি ভারী এবং দীর্ঘস্থায়ী অবদান রেখেছে। উনিশ শতকের অন্যান্য শক্তিশালী কিন্তু কম অভিযোজিত আন্দোলনের তুলনায় এই আন্দোলন ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে মুসলিম সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এটি অন্যান্য সমসাময়িক আন্দোলনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল যে এটি উনিশ শতকে অন্যান্য সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের উত্থান ঘটায়। আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব শুধুমাত্র উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এর বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বার্ষিক শিক্ষা সম্মেলন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আঞ্জুমান-ই-তারক্বী উর্দু, জামিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। মিলিয়া ইসলামিয়া, দার-উল-উলূম নদভা, লখনউ, এবং দার-উল-মুসানফাফিন। এই সব জিনিস সম্মিলিত ভাবে মুসলিম সমাজের উন্নতির পথের পথেয় হয়ে ছিল।
ইংরেজি ও উর্দুর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব:
১৮৫৭ সালে, ভারতে সর্বত্র ইংরেজি শিক্ষার বিকাশ ঘটেছিল, কিন্তু আলফ্রেড ক্রফ্টের শিক্ষাগত প্রতিবেদনে দেখা যায়, মুসলমানদের অবস্থা শিক্ষার দিক থেকে খুবই পশ্চাৎপদ ছিল, সমগ্র দেশে মুসলিম স্নাতকের সংখ্যা ছিল বিশ জন। সতেরো বিএ এবং তিন এমএ কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের পশ্চাৎপদতা উপলব্ধি করতে পারেনি, কারণ উপরোক্ত উদ্ধৃতি অধ্যয়ন থেকে এটা স্পষ্ট যে মুসলিম সম্প্রদায় অবহেলা ও গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি তার প্রাচীন বিজ্ঞান নিয়ে
গর্ব করতেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে তিনি বেকারত্ব ও দারিদ্রে ভুগছিলেন, তবুও তিনি তা উপলব্ধি করতে পারেননি।
স্যার সৈয়দ আহমদ খান চেয়েছিলেন উন্নয়নের জন্য মুসলমানরা ইংরেজি শিখুক। তবে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল। তিনি উর্দু ভাষাকে শুধু রক্ষাই করেননি বরং উর্দু সাহিত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটিয়ে উর্দু সাহিত্যের বিকাশ ও বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।স্যার সৈয়দ আহমদ খান তাঁর সাহিত্য ও রাজনৈতিক কৃতিত্ব দিয়ে ভারতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নবাব মহসিন-উল-মুলক, নবাব ওয়াকার-উল-মুলক, মাওলানা নাজির আহমদ, মৌলভী চেরাগ আলী, মৌলভী জয়নুল-আবিদীন এবং আলতাফ হুসেন হালীর মতো ব্যক্তিবর্গ, যারা মুসলমানদের সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারা তাঁর সাহিত্য বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ডজন খানেক বই এবং শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার জীবদ্দশায় ইংরেজি, ফার্সি, ফরাসি ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে।
তার সম্মাননা ও ভর্ৎসনা:
একদিকে মুসলিম সমাজ স্যার সৈয়দের নিঃস্বার্থ সেবা এবং তাঁর চিন্তা-চেতনা থেকে উপকৃত হচ্ছিল, তাঁর জীবনে এক নতুন সূর্য উদিত হচ্ছিল।এটাও সত্য যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব বিতর্কিত থেকে গেছে।ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। তৎকালীন পণ্ডিতরা তাকে কাফের ও নাস্তিকদের কাতারে স্থান দিয়েছিলেন, অন্যদিকে আলোকিত শ্রেণী তাকে "মুজতাহিদুল-আছর" এবং "ইমাম-এ-জামানা" বলে মনে করতেন। নামেই স্মরণ করা হয়। স্যারের শিক্ষাগত চিন্তাধারা। সৈয়দ একদিকে যেমন তাকে ইসলাম বিদ্বেষী এবং ব্রিটিশদের বন্ধু আখ্যা দিয়েছিলেন, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবীরা তাকে সমসাময়িক ও দূরদর্শী উপাধিতে ভূষিত করেন।
এত কিছুর পরেও, কিছু পণ্ডিত ও সমালোচক এবং এমনকি তাঁর বিরোধীরাও একমত বলে মনে হয় যে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি সামাজিক, রাজনৈতিক, সভ্য, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার সম্পাদকীয় ও সংঘ। মুসলমানদের জীবনের দিকনির্দেশনা এবং তাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কোণ, এতে নতুন সম্ভাবনার আলোকিত করা এবং সময়ের সাথে ধাপে ধাপে হাঁটতে নিরন্তর নিজের থেকে উচ্চতর হওয়ার চেষ্টা করা।আধুনিক সব পরিবর্তন মুসলমানদের প্রগতিশীল চিন্তাধারায়। , যে চিন্তা ও আন্দোলন দেখা যায় বহু বছর আগে স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সবার সামনে। স্যার সৈয়দ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানরা যদি যত্ন না নেয় এবং সময়ের সাথে এগিয়ে না যায় তবে তাদের ধ্বংস হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না।
ইতি কথা:
নিঃসন্দেহে স্যার সৈয়দ এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার সময়ের চেয়ে এক শতাব্দী এগিয়ে কথা বলতেন। আর আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পা রেখেছি, তাই মনে হচ্ছে মুসলিম উপমহাদেশ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উল্টো দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি এমন এক অন্ধকার যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে জাতি নিপীড়নে ভুগছিল। এমন পরিস্থিতিতে জাতি সংস্কারের ভার নিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ।
তার ব্যক্তিগত ও এএমইউ-এর মহান কৃতিত্ব সত্ত্বেও, এটি একটি দুঃখজনক সত্য যে মুসলমানরা এর প্রতিষ্ঠাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে চলতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই ধরনের আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিবর্তে, সম্প্রদায়ের নেতারা স্থির হয়ে বসে ছিলেন, স্যার সৈয়দের প্রশংসা করে এবং প্রায় দেড়শো বছর আগে তিনি যে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করেছিলেন তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। এএমইউ-এর দৃষ্টিভঙ্গির আদলে তৈরি নতুন প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রদায় এবং দেশকে আরও অনেক বেশি উপকৃত করবে। সম্ভবত মুসলিমরা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি সময় বিপর্যস্ত ছিল, এবং মাদ্রাসায় দেওয়া ধর্মীয় শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, যতক্ষণ না তারা মাত্র কয়েক দশক আগে জেগে উঠেছিল একটি পরিবর্তিত সমাজে নিজেদেরকে বাক্সবন্দী এবং আউটক্লাস করার জন্য। এখন মুসলমানরা তাদের জড়তা থেকে বেরিয়ে আসছে এবং আবার আধুনিক শিক্ষায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে-আশা করি, এখনও খুব বেশি দেরি হয়নি।