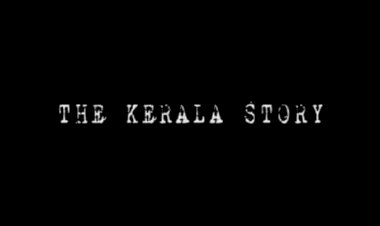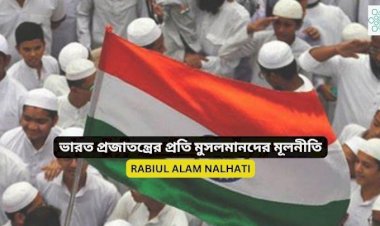সংকটময় মোড়ে নেপাল: প্রজন্মের পরিবর্তন নাকি বিশৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি?
ভূমিকা
২০০৮ সালে রাজতন্ত্র বিলোপের পর থেকে নেপাল একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু স্বাধীন গণতান্ত্রিক কাঠামোর এই অভিযাত্রা শুরু থেকেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বল শাসনব্যবস্থার ভারে ন্যুব্জ হতে থাকে। ২০২৫ সাল এসে যেন এক অগ্নিক্ষণের সূচনা ঘটায়। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির (K.P. Sharma Oli) সরকার হঠাৎ করেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ২৬টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (Social Media Platforms) —ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি। সরকার একে “জাতীয় নিরাপত্তা” ও “ক্ষতিকর কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের” যুক্তিতে বৈধতা দিতে চাইলেও সাধারণ মানুষের চোখে এটি ছিল ভিন্ন বাস্তবতা, বাকস্বাধীনতার উপর আঘাত এবং দুর্নীতিকে আড়াল করার এক মরিয়া চেষ্টা। যে নীতি শুরুতে প্রযুক্তিনির্ভর এক পদক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল, তা দ্রুতই পরিণত হয় জাতীয় সঙ্কটে। প্রকাশিত হতে থাকে গভীরতর ক্ষত—দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, বেকারত্ব, ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা। এ যেন কেবল ওলির পতনের আখ্যান নয়, বরং তিন দশকের ব্যর্থ রাজনীতির বিরুদ্ধে এক প্রজন্মের সম্মিলিত বিদ্রোহ।
রাজতন্ত্র থেকে রাজনৈতিক ভাঙন: ভগ্ন গণতন্ত্রের চিত্র
নেপালের আধুনিক রাজনৈতিক যাত্রাপথ মূলত অস্থিরতা ও রূপান্তরের কাহিনি। গৃহযুদ্ধ ও রাজতন্ত্রের অবসানের পর ২০০৮ সালে দেশটি আত্মপ্রকাশ করে একটি ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে। নতুন যুগের সূচনা বলে একে উদ্যাপন করা হলেও বাস্তবতা ছিল ভিন্ন, অস্থায়ী জোট সরকার, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আর দুর্নীতির শৃঙ্খল। তিন নেতা—কেপি শর্মা ওলি (KP Sharma Oli), পুষ্পকমল দাহাল (Pushpa Kamal Dahal) ও শের বাহাদুর দেউবা (Sher Bahadur Deuba) —প্রায় তিন দশক ধরে পালাক্রমে ক্ষমতা ভোগ করেছেন। প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিবর্তে তারা লিপ্ত থেকেছেন স্বজনতন্ত্র, দখলদারিত্ব ও ক্ষমতার লোভে।
এই ভগ্ন রাজনৈতিক চিত্রের ভার বহন করেছে তরুণ প্রজন্ম। কাজের অভাবে প্রতি বছর হাজারো তরুণ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে ক্ষুদ্র ও স্বল্পমজুরির কর্মসংস্থানের জন্য। অন্যদিকে দেশে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন প্রতীক—‘নেপো কিডস’ (Nepo Kids)। রাজনীতিবিদদের সন্তানরা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করছে বিদেশি গাড়ি, বিলাসী জীবনযাপন ও ভোগবিলাস। বঞ্চনা আর বৈষম্যের এই দুই মেরু তরুণদের মনে জন্ম দিয়েছে ক্ষোভ ও হতাশার। ২০২৫ সালের মধ্যে প্রজন্মটি উপলব্ধি করে—এই গণতন্ত্র তাদের নয়, এই নেতৃত্ব তাদের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।
ওলি সরকারের ২৬টি সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত যেন আগুনে ঘি ঢেলে দিল। সরকারের যুক্তি—জাতীয় নিরাপত্তা, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও ক্ষতিকর কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু জনগণের কাছে এটি ছিল স্পষ্টতই ভিন্নতর বার্তা: দুর্নীতিকে আড়াল করা ও সমালোচনার কণ্ঠ রুদ্ধ করা। সামাজিক মাধ্যম তখন কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং রাজনৈতিক মতপ্রকাশের ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বাজার, এমনকি পর্যটন খাতেরও প্রাণ। হঠাৎ এই বন্ধে আঘাত হানল মানুষের জীবিকা, আর বিশেষত তরুণ প্রজন্মের আত্মপরিচয়ে। সরকারের কাছে এটি ছিল প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্ত, কিন্তু জনগণের কাছে এটি সরাসরি বাকস্বাধীনতা ও অস্তিত্বে আঘাত। ফলশ্রুতিতে জ্বলে উঠল প্রতিবাদের শিখা।
২০২৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রাস্তায় নামে হাজারো ছাত্রছাত্রী ও তরুণ। কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান—সবখানে শ্লোগানে মুখরিত শান্তিপূর্ণ মিছিল। তাদের দাবির মূলকথা ছিল সহজ—বাকস্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির অবসান। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া হলো নির্মম। নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালায় নিরস্ত্র যুবকদের ওপর। প্রাণ হারায় প্রায় কুড়িজন, যার মধ্যে এক ১২ বছরের শিশু; আহত হয় চার শতাধিক।
সরকারের ব্যাখ্যা ছিল তারা নাকি ‘অসামাজিক উপাদান’ (Anti-social Elements) দমন করছে। অথচ প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে আর মোবাইল ভিডিওতে ফুটে ওঠে ভিন্ন ছবি—শান্তিপূর্ণ ছাত্রদের উপর রাষ্ট্রের অতি-নৃশংস দমননীতি। একটি সাধারণ ইন্টারনেট ইস্যু মুহূর্তেই পরিণত হলো সর্বজনীন আন্দোলনে, যেখানে রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত একই দাবিতে মানুষ রাস্তায় নেমে এলো। ওলি সরকার ভেবেছিল কেবল একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার মুখোমুখি, কিন্তু তারা বোঝেনি ক্ষোভ কত গভীরে প্রবাহিত।
৮ই সেপ্টেম্বরের রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর যেন আগুন জ্বলে ওঠে সর্বত্র। উত্তেজিত জনতা জ্বালিয়ে দেয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের বাড়িঘর, সংসদ ভবনেও হয় হামলা। হেলিকপ্টারে করে মন্ত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ আন্দোলনকে প্রশমিত করতে পারেনি। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি বাধ্য হন পদত্যাগে। কিন্তু এটি কেবল এক ব্যক্তির পতন নয়; এটি ছিল পুরনো রাজনৈতিক প্রজন্মের প্রতি সর্বাত্মক অবিশ্বাসের ঘোষণা। তিন দশকের গোষ্ঠীভিত্তিক নেতৃত্ব যে জনগণের আস্থা হারিয়েছে, এই আন্দোলন তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।
কাঠমান্ডুর যুবভূমিকম্প: প্রজন্মের বিদ্রোহ
২০২৫ সালের এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তরুণ প্রজন্ম, বিশেষত জেন-জী (Gen-Z)। যাদের এতদিন রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় বলা হতো, তারা Social Media-এর মাধ্যমে পেয়েছে কণ্ঠস্বর ও সংগঠনের শক্তি। দুর্নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ হয়ে ওঠে #NepoKids-এর মতো হ্যাশট্যাগে। সরকারের নিষেধাজ্ঞা তরুণদের ডিজিটাল প্রতিরোধকে রূপ দিল রাস্তায় নেমে বাস্তব আন্দোলনে। প্ল্যাকার্ড, বই, স্কুলব্যাগ হাতে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গড়ে তোলে প্রতিবাদের সামনের সারি। এ আন্দোলন তাই ছিল শুধু প্রতিবাদ নয়, বরং এক প্রজন্মের রাজনৈতিক জাগরণ, যেখানে যুবসমাজই হলো পরিবর্তনের চালিকাশক্তি।
নেপালের এই নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৌশলগত অবস্থানের কারণে ভারত ও চীন পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। ভারত গণতান্ত্রিক আলোচনার আহ্বান জানায়, চীন স্থিতিশীলতার ওপর জোর দেয়। পাশ্চাত্য গণমাধ্যম এ আন্দোলনকে চিত্রিত করে তরুণদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক জাগরণ হিসেবে, যার তুলনা টানা হয় শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের আন্দোলনের সাথে। আন্তর্জাতিক এনজিও (NGO) ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালানোকে মানবিক আইন লঙ্ঘন বলে আখ্যা দেয়। যদিও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ হয়নি, তবু বৈশ্বিক চাপ নেতৃত্বের ওপর বাড়তে থাকে। হিমালয়ের এই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের স্থিতিশীলতা যে বিশ্বরাজনীতির জন্য কতটা মূল্যবান, তা আবারও স্পষ্ট হয়।
ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণ: সংস্কার নাকি ধ্বংস?
এই সঙ্কট নেপালের জন্য একদিকে তৈরি করেছে বিরাট সুযোগ, অন্যদিকে নতুন বিপদের আশঙ্কাও। সুযোগ হলো—নতুন প্রজন্ম এখন প্রকাশ্যে জবাবদিহি ও সংস্কারের দাবি তুলেছে। দুর্নীতি, স্বজনতন্ত্র আর ফাঁকা প্রতিশ্রুতিকে তারা আর মানবে না। এই ক্ষণটিকে কাজে লাগানো গেলে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা এবং তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ সম্ভব।
কিন্তু ঝুঁকিও প্রবল। ওলির পতনের ফলে সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক শূন্যতা যদি পূরণ না হয়, তবে অস্থিতিশীলতা দীর্ঘায়িত হতে পারে। সেনা হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ববাদী শক্তির উত্থানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিক্ষোভ, অবরোধ ও অনিশ্চয়তা নেপালের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করতে পারে, যা বিনিয়োগ ও পর্যটন কমিয়ে দেবে, আরেক দফা তরুণদের বিদেশগমনে বাধ্য করবে।
নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও জনঅসন্তোষের মধ্যে যে তরুণ প্রজন্ম রাজপথে নেমেছে, তাদের মধ্যে বিশেষত Gen Z-এর একাংশের আচরণ এখন সীমা ছাড়াচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, এমনকি দেশের সংসদ ভবন পর্যন্ত ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া নিছক ‘বিপ্লবী আবেগ’ নয়, বরং এক গভীর রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও তাৎক্ষণিক উত্তেজনার ফল। জনস্বার্থে আন্দোলন করা গণতান্ত্রিক অধিকার—কিন্তু সেই আন্দোলনের নামে যখন শহরের রাস্তাঘাট, সরকারি দপ্তর এমনকি রাষ্ট্রের প্রতীকগুলিকে ধ্বংস করা হয়, তখন তা কেবল ‘প্রতিবাদ’ নয়, তা হয়ে ওঠে দায়িত্বহীনতা ও ছেলেমানুষি। Gen Z-এর এই "স্পন্টেনিয়াস" রাগ যেন এক ডিজিটাল তাড়নার প্রতিফলন—যেখানে মীম, টিকটক আর ইনস্টাগ্রামের লাইভ ভিডিও-র চেয়ে বাস্তব ইতিহাস ও কৌশলগত আন্দোলনের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে।
ইতিহাস সাক্ষী, আরব বসন্তের সময়েও তরুণ প্রজন্মের রাগ ও আন্দোলন মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে দ্রুত পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু কী হলো পরিণামে? মিসরের তাহরির স্কয়ারে লক্ষ লক্ষ তরুণ যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিল, তা কয়েক বছরের মধ্যেই সামরিক শাসন, অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় পর্যবসিত হয়। ইন্দোনেশিয়াতেও ১৯৯৮ সালে সুহার্তো সরকারের পতনের সময় ছাত্র আন্দোলন রাজপথ দখল করেছিল, কিন্তু পরবর্তী দশকে দুর্নীতি, রাজনৈতিক সহিংসতা ও ধর্মীয় বিভাজন নতুন করে মাথা তোলে। নেপালের Gen Z যদি সত্যিকারের পরিবর্তন চায়, তবে ধ্বংস নয়—নির্মাণে মন দিতে হবে। ইতিহাস কেবল গর্জনে নয়, পরিণতিতে বিচার করে। হেডলাইন বানানো সহজ, রাষ্ট্র গঠন কঠিন। তাদের সেই কঠিন দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে এখনই।
অতএব, নেপাল এখন দাঁড়িয়ে আছে এক সঙ্কটময় মোড়ে। একদিকে আছে সংস্কার ও নবজাগরণের পথ, অন্যদিকে আছে বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ের খাদ। কোন পথ বেছে নেবে নেপাল, সেটিই আগামী সময় নির্ধারণ করবে।
উপসংহার
২০২৫ সালের নেপাল সংকট কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার লড়াই ছিল না; এটি ছিল কয়েক দশকের দুর্নীতি, স্বজনতন্ত্র ও ব্যর্থ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ। রক্তদানের মধ্য দিয়ে যে প্রজন্ম আন্দোলনের অগ্রভাগে দাঁড়িয়েছে, তারা কেবল পরিবর্তন চায়নি—তারা শাসনব্যবস্থার নৈতিক পুনর্জাগরণ দাবি করেছে। তাদের ঐক্য ও সাহস একদিকে পুরনো রাজনৈতিক প্রজন্মের পতন ঘটিয়েছে, অন্যদিকে খুলে দিয়েছে গণতন্ত্রের নতুন দিগন্ত। তবে ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নেতৃত্বের প্রজ্ঞা ও সাহসের উপর। যদি তারা স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি ও প্রকৃত সংস্কারের পথে হাঁটে, তবে এই সংকট পরিণত হবে নেপালের গণতন্ত্রের নতুন ভিত্তিপ্রস্তরে। আর যদি ব্যর্থ হয়, তবে ইতিহাস হয়তো একে আরেকটি অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির অধ্যায় হিসেবেই লিখে রাখবে।